গল্প - জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
(১)
অণু-পরমাণুরা এমনিতেও এখানে ওখানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ অবধি তা নিয়ে কোনো গোলমাল হয় নাই। মাঝ থেকে মানুষ এসে এমন কায়দা করে দিলে… যে দুটো শহর ঝলসে গেল।
প্রথম শো
সুপার মারিও
স্টেশন থেকে ক্রমশ দূরে সরতে সরতে প্রথমে আশেপাশে রাস্তা ঘাটের চেহারা বদলায়, তারপর বাড়ি-ঘরের উচ্চতা হ্রাস পায়... একসময়ে টাউনের আধুনিকতাকে একদম পেছনে ফেলে ক্রমে পাড়া-গেঁয়ে হয়ে ওঠে সব কিছু। এখানে ওখানে উঁকি দেয় হাঁস-পুকুর আর নারকেল-সুপুরির বাগান মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাইস্কুলের মাঠে বাঁশের গোলপোস্ট আর তার সামনে ঘেঁটে থাকা কাদা জানিয়ে দেয়, এই মাঠে এখনও দাপিয়ে বেড়ায় দামাল ছেলেরা। কোনও নিচু বাড়ির দেওয়ালে সাড়ি সাড়ি ঘুঁটে শুকোতে দেখা যায় চড়া রোদে। ব্যাটারিতে চলা অডিও প্লেয়ার আর মাইকের চোং নিয়ে কোনও আসন্ন যাত্রা, ম্যাজিক শো অথবা ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচার করতে করতে চলে যায় সাইকেল ভ্যান। তাঁবু খাঠানো হয় গাজনতলার মাঠে। যাত্রা, কীর্তন, পালা-গান, মেলা… যখন আর কিছু থাকে না, শুধু খুঁটিগুলো পড়ে থাকে এদিক ওদিক... বাঁধা গোরু আর ছাড়া ছাগলে তার চারপাশে চড়ে খায়।
গোপীবল্লভের মন্দিরে শ্রাবণ পূর্ণিমায় উৎসব হয়, মেলা বসে তার সিকি মাইল দূরে গ্রামের এই গাজনতলায়। দশ দিন ধরে চলে মেলা... তবে সুনাম আছে। আশপাশের অন্য গ্রামের লোকও আসে। অস্থায়ী প্রাকারের ওপর বেশ কিছু রঙচঙে ছবি আর কাগজের বড়ো পোস্টার আভাস দেয়, এবারের মেলায় মনোরঞ্জনের কী কী চমক। তার মধ্যেই কিছু বর্ণময়ে পোস্টারে মোটা কাজল পড়া দু’টো চোখ আর অদ্ভুত মুদ্রায় দু’টো হাত পথ-চলতি মানুষকে সম্মোহিত করে চলে– মাস্টার মারিওর ইন্দ্রজাল...প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা… দুটো করে শো।
– এই হুলো, কটা বাজল দেখ তো?
– সাড়ে চারটা বাজতে এখনো দেরি আছে গুরু।
– লোকজন কেমন? ভিড় না থাকলে ফালতু হাজার ভ্যানতারা পোষাবে না!
– আছে আছে... আসছে তো এখনও।
– ‘আছে আছে!’ কাল দুইটা শো মিলায় পঞ্চাশজনও হয় নাই! গিয়ে দেখ জলদি… পাবলিক কম থাকলে আইটেমও কম থাকবে!
স্পষ্ট অনীহা নিয়েই স্যান্ডো গেঞ্জী আর খয়েরী ফুল-প্যাণ্ট পরা মেটে-রঙা রোগা-পাতলা ছেলেটি ছাউনির সেই অংশের দিকে চলে গেল যেখান থেকে দর্শকদের দেখা যায়। তার যাওয়া নিশ্চিৎ করে আবার আয়নার দিকে ফিরে বসল মাঝবয়সী লোকটা। হাতে দশ মিনিট সময়, তার মধ্যেই সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে।
তাঁবুর পেছন দিকে এই ছোট্ট অংশটাকে গ্রীনরুমও বলা চলে... মঞ্চে নামার আগে প্রস্তুতির সাজঘর। মনযোগ দিয়ে মুখে সাদা রঙের পোঁচ চড়িয়ে যাচ্ছে লোকটা। মুখটা যতটা সম্ভব ফরসাপানা করে ফেলতে হবে, যাতে অল্প আলোতে নীল, বেগুনি ফোকাস পড়লে বেশ রহস্যময় লাগে। তারপর মোটা করে কাজল পড়তে হবে দু’টো চোখে। কাঁচা-পাকা গোঁফে ইতিমধ্যেই লেপে নিয়েছে কালি। অবশেষে সাদা পালক দেওয়া লাল-কমলা রেশমের তাজটা পাতলা হয়ে আসা চুলের মাথাটা ঢেকে ফেললেই মুরারীমোহন বেরা থেকে একেবারে মাস্টার মারিও! কারো বাপের সাধ্যি নেই মাস্টার মারিওকে দেখে বলে, যে ব্যাটা পাশের নবগ্রামের মুরারীমোহন! হুলো অবশ্য খুব একটা মেক-আপ করে না। শুধু একটা সাদা শার্ট আর কালো প্যান্টের সঙ্গে বো টাই পরে নেয়। মাথার চুলটা কায়দা করে টেরি করে একেবারে কেতাদুরস্ত সহকারী। মাস্টার মারিওর ইন্দ্রজাল বিস্তারের ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী দর্শকদের মাঝে সবসময়ে অন্যকিছু খোঁজে তার চোখ দু’টো। ভিড়ে পরিণত বয়সের মহিলা চোখ টানলে একটু বেশি সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। মুরারীও ব্যাপারটা এতদিনে বুঝে গেছে, মাঝে মাঝে টনিক দিতে হয় বাগে রাখতে।
চোখেও কাজল পড়ে গেছে, এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা... পাগড়ী আর আলখাল্লাটা চাপালেই একদম মাস্টার! হুলো ফিরে এসে বলল ‘গুরু... কুড়ি জনের বেশিই তো মনে হচ্ছে দেখে, আরও আসছে... কালকের থেকে বেশিই হবে বুঝলে?’ জলের বোতলটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মুরারী। খুব সাবধানে আলগোছে দু’ঢোক জল খেয়ে আবার নিজের মুখটা আয়নায় দেখে নিল। নাঃ কোথাও রঙ চটে যায়নি। রেডি-মেড পাগড়িতে বসানো পালকটা হালকা ভাবে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল– “হাফও ভরেনি তাহলে... বেশি মাল বের করিস না। চটপট কম খাটনির মালগুলো রেডি কর। হাতে হাতে আগায়ে দিবি।
স্টেজটা ছোটো হলেও, তাতেও কায়দা করে বেশ লাল পর্দা টাঙানো আছে। মঞ্চের একদিকে কম পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে, সেখানে সব সরঞ্জাম রেখে, আড়ালে দাঁড়িয়ে আসতে আসতে পর্দা সরানো... রীতিমত অনুশীলন করে রপ্ত করেছে হুলো। তারপর কিছু একটা রঙচঙে তাক লাগানো ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে মাস্টার মারিওর প্রবেশ। এমনই হয়ে প্রতিবার। যারা মাস্টার মারিওর শো দেখেছে এর আগে, তারা এও জানে– কীভাবে মুখ রহস্যময় হাসি নিয়ে লোকটা আসবে, তারপর মাথার পাগড়ীটা খুলে তাতে হাতের বেঁটে লাঠিটা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক ছুঁড়ে দেবে রঙিন কাগজের ফুল, অথবা ছোটোদের জন্য লজেন্স। আর তার সাথে বাজতে থাকে এক রকমের লাড়েলাপ্পা মিউজিক! সেও হুলোর দায়িত্ব চালানো। আগে আর একটা স্যাঙাৎ ছিল, টাকার বখরা নিয়ে ঝামেলা করে পালিয়েছে। এখন হুলোই অল-ইন-অল। হিন্দী গানের সুর ঝ্যাঁঝ্যাঁ করে বেজে উঠল ভাড়া করা স্টিরিওতে, তারপর কমজোরী রঙিন আলোয় পর্দা ওঠার কিছুক্ষণ পরেই মাস্টার মারিওর প্রবেশ। জোরালো রঙিন আলো জ্বলে উঠল দু দিকে।
বেঁটে কালো রঙের ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে ঝলমলে ফুলের চেন বার করে আনলো টুপির ভেতর থেকে! জনা ত্রিশেক দর্শক, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছোটো ছেলেমেয়ে, হয়ত কিছু পরিবার এসেছে এছাড়া। পরিবার মানে মূলতঃ মহিলারা, তাদের চার-পাঁচ বছরের নাকে সর্দিঝড়া বাচ্চাদের নিয়ে। কে হিন্দী-ভোজপুরী গান শুনে খুশি আর কে মাস্টার মারিওর ম্যাজিক দেখে তা বোঝা মুশকিল। হাতের কাজ দেখানোর সময়ে দর্শক গুণতে নেই, গুরুর নিষেধ। তাই একটা কৃত্রিম হাসি নিয়ে মনোরঞ্জন করে যাচ্ছে জাদুকর মারিও। খেলার ফাঁকে ফাঁকে পরিস্থিতি মতো হুলো গান পালটে দিচ্ছে। গানের তালে তালে হাত-পা হেলিয়ে নেচে নিচ্ছে। ওটা দর্শকের উপড়ি।
হুলো নজর রাখছে– রঙিন বলের খেলা।
গুরু হলুদ বল আর নেট হাতে নিয়ে দেখাচ্ছে... বল গায়েব হবে, কমলা বল আসবে ঝুলি থেকে, তারপর লাল... তারপর কিচ্ছু না... তারপর দর্শকদের মধ্যে একজন ওদেরই চেনা ছেলেকে নিয়ে এসে তার এদিক ওদিক থেকে বেরোবে সব ক’টা বল। চেনা ছেলেটাও অপেক্ষা করে আছে, কখন ওর ডাক পড়বে। ডেলি পঞ্চাশ টাকা পায় ও– এইটুকু করার জন্য। কিন্তু বল আর নেট নিয়ে হাওয়ায় ঘোরাতে গিয়ে হাত থেকে বলটা ঝপ করে স্টেজে পড়ে গেল! কী সাঙ্ঘাতিক! মাস্টার মারিওর হাত থেকে এইভাবে বল পড়ে যায়নি কোনওদিন। নেট হাওয়ায় ঘুরোতেই বেকায়দায় কমলা বলটাও পড়ল স্টেজের ওপর। হলুদ-কমলা বল একসাথে বাউন্স করছে। তাতেই কেউ কেউ কী বুঝে হাততালি দিয়ে উঠল। মাস্টার মারিও বোকার মতো তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, দর্শকদের দিকে। হুলো আর সময় নষ্ট না করে চটপট ভোজপুরী গানের সুরে নাচের তালে তালে স্টেজে ঢুকে দু’টো বল তুলে নিল একটা মাথার ওপর কায়দা করে বসিয়ে অন্যটা নিয়ে পায়ে নাচাল খানিকক্ষণ... ডান পা, বাঁ পা... আবার ডান পা। বিখ্যাত লাতিন আমেরিকান ফুটবলারের মতো– এক বার হলুদ একবার কমলা বল নিয়ে জাগলিং, তার সঙ্গে লাড়েলাপ্পা গান। এও অনুশীলন করেছে একা একা। মারিওর ম্যাজিকের থেকেও কিছু বেশি ফোকট হাততালি কুড়িয়ে দু’টো বল আবার ম্যাজিশিয়ানের হাতে তুলে দিয়ে কুর্নিশ করে পর্দার আড়ালে চলে গেল হুলো। বল দুটোকে শূন্যে ছুঁড়ে হাওয়ায় গায়েব করে দিয়ে দ্রুত তাসের দিস্তা হাতে নিয়ে শাফ্ল করা শুরু করে দিল মাস্টার মারিও।
মাস্টার মারিওর পরিচিত, ঝলমলে কারসাজি… শো-এর পর শো দেখিয়ে যাওয়া প্রায় একই রকম কিছু খেলা। তাও কোনো না কোনো লোক বছরের পর বছর টাকা দিয়েই দেখতে আসে। চমৎকৃত হতে আসে। তারা কী নেহাৎই নির্বোধ অথবা নাবালক বলেই? নাকি সরল মানুষ এভাবেই পরিচিত মনোরঞ্জন আবার আবার ফিরে পেতে চায়, দেখাতে চায় পরের প্রজন্মকেও! এই গ্রাম কিংবা অন্য গ্রাম… কেউ না এলে কি আর এই পেশার কেরামতি চলত?
লোক ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাও, তাই নতুন কিছু ট্রিক শিখতে হয়… অন্যভাবে মনোরঞ্জন করার কথা ভাবতে হয়। সংলাপ, নাটক, সস্তা ভাঁড়ামো– যা খায় যে গ্রামের মানুষ!
খেলার সময়ে সাত পাঁচ চিন্তা না করলেও… লোক বুঝে মাঝে মাঝে নতুন ট্রিকগুলো ঝুলি থেকে বার করে মাস্টার মারিও।
দর্শকদের মধ্যে কারো কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটা দশ টাকার নোট নিমেষের মধ্যে পুরনো খবরের কাগজের টুকরো হয়ে যায়, তাতে কী পুরনো ফালতু খবর লেখা আছে– সেই পড়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে জাদুকর। নোটের মালিকের দিকে এগিয়ে দেয় সেই কাগজ। তাকেও পড়তে বলে। বোকার মতো সেই কাগজ হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেই লোকটি। তারপর সেই কাগজের টুকরো নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে দুবার হাতের মুঠোয় ঘুরিয়েই মারিও নিয়ে আসে একশ টাকার নোট। দর্শকের হাতে হাতে ঘুরে ফেরত চলে আসে সেই একশো টাকার নোট। তারপর আবার দশ টাকার নোট হয়ে ফিরে যায় মালিকের কাছে। বেচারা বোকার মতো হাসে– একশ টাকা ফিরে এলেই ভালো হত, ফেরে না। মনে সন্দেহ জন্মায়– দশ টাকার নোটটাও এখনো সচল কি না আলোয় উলটে-পালটে দেখে আস্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করে বোকা বোকা হাসি নিয়ে। জাদুর খেলা এগিয়ে যায়…
একটা ছোটো কামানে সাদা পায়রা ঢুকিয়ে দেয় হুলো। আর তারপর পটকা ফাটার মতো শব্দ আর ধোঁয়ার পর বেরিয়ে আসে অনেকটা রঙিন কাগজ। বারুদের গন্ধ ভরে যায় তাঁবুতে। গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ার শব্দ আসে। মনে হয় কাগজ পোড়ার গন্ধ আসছে। পায়রাটা বেরোয় জাদুকরের আলখাল্লার ভেতর থেকে। দুটো পায়রা প্রয়োজন, একটা কামানের মধ্যেই থেকে যায়। কখনো কখনো বাজির শব্দে কামানের ভেতরেই মরে যায়। হুলো চটপট কামানটা তুলে নিয়ে আসে পর্দার আড়ালে। ভেতরে কী অবস্থা দেখতে হবে…
নতুন খেলার আগেই জাদুকরের হাত থেকে হাত ফসকে পালায় একটা খরগোশ, কামান ফেলে রেখে তাকে ধরে নিয়ে আসতে ছোটে হুলো, কোনো রাজাজীর পালঙ্গ ভাঙা নিয়ে ভোজপুরী গানের তালে নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করে খরগোশটা হাতে নিয়ে। জাদুর ফাঁকেই কেউ চেঁচিয়ে ওঠে– খরগোশের মাংস খায়নি অনেকদিন! আর দুজন তাকে চুপ চুপ করে থামিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে… অমুক বার, নিরিমিষ। অমুক পুজো, নিরিমিষ! খাদ্য, খাদক, নিষেধ আর পাপের কথা ধোঁয়ার মতো ভরে যায় তাঁবুর ভেতর। খরগোশটাকে নিয়ে ঠিক কী করবে মারিও, বেমালুম ভুলে গেল। টিকিট কেটে যারা এসেছিল তার ম্যাজিক দেখতে… এখন নিজেদের মধ্যে বচসা করছে।
একজন চেঁচিয়ে ওঠে জয় গৌর-নেতাই। পাঁচ জন চেঁচিয়ে ওঠে জয় শ্রী রাম।
হঠাৎ করেই মনে হয়… তাঁবুতে ভিড় তিন-চারগুণ বেড়ে গেছে। মারিও নিজেই বুঝতে পারেনি… এত লোক কখন… কোথা থেকে এলো!
কয়েক মুহূর্তের সংগীতশূন্যতা। তারপরেই হুলো গান বদলে দিয়েছে সাউন্ড সিস্টেমে– ভারত কা বাচ্চা বাচ্চা…
মারিওর এতকালের শেখা ট্রিকগুলোর থেকেও বেশি জোরালো ম্যাজিক। সংগীত শুরু হতেই সবাই উঠে পড়ে হাত তুলে নাচতে শুরু করে দিল।
নতুন ট্রিক!… এইসব দর্শককে টানতে আরো ভালো নতুন ট্রিক দরকার। মারিওর থেকে মুরারীমোহন অনেক ভালো নাম… আর মঞ্চের চেহারা এবং সাজপোশাকটাও হতে হবে অন্য রকম।
খুব পরিচিত কারো চেহারা মনে পড়ে যায়, তার মতোই দু হাত তুলে দর্শকের সামনে দাঁড়ায় মুরারীমোহন। তারই মতো হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায়, দর্শকদের সমাদর স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গিতে। যেন তারই জয়ধ্বনি দিচ্ছে দর্শক। তারই পারফর্মেন্স দেখে আনন্দে নাচছে সবাই! মুরারীমোহনের উজ্জ্বল মেকআপ করা মুখে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভুৎ রূপ নেয় ক্রমশ। কামান থেকে বার করা প্রায় আধমরা পায়রাটা হাতে নিয়ে হুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই লাল আলোয় রূপান্তরিত মঞ্চের দিকে।
(২)
শুলেও শব্দ হয়, পাশ ফিরলেও শব্দ হয়। আর খাটের শব্দে পাশের ঘরের লোক অন্য কিছু ভেবে নেয়। এই ভেবে নেওয়া আর মনে হওয়ার কোনো একক নাই। যেমন ভিড়ের কোনো মুখ নাই। মুখ থাকলেও সাক্ষী নাই। সাক্ষী থাকলেও তার হদিশ নাই। তদ্দিনে অবতারের অবসর আর নটে শাকের চচ্চড়ি হয়ে যায়।
দ্বিতীয় শো
আরো বড়ো জাদুকরের খোঁজে…
করিমগঞ্জে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হলেও এদিক ওদিক হিন্দুদের বসতি টিকে আছে বহুকাল ধরেই। দেশ ভাগ বা দাঙ্গাও তাদের উৎকন্ঠিত করে কোথাও তাড়াতে পারেনি। দুর্দিনে খুব নিশ্চিন্তে না থাকলেও, দু’একটার বেশি লাশ পড়েনি এখানে ওখানে। সংখ্যা থাকলে তার লঘু-গুরু থাকবে, ঠিক যেমন স্বার্থ থাকলে তার ওঠা নামা থাকে। সেটা কথা নয়, কথা হল– ওই করিমগঞ্জেই মোরশেদ ফকিরের দরগা... সেখানে বাজারের কাছে একটা অশ্বত্থগাছের তলায় কোনও দোকান বসেনি কোনওদিন... তবু ভিড় জমে মাঝে মধ্যেই। শহুরে বিলাসিতা, আধুনিক মনোরঞ্জন থেকে অনেক দূরে থাকা করিমগঞ্জের বিস্ময় আর কৌতূহল দু-তিন ঘন্টা ওই অশ্বত্থগাছের নীচে তাদের আটকে রাখে। কখনও কুড়ি, কখনও পঞ্চাশ... কখনও তারও বেশি লোক ভিড় করে দেখে আজিজ ওস্তাদের ভেলকির খেলা। লাগ লাগ লাগ ভেলকি... ছু মন্তর ছু... কখন কী গায়েব হয়, আর কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করে বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয় হয়ে যায়। ছোটো গামছা পেতে খুচরো থেকে নোট ঘুরে ঘুরে জড়ো করে নেয় স্যাঙাৎ ফজল। ওস্তাদ জানে হাত-কী-সাফাই, ওস্তাদ জানে দেখনেওয়ালোকো বেকুব বানিয়ে দেওয়া ম্যাজিক কাকে বলে। করিমগঞ্জ শুধু জানে আজিজ-কা-খেল। আর ফজল জানে, মানুষ সম্মোহিত হ’তে ভালোবাসে, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করেই বেঁচে থাকতে চায়... স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির ঊর্দ্ধে কিছু দেখিয়ে মানুষকে আকর্ষিত করা এক সহজ আর প্রাচীন জীবিকা। যারা এতে মাত করতে জনে, তারা সিকন্দর হয়ে যায়। এ নিজেই এক মস্ত জাদু হয়ে আছে দুনিয়াদারির মাঝে।
আজিজের পুরো নাম কী– তা করিমগঞ্জের কাউকে জিজ্ঞেস করলে ঠিকঠাক বলতে পারবে কি না সন্দেহ। কেউ জানে না কোথা থেকে এসেছে, সঙ্গের ছেলেটাই বা কে হয়। শুধু নামাজ পড়ে, মসজিদে যায়... তাক লাগিয়ে দেওয়া হাতের কাজ, গলায় তাবিজ, ফেজ টুপি, কালচে ছোপ ধরা দাঁতের হাসি, চিলের মতো বাঁকানো নাক... আর চা-পাতার রঙ ধরানো লাল দাড়ি... ব্যস, আর কী বাকি থাকে জানার? সঙ্গের ছেলেটিও গলায় তাবিজ, মসজিদে নামাজ পড়তে যায়, হালকা সরু গোঁফ... চোখে সুরমা।
ওস্তাদ অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ… দেখলে ঠিকঠাক বয়েসও আন্দাজ করা যায় না– চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট... এর মধ্যে যা খুশি হ’তে পারে। শুধু মাথার ফেজটা সরালে বোঝা যায় কপালটা চওড়া হতে হতে মাথার মাঝখান অবধি চলে গেছে। গভীর বলিরেখার জ্যামিতি নকশা করা প্রশস্ত কপাল থেকে শুধু পেছনে ফেলে আসা অনেকটা সময় নয়, যেন তার থেকেও আরও বেশি কিছুর আভাস পাওয়া যায়। ওস্তাদকে ফজল কেবল তিন-চার বছর হল দেখছে... তার আগে সেও চিনত না এই আজিজ কে।
আজিজও কি জানে এই ফজলের সব নাড়ি-নক্ষত্র? দেখে কাজের ছেলে বলেই মনে হয়, আর নিজের এই মানুষ-চেনা নজরের ওপর ভরসা করেই রেখে নিয়েছে সঙ্গে। তারপর একসাথেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা... বারাসাত, কালিয়াচক, মেটিয়াবুরুজ, নাজিরগঞ্জ... তারপর আরও ক্রমশ ভাসতে ভাসতে অমুক পুর, তমুক নগর হয়ে এই করিমগঞ্জের এসে আস্তানা বেঁধেছে তারা। বাঁশের পোলের ওপারে তাঁতিপাড়ার কাছেই কোথাও একটা আস্তানা দু’জনের... ওস্তাদ আর তার স্যাঙাৎ। আর সপ্তাহে দু’তিন বার তাদের দেখা মেলে ওই মোরশেদ ফকিরের দরগার সামনে... অশ্বত্থ গাছের নীচে।
গানের ওস্তাদরা যেমন রেওয়াজ করে, ঠিক সেইরকম আজিজ ওস্তাদের রেওয়াজের সময় থাকে… নিশুত রাতে। স্থির দৃষ্টিতে শুধু তার হাত আর হাতের সামনে খেলা দেখানোর জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে থাকে। কপালে ঘামের ফোঁটা জমে নাকের ওপর গড়িয়ে পড়লেও, তা মুছবে না– এমনই মনসংযোগ। হাতের কাজ দেখলেই বোঝা যায়, বেশ উঁচু দরের শিল্পী। কেন যে এখানে মরতে পড়ে আছে, ফজল ভেবে পায় না। এই প্রাণবন্ত আঙুলগুলো আর এই একাগ্র চোখের সম্মোহনই ফজলকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে এসেছে সেই বারাসাত থেকে এই করিমগঞ্জে। ওস্তাদকে এই সময় ডাকারও সাহস হয় না ফজলের। ওস্তাদ একদম ভেতর থেকে আসলি বনজারা, কোনওদিনও কোথাও তার শেকড় গজাবে না... আর গজালেও তা মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার আগেই ওস্তাদ নিজেকে উপড়ে নিয়ে যাবে অন্য কোথাও – এ’কথা বেশ ভালো টের পায় ফজল। এই যে খেলা দেখিয়ে টাকা, একটা ছাউনিতে খাটিয়ার ওপর ওস্তাদ আর নীচে মাদুর পেতে ফজল... এ সবই নেহাৎ দিনগুজরান। আজিজ যতটা উদাসীন... ফজল ততটা নয়... হারিকেনের আলোয় সারাদিনের জমানো টাকার বখরা ভাগ হওয়ার সময়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে ফজলের চোখ। হয়ত আর একটু ভালো ভাবে বাঁচার ইচ্ছে থেকেই… হয়ত তার থেকে কিছু বেশি।
একটা মাস-মাইনের চাকরি, টালি কিংবা অ্যাসবেস্টসের চাল... শহরের কাছাকাছি। একবার কোনও হোটেলের ফাই-ফরমাশ খাটার কাজে লেগেছিল, সেখানে থেকে গেলে এতদিনে বেশ নিজের নাম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে পারত। কিন্তু টিকতে পারল কই? নিজের মর্জি মতো কিছু করার তাগিদটাও যে কিছুতেই পিছু ছাড়ে না! আজিজের সঙ্গে অল্প ভাব জমিয়ে বুঝতে পেরেছিল, সেই হোটেলের চাকরি থেকে বেরোনোর প্রথম ধাপই এই ওস্তাদ। এমন কলাকার লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে এমন কিছু এমনিতেই শেখা হয়ে যায়, যা হোটেলের টেবিল মুছতে মুছতে জানতেই পারবে না কোনওদিন। শিখেওছে অনেক কিছু।
রাত গভীর হলে, হারিকেনের আলোয়ে আজিজের খয়েরি চোখের মণি যখন এক মন দিয়ে একের পর এক তাস গায়েব করতে করতে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়... সেই কারচুপির ধরার চেষ্টা করতে করতে কোথায় যেন তলিয়ে যায় ফজল। কাচের ঘরের ভেতর আগুনের শিখাটা একের পর এক অন্যরকম কিছু বাজিকরের খেলা দেখাতে থাকে চোখের সামনে। ঘর বলে কোনওদিন যাদের কিছু থাকেনি, তাদের কাছে ঘর শব্দের মানেটাই সময়ে সময়ে এই ভাবে পালটে যায়। তবু কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে ফজল... বাইরে নিস্তব্ধ রাত, ছাউনির ভেতর ছায়াবাজী। করিমগঞ্জের রজনীর আনসুনি দাস্তাঁ।
ওস্তাদ বলে, “বুঝলি ফজ্লে... আমাদের লাইনে লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে নেই... তফাৎ রেখে থাকতে হয়। বেশি গা সওয়া হয়ে গেলে… কোনো খেলাই দিমাগের ওপর আর অসর করে না।” ওস্তাদের হুকুম, ফজলও যেন কারও সাথে বেশি মেলামেশা না করে। আস্তানা বাঁধলেও করিমগঞ্জের তারা কেউ নয়।
ফজলেরও এখানকার কোনও কিছুই ঠিক পোশায় না। মানুষগুলো এক যুগ পেছনে পড়ে আছে যেন। সকলের হাতে হাতে মোবাইল ফোন দেখা যায় না। হাটে বাজারে কোনও কোনও দোকানে রেডিও-ক্যাসেটে খুব জোরে যা গান বাজে, সে সব পুরনো। সিনেমা হল সেই পনেরো মাইল দূরে, টাউনে। দিশী মদের ঠেক সন্ধ্যের পর রমরমিয়ে চলে… সেখান থেকেই ব্র্যান্ডেড মালও কেনা-বেচা হয়। বড়ো বাবু, মেজো বাবুরা নিজে না এলেও কনস্টেবল জয়নুল কাগজে মুড়ে বোতল নিয়ে যায়... এসব কিছুই ফজলের অজানা নয়। তবু সে দূরে দূরেই থাকে। ওই দরকার মতো চালটা, নুনটা... হাটে গেলে আলু-পেঁয়াজ... এই সবের মধ্যে যা অল্প কথাবার্তা। আর নামাজে গেলে যা পাড়ার মুরুব্বি মাতব্বরদের সঙ্গে আজিজের মোলাকাৎ হয়, ফজলও পরোক্ষ ভাবে তার অংশ হয়ে থাকে। হঠাৎ করে কোনও বুজুরগের সঙ্গে চোখাচুখি হয়... কেউ কেউ মেপে নেয় সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে। ছোটো ছেলেগুলো ঘিরে ধরে ‘চাচু ম্যাজিক দেখাও’ বলে। সমবয়সীরা কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে… নেশাভাঙের আড্ডায় ডাকে। তবে ফজল মনে রাখে– সে এই করিমগঞ্জের কেউ নয়, নিজেকে সরিয়ে রাখে সতর্ক ভাবেই।
মিলেমিশে যেতে জানলে, সহজে টিকে থাকা যায়... তবে সকলের মাঝেও নিজেকে আলাদা করে রাখতে জানলে, অনেক কিছুই বোঝা যায়... যা তাদের একজন হয়ে গেলে আর বোঝা যায় না। ঠিক অনেকটা নিজে দাবা খেলা... আর পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে অন্য দু’জনকে দাবা খেলতে দেখার মতন। এমনকি আসতে আসতে আজিজের সঙ্গেও নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার একতা মানসিক প্রক্রিয়া মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আজকাল। নানারকম পরিকল্পনা নদীর ঢেউয়ের মতো চিন্তার ধাপগুলোতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে যায়। হয়ত তার বেশির ভাগটাই আকাশ-কুসুম... তবু ফজল জানে... এই করিমগঞ্জ ফজলের জায়গা নয়। এই জাদুকর আজিজ তার মসীহা নয়, জরিয়া মাত্র। চিন্তাগুলো লাট্টুর মতো পথে পথে ঘোরে, মশার মতো অন্ধকার ঘরে ওরে, হারিকেনের কমিয়ে দেওয়া আলোর মতো ক্রমশ ধুঁকতে ধুঁকতে হারিয়ে যায় প্রতি রাতে।
একটা দাগকে না মুছেই আরো একটা লম্বা দাগ টেনে তাকে ছোটো করে দেওয়া হয়।
একটা পুরনো ইমারৎ, স্রেফ অযত্নে ফেলে রেখেই ভগ্নাবশেষ বানিয়ে দেওয়া যায়।
একটা পুকুরে নিয়মিত পাড়ার জঞ্জাল ফেলেফেলেই বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।
নিয়মিত কিছু অসত্য শেখাতে শেখাতেই তাকে সঠিক তথ্য বলে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যায়।
আরো বর্ণাঢ্য উৎসব, আর বেশি উদযাপনের ব্যবহারিক প্রয়োগে ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা… এমনকি কোনো একটি বা দুটি পরিবারের শোকও চাপা দিয়ে দেওয়া যায়।
একটা মরশুম থেকে আর একটা মরশুমে চলে যায় সব কিছু… মাঝে আবোলতাবোল খেলা ভণ্ডুল করা ব্যাপার। সেসব ছু মন্তর বলে কাপড় উড়িয়ে গায়েব করে দিতে পারে দক্ষ জাদুকর।
এই সব কিছুর প্রশিক্ষণ শুরু হয় কোনো না কোনো গাছের তলায় বসেই। কারো না কারো কাছে তালিম পেয়ে, বাকি নিজের কেরামতি আর হাতযশ।
আজিজ যা পারে, তা-ও খুব সামান্য আর সস্তা মনে হয় সেই সব বড়ো কারামাতের কাছে। গভীর রাতে হারিকেনের নিভু নিভু আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে আজিজ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে, একটা বড়ো কিছু ভেঙে দিয়ে আরো বড়ো কিছু যা বানিয়েছে… সে যতই বিশালই হোক, তাকেও গায়েব করে দেওয়ার কোনো তর্কীব থাকবে! আরো বড়ো জাদুকর নিশ্চয়ই জানে সেই তর্কীব। হাতো কী সাফাই আর আঁখো কী ধোকার ওপরেই দুনিয়া কায়েম হ্যায়। যা কিছু হচ্ছে, আসলে সব অন্য কিছু ঘটছে… আর অন্য কিছু দেখছে-জানছে মানুষ। তরক্কী করতে গেলে আরো বড়ো জাদুকরের সংগত করতে হয়। এই ডালভাতের জীবন তার চলে যাবে। কিন্তু ফজলের চোখ ফুটে গেছে… সে আরো বড়ো কারামাতের কাছে ঠিক যেতে চাইবে। সে নিজেই ফজলকে শিখিয়েছে– টান রাখতে নেই। অথচ…
একদিন শুয়ে শুয়ে রাতের অন্ধকারে আজিজ হঠাৎই জিজ্ঞেস করে ফেলল—
আচ্ছা ফজলে, আমাদেরও যদি একদিন বেরহেমি সে পিটিয়ে মেরে দেয়…
কী দেখে মারবে… কী খাই দেখে? না আমরা এভাবে থাকি দেখে?
সেই রাতটা অন্যরকম কোনো কোনো রাতের মতো, যে রাতগুলোতে ওস্তাদও ফজলের সঙ্গে নীচে মাদুরে শোয়।
ফজল গভীর ঘুমের মধ্যে উট, আতর আর জাফরান দেওয়া বিরিয়ানির স্বপ্ন দেখে। কতটা কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্নটা করছে ওস্তাদ… বুঝতে পারে না।
(৩)
গপ্পের কাগজে চিৎকার ছাপতে গিয়ে শীৎকার ছেপে দিয়ে একবার হেব্বি কেলো হয়েছিল। অল্প বয়সী পোলাপান। সব মাল নষ্ট। চিৎকার বলতে মনে পড়ে গেল– বুক ফাটিয়ে চিৎকার করল তিনটা প্রাণী। কুকুরের চিৎকার কুকুর শুনতে পেল। কাকের চিৎকার কাকে শুনতে পেল…কিন্তু মানুষের চিৎকার মানুষ শুনতে পায় না!
তৃতীয় শো
দ্য এন্ডলেস সার্কাস
“ওই দেখ... বুড়ির মাথার পাকা চুল! খাবি?”
প্লাস্টিকের প্যাকেট-এ গোল গোল... সাদা, গোলাপী, হলুদ তুলোর বলের মতো। সেই দিকেই ছুটে গেল মেয়ে দু’টো। অসমবয়সী বন্ধু, বড়ো মেয়েটির নাম আফরোজা... স্কুল ফাইনাল দেবে সামনের বছর। ছোটো মেয়েটি আফসারা… আফরোজাদের পাড়ায় থাকে। আফসারার কিছুকাল আগে অবধি রূপকথার গল্প, পরী-জ্বীনদের গল্প শুনতে ভালো লাগত, জানত— শেষে শাহজাদারা জিতে যাবে, দুষ্টুরা মরে যাবে। সেই ভালো লাগা নিয়ে ঘুমোলে সুন্দর খোয়াব দেখা যায়। কিন্তু এখন নতুন ভালো লাগা আসছে… টিভিতে বাংলা ধারাবাহিক, বাংলা সিনেমা।
আফরোজারও টিভি সিরিয়াল দেখতে ভালো লাগে, সিরিয়ালের অভিনেত্রীদের মতো সাজতে ইচ্ছে হয়… পারে না। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে মোটা করে কাজল লাগায়, ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক দেয়। যখন যে সিরিয়ালের মুখটা ভালো লাগে, সেরকম। আম্মি জানলে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আব্বু জানলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এমনিতেই দাদি বলছে মেয়েকে আর স্কুলে না পাঠিয়ে চটপট নিকাহ্ দিয়ে দে। আফরোজার মতো মেয়েকে নিজের ছেলের বিবি হিসেবে দেখতে চাইবে না, এমন পরিবার পাওয়া মুশকিল। শুধু সময়ের ব্যাপার, অনেকের ফুফা-খালা এসে ফিরোজার আম্মিকে মাঝে মাঝে বলে যায়… ‘কী ভাবলে জানিও, তোমাদের মেয়েকে একেবারে কলিজা করে রাখব।’
অথচ আফসারা সেই ছোট্ট মেয়েটি, যার জ্বিন-পরীদের কিস্সা শুনতে ভালো লাগত। তার কাছে এই ধারাবাহিকের জগৎটাই অন্যরকম একেবারে অন্যরকম মানুষ, অন্যরকম ঘরবাড়ি, অন্যরকম অন্দরমহল… অন্যরকম গল্প। আফসারার দেখা চারপাশের সঙ্গে মেলে না। দাদি-আম্মির কাছে শোনা গল্পগুলোর মতো নয়; অন্য রকম। আর আফরোজা ভালোলাগার কাছাকাছি থাকতে থাকতেই আরও বেশি করে ভালো লেগে গেছে এই রঙিন টিভির পর্দায় দেখা রঙিন জীবনের গল্পগুলো। কান্না, হাসি, ঝগড়া, উজ্জ্বল সাজ… একটা নেশ ধরে যায় দেখতে দেখতে– সন্ধ্যে হলে এসে দেখতে হবে, তারপর কী হ’ল?
‘কী রে… খাবি? দু’খান গোলাপী কিনি?’
ফিরোজাকে বোরখা পরতে হয় এখন, যদিও কালো বোরখার মুখটা খোলাই রাখে। আফসারাকেও পরতে হবে কয়ক বছর পর… এখন নীল ফুল ফুল ফ্রক, শুধু মাথায় ওড়নাঢাকা। বোরখা পরলে আগের মতো দৌড়ে যেতে একটু অসুবিধে হয়, না হলে প্রশ্নটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ওই ফেরিওয়ালার কাছে ছুটে চলে যেত ফিরোজা। কিন্তু এখন ছোটা যায় না, আম্মিও মানা করে। বুড়ির মাথার পাকাচুলের অনেকগুলো প্যাকেট একটা বাঁশের লাঠিতে বেঁধে সাইকেল নিয়ে রাস্তার উলটোদিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। সেই দিকেই আফসারার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল ফিরোজা, ছুটতে পারছিল না। চাইছিল কিন্তু পারছিল না। ওদের আসতে দেখে ফেরিওয়ালাটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। সেও সাইকেলের স্ট্যান্ড নামিয়ে দাঁড়াল।
রাস্তাটা পার হ’তে যাবে, ঠিক সেই সময়ে সার্কাসের ক্লাউনের মতো মুখোশ পরে দুটো লোক একটা বাইকে করে দ্রুত গতিতে এলো, আর চলে গেল… বোমারু বিমানের মতো। সাইকেলটা পড়ে গেল রাস্তার ধারে। ফেরিওয়ালাটা মুখ থুবড়ে পড়ল একটা চাপা শব্দ করে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পিঠ। তখনও মুখ থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে। সাপে ব্যাঙ ধরলে যেমন আওয়াজ করে ব্যাঙ, সেইরকম আওয়াজ মনে হল ফিরোজার। আফসারার হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কী করে কী হ’ল বুঝতে পারেনি আফসারা, ওরা হাতটা কাঁপছে। হলুদ-গোলাপী-সাদা বুড়ির মাথার পাকাচুল ভরা প্যাকেটগুলো রাস্তায় পড়ে আছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে আফসারা।
আওয়াজটা থেমে গেল। কুরবানীর গোস্তের মতো পড়ে আছে ফেরিওয়ালার রক্তাক্ত দেহ। বোর্খার নিচের দিকটা বাঁ হাত দিয়ে লুঙ্গির মতো তুলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল ফিরোজা। ডানহাতে আফসারার হাত শক্ত করে ধরে যত জোড়ে পারে দৌড়োতে শুরু করল কোনও দিকে না তাকিয়ে। আফসারার কান্না, বা তার নিজের আতঙ্কে ভরা মুখ দেখে কে কী ভাবতে পারে… সেই নিয়ে এতটুকু ফালতু চিন্তা না করা নিজেদের পাড়ার দিকে ছুটতে লাগল রুদ্ধশ্বাস।
রেসের মাঠে সীমারেখার মতো টাঙিয়ে রাখা একটা ব্যানারের নীচ দিয়ে ছুটে চলে যায় রুদ্ধশ্বাস… মন্ত্রী আসছেন দুদিন পর। মন্ত্রী হাসছেন হাত-জড়ো করে। গ্রাম হাসছে… শহর হাসছে…
দুটো ক্লাউন, বুড়ির মাথার পাকা চুলের মতোই নানা রঙের বল নিয়ে, বিচ্ছিন্ন ঘটনার মতো জাগলিং করে যাচ্ছে মৃতদেহ ঘিরে।
তাদের নিয়ে জাগলিং করে যাচ্ছে আরো বড়ো বাজিকর। তাদের নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে অন্য কেউ।
Juggled by the Juggled by the Juggled… Surreal Loop.
সে এক বীভৎস সার্কাসের বিস্তৃত এবং দীর্ঘ লাইভ পারফর্মেন্স।
পারিশ্রমিক দেওয়া নেওয়ার মাঝেও বিনোদন থেমে থাকে না।
বুড়ির মাথার পাকাচুলের প্যাকেটগুলো পড়ে থাকে। আর কিছু না পাক, ওইগুলো নিয়ে যাবে ‘সার্কামস্টানশিয়াল এভিডেন্স বলে’। হয় খেয়ে নেবে, না হলে ফেলে দেবে। উবে যাবে হাওয়ায়…



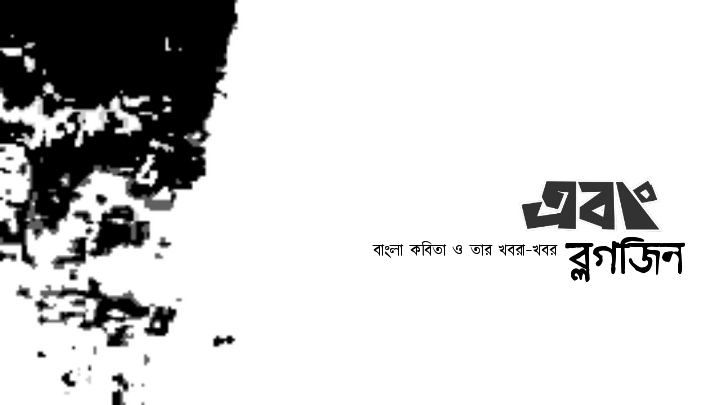
Comments