কবিতা বিষয়ক গদ্য —
প্রেম মানব জীবনের সর্বাত্মক এক অনুভূতি। এই অনুভূতি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সিনেমায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রেমের নানান ফর্ম ,আবেগ,রং,রূপ আমরা সিনেমার জন্মলগ্ন থেকে রূপালি পর্দায় দেখে এসেছি। সিনেমার প্রধান থিম হিসেবে 'প্রেম' শাশ্বত এবং বহুল ব্যবহৃত।
মানুষ-মানুষীর রোমান্টিক প্রেম (Eros Love) ছাড়াও অবসেসিভ ম্যানিয়াক প্রেম,লুডাস লাভ অর্থাৎ প্রেম-প্রেম খেলা যেখানে খুব সিরিয়াস ঘনিষ্ঠতা নেই, Agape love অর্থাৎ কিনা কোনোকিছুর আশা না করেই শুধু দেবার মাঝে আনন্দ পায় প্রেমিক/প্রেমিকা। একে অন্যের জন্য ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। অথবা প্লেটোনিক প্রেম যেখানে আত্মিক সম্পর্কটাই মূল। শারীরিক তাড়না বিশেষ থাকে না সেখানে। সিনেমাটিক ক্যানভাসে আমরা প্রেমের নানান প্রকাশ দেখে এসেছি আজ অব্দি। রোমান্টিক রিয়েলিজম যেসব সিনেমায় দেখা গেছে ,যেখানে খুব সুখকর পরিণতির দিকে কাহিনী সবসময় মোড় নেয়নি, চরিত্রের রসায়ন যেখানে অত্যন্ত ইডিওসিনক্র্যাটিক , escapist fantasy যেসব সিনেমায় দেখা যায় না তেমনই কয়েকটি ব্যক্তিগত পছন্দের সিনেমায় প্রেমের চিত্রায়ণ বিষয়ে আমার এই আলোচনা ।
Rob Reiner নির্মিত When Harry met Sally (1989) ছবির মূল বিবেচ্য বিষয়টি ছিল একজন পুরুষ এবং নারীর মাঝে আদৌ কি প্লেটোনিক প্রেম থাকা সম্ভব , যেখানে যৌন চেতনা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ! ছবির একটি ক্লাসিক সংলাপ " Men and women can't be friends because the sex part always gets in the way” । প্রেম ও যৌনতা কী তাহলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ! অভ্যাস না আবেগ ,কার প্রতিক্রিয়া অধিক এই জীবনে ? হ্যারি আর স্যালির দীর্ঘ এগারো বছর প্লেটোনিক সম্পর্ক একসময় শেষ হয়, তাদের সেই সম্পর্কে একদিন যৌনতার প্রবেশ ঘটে। হ্যারির হেটেরোনরমেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি, হ্যারি বিশ্বাস করে যে সমস্ত পুরুষই সমস্ত মহিলার প্রতি শুধু যে আকৃষ্ট হয় তাই নয়, এই আকর্ষণ যেকোনো ধরনের প্লেটোনিক সম্পর্ককে বস্তুত অসম্ভব করে তোলে। অপরদিকে স্যালি সাধারণত যৌনতার দিকে কম মনোনিবেশ করে এবং প্লেটোনিক বন্ধুত্বের প্রতি অনেক বেশি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, তবে যৌনতাকে সে-ও কিছুটা গুরুত্ব দেয়। সে বিশ্বাস করে বিবাহিত সম্পর্ক অধিকাংশই "অতি-বিঘ্নিত", কারণ তার ধারণা বিবাহিত দম্পতিরা সচরাচর নিয়মিত যৌন সম্পর্ক করে না !
কবি দেবারতি মিত্রের ‘ভূতেরা ও খুকী’ কাব্যগ্রন্থের ‘ঝরণার সোনা’ কবিতার কিছুটা পড়া যাক
“ ঘোর কদমের মাসে
তার সঙ্গে বিয়েভাঙ্গা স্কার্ফখোলা চটুল বত্রিশ
গাড়ি ছাড়বার আগে লাফাতে লাফাতে যেন চাকা ছুটে আসে,
মেয়েলি ঘাড়ের হাড়ে বেঁধে গিয়ে তুরপুনের মতো প্রজাপতি,
জড়াজড়ি মুঠোভর্তি স্বাদুমাংস রান্নার আগুন,
আঠায় মধুতে ঠোঁট স্ট্রবেরি জারানো দামী নুন।
রুমাল নাচিয়ে বলে মহিলাটি, ‘চলো যাই, সিংহের কেশর ধরে
ঝাঁকিয়ে
আসিগে,
ভবিষ্যৎ টাইগনের মতো হবে অথবা সফল।”
অপূর্ব কুশলতায় কবিতাটির ভেতর রয়েছে অন্তর্লীন যৌনতা। ‘বিয়েভাঙ্গা চটুল বত্রিশ’, ‘সিংহের কেশর ধরে ঝাঁকানো’, ‘ভবিষ্যৎ টাইগনের মতো’ প্রভৃতি শব্দবন্ধ গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বহন করে। যৌনতা ধারণাটিকে ব্যাপক অর্থে সম্প্রসারিত করেন ফ্রয়েড। তাঁর মতে নরনারীর ভালোবাসার সহজাত সব প্রবৃত্তির সংহত ও মিলিত রূপই হচ্ছে লিবিডো বা কামপ্রবৃত্তি। এমন কি মানবপ্রেম, আত্মপ্রেম, বন্ধুত্ব, বাৎসল্য, অপত্য সবকিছুর পেছনেই রয়েছে লিবিডোর উপস্থিতি।
When Harry met Sally সিনেমাটির সবচেয়ে হেটেরোনরমেটিভ ও নেগেটিভ দিকটি হলো এই যে ছবিতে হেটেরোসেক্সুয়াল বিবাহকে একটি সর্বজনীন সম্পর্ক এবং একমাত্র প্রয়োজন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । সিনেমাটি এমন হেটেরোসেক্সুয়াল বিবাহিত দম্পতিদের ছোট ছোট অসংখ্য দৃশ্যে ভরা।
প্রাচীন গ্রিক মিথ থেকে শুরু করে শেক্সপিয়রের নাটকে সমকামিতা বা সমকামী প্রেম আন্ডারকারেন্ট হিসেবে রয়ে গেছে , যেহেতু তৎকালীন সমাজে সমকামী প্রেম এক বিরাট ট্যাবু ছিল । এমন একটি ছবি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যা সমকামী প্রেমের স্টিরিওটাইপ চলচ্চিত্রায়ণ ভেঙে দর্শকদের মনে চিরতরে স্থান করে নেয়, Brokeback Mountain (2005) , এলজিবিটি সিনেমার একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে ছবিটি প্রশংসিত এবং যা সমকামী অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । দুই তরুণ এনিস ডেল ও জ্যাক টুইস্ট গ্রীষ্মকালীন ব্রোকব্যাক পর্বতে ভেড়া চরানোর কাজে নেমে দিনের পর দিন একসঙ্গে কাটাতে কাটাতে একে অপরের প্রতি মানসিক ও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করে। গল্পের প্রেক্ষাপট 1963 সালের আমেরিকা ,যেখানে তখন সমকামী সম্পর্ক ছিল ভীষণ অপরাধের বিষয়। ফলে সামাজিক চাপ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সর্বোপরি নিজেদের ভিতরে চলা দ্বন্দ্ব এই প্রেমের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে বাধা দেয়।
এনিস যেন সেই টক্সিক মাসকুলিনিটির খাঁচায় বন্দি , দ্বিধান্বিত তার অভিব্যক্তি । নিষিদ্ধ প্রেমের উদ্দাম অন্তর্নিহিত প্রবাহ চলে । এনিস - জ্যাক একে অপরের তবু প্রেমে পড়তে পারে না। কোনোমতেই সম্ভব না যেহেতু । তাই সেই ক্ষীণ সত্যকে বাঁচতে কোনো এক অরণ্য ঘেরা জলাশয়ে, বিচ্ছিন্নতায়,একান্তে ওরা মাছ ধরতে যায় । সমাজের নিষিদ্ধ প্রেমকে ওরা স্বীকৃতি দেয় এইভাবে। এনিসের ছেলেবেলায় দেখা এক নিহত 'gay' মানুষের কথা মনে পড়ে যায় , যে দৃশ্যটি তাকে বারবার সাবধান করে দেয় । বলে যায় 'সমকামিতা পাপ',বলে যায় 'don't be gay or this will happen to you'।
আধুনিক কালের অন্যতম কবি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ' বান্ধবীবিহার' কবিতাটি এই নিষিদ্ধ প্রেম ও তার অপরাধচেতনার এক সমান্তরাল সুস্পষ্টতা , গণ্ডি ভাঙার প্রবণতা দেখাচ্ছে যেন
কবি বলছেন :
Rob Reiner নির্মিত When Harry met Sally (1989) ছবির মূল বিবেচ্য বিষয়টি ছিল একজন পুরুষ এবং নারীর মাঝে আদৌ কি প্লেটোনিক প্রেম থাকা সম্ভব , যেখানে যৌন চেতনা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ! ছবির একটি ক্লাসিক সংলাপ " Men and women can't be friends because the sex part always gets in the way” । প্রেম ও যৌনতা কী তাহলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ! অভ্যাস না আবেগ ,কার প্রতিক্রিয়া অধিক এই জীবনে ? হ্যারি আর স্যালির দীর্ঘ এগারো বছর প্লেটোনিক সম্পর্ক একসময় শেষ হয়, তাদের সেই সম্পর্কে একদিন যৌনতার প্রবেশ ঘটে। হ্যারির হেটেরোনরমেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি, হ্যারি বিশ্বাস করে যে সমস্ত পুরুষই সমস্ত মহিলার প্রতি শুধু যে আকৃষ্ট হয় তাই নয়, এই আকর্ষণ যেকোনো ধরনের প্লেটোনিক সম্পর্ককে বস্তুত অসম্ভব করে তোলে। অপরদিকে স্যালি সাধারণত যৌনতার দিকে কম মনোনিবেশ করে এবং প্লেটোনিক বন্ধুত্বের প্রতি অনেক বেশি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, তবে যৌনতাকে সে-ও কিছুটা গুরুত্ব দেয়। সে বিশ্বাস করে বিবাহিত সম্পর্ক অধিকাংশই "অতি-বিঘ্নিত", কারণ তার ধারণা বিবাহিত দম্পতিরা সচরাচর নিয়মিত যৌন সম্পর্ক করে না !
কবি দেবারতি মিত্রের ‘ভূতেরা ও খুকী’ কাব্যগ্রন্থের ‘ঝরণার সোনা’ কবিতার কিছুটা পড়া যাক
“ ঘোর কদমের মাসে
তার সঙ্গে বিয়েভাঙ্গা স্কার্ফখোলা চটুল বত্রিশ
গাড়ি ছাড়বার আগে লাফাতে লাফাতে যেন চাকা ছুটে আসে,
মেয়েলি ঘাড়ের হাড়ে বেঁধে গিয়ে তুরপুনের মতো প্রজাপতি,
জড়াজড়ি মুঠোভর্তি স্বাদুমাংস রান্নার আগুন,
আঠায় মধুতে ঠোঁট স্ট্রবেরি জারানো দামী নুন।
রুমাল নাচিয়ে বলে মহিলাটি, ‘চলো যাই, সিংহের কেশর ধরে
ঝাঁকিয়ে
আসিগে,
ভবিষ্যৎ টাইগনের মতো হবে অথবা সফল।”
অপূর্ব কুশলতায় কবিতাটির ভেতর রয়েছে অন্তর্লীন যৌনতা। ‘বিয়েভাঙ্গা চটুল বত্রিশ’, ‘সিংহের কেশর ধরে ঝাঁকানো’, ‘ভবিষ্যৎ টাইগনের মতো’ প্রভৃতি শব্দবন্ধ গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বহন করে। যৌনতা ধারণাটিকে ব্যাপক অর্থে সম্প্রসারিত করেন ফ্রয়েড। তাঁর মতে নরনারীর ভালোবাসার সহজাত সব প্রবৃত্তির সংহত ও মিলিত রূপই হচ্ছে লিবিডো বা কামপ্রবৃত্তি। এমন কি মানবপ্রেম, আত্মপ্রেম, বন্ধুত্ব, বাৎসল্য, অপত্য সবকিছুর পেছনেই রয়েছে লিবিডোর উপস্থিতি।
When Harry met Sally সিনেমাটির সবচেয়ে হেটেরোনরমেটিভ ও নেগেটিভ দিকটি হলো এই যে ছবিতে হেটেরোসেক্সুয়াল বিবাহকে একটি সর্বজনীন সম্পর্ক এবং একমাত্র প্রয়োজন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । সিনেমাটি এমন হেটেরোসেক্সুয়াল বিবাহিত দম্পতিদের ছোট ছোট অসংখ্য দৃশ্যে ভরা।
প্রাচীন গ্রিক মিথ থেকে শুরু করে শেক্সপিয়রের নাটকে সমকামিতা বা সমকামী প্রেম আন্ডারকারেন্ট হিসেবে রয়ে গেছে , যেহেতু তৎকালীন সমাজে সমকামী প্রেম এক বিরাট ট্যাবু ছিল । এমন একটি ছবি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যা সমকামী প্রেমের স্টিরিওটাইপ চলচ্চিত্রায়ণ ভেঙে দর্শকদের মনে চিরতরে স্থান করে নেয়, Brokeback Mountain (2005) , এলজিবিটি সিনেমার একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে ছবিটি প্রশংসিত এবং যা সমকামী অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । দুই তরুণ এনিস ডেল ও জ্যাক টুইস্ট গ্রীষ্মকালীন ব্রোকব্যাক পর্বতে ভেড়া চরানোর কাজে নেমে দিনের পর দিন একসঙ্গে কাটাতে কাটাতে একে অপরের প্রতি মানসিক ও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করে। গল্পের প্রেক্ষাপট 1963 সালের আমেরিকা ,যেখানে তখন সমকামী সম্পর্ক ছিল ভীষণ অপরাধের বিষয়। ফলে সামাজিক চাপ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সর্বোপরি নিজেদের ভিতরে চলা দ্বন্দ্ব এই প্রেমের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে বাধা দেয়।
এনিস যেন সেই টক্সিক মাসকুলিনিটির খাঁচায় বন্দি , দ্বিধান্বিত তার অভিব্যক্তি । নিষিদ্ধ প্রেমের উদ্দাম অন্তর্নিহিত প্রবাহ চলে । এনিস - জ্যাক একে অপরের তবু প্রেমে পড়তে পারে না। কোনোমতেই সম্ভব না যেহেতু । তাই সেই ক্ষীণ সত্যকে বাঁচতে কোনো এক অরণ্য ঘেরা জলাশয়ে, বিচ্ছিন্নতায়,একান্তে ওরা মাছ ধরতে যায় । সমাজের নিষিদ্ধ প্রেমকে ওরা স্বীকৃতি দেয় এইভাবে। এনিসের ছেলেবেলায় দেখা এক নিহত 'gay' মানুষের কথা মনে পড়ে যায় , যে দৃশ্যটি তাকে বারবার সাবধান করে দেয় । বলে যায় 'সমকামিতা পাপ',বলে যায় 'don't be gay or this will happen to you'।
আধুনিক কালের অন্যতম কবি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ' বান্ধবীবিহার' কবিতাটি এই নিষিদ্ধ প্রেম ও তার অপরাধচেতনার এক সমান্তরাল সুস্পষ্টতা , গণ্ডি ভাঙার প্রবণতা দেখাচ্ছে যেন
কবি বলছেন :
“ ব্যত্যয় নেই কোনও ! আমি
জানি, তোকে ভালবাসি, তাই এ–জগত
মধুময় লাগে। আয়োজনে, যদি কিছু
বিরোধিতা জাগে ! খুনি বোমা বেঁধে
চলে, কোকিল লুকিয়ে কাঁদে
বসন্তগোড়ায়, দুধে–বিষে মিশে গেলে,
তখন সমাজ, খোলা বাথরুম হয়ে,
যায় ! … দরোজা দিয়েছি, জানলাও,
আমাদের ঘরে মধুঘুম নামবে, বল
সখি, মম সঙ্গে লিভ–ইন করবে কি”।
মানুষের মনের প্রেম-প্রবৃত্তির যৌনরূপ রক্ষণশীলতার ঘের থেকে বেরোচ্ছে বৈকি! ব্রোকব্যাক মাউন্টেনের এনিস ও জ্যাকের সমলৈঙ্গিক প্রেম পূর্ণতা পায় নি,ছবিটির শেষ অংশে জ্যাকের মৃত্যু এনিসকে গভীরভাবে আঘাত করে। এনিস তার জ্যাকেটের ভেতর জ্যাকের শার্ট রেখে দেয়, যা তাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের একটি প্রতীক হয়ে থাকে। প্রথমদিকের সিনেমায় সমকামিতা অত্যন্ত নেতিবাচক ভঙ্গিমায় চিত্রায়িত হতো,Brokeback Mountain-এ সমকামী প্রেমের নান্দনিকতা , মর্মস্পর্শী এই উপস্থাপন সত্যিই অবিস্মরণীয়।
আরেকটি সিনেমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 2017 সালের ছবি 'Call Me by Your Name' । সমকামী সম্পর্কের অতি-স্পর্শকাতরতা,আবেগ এবং সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের আরো সহনশীল,আরো সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলে সিনেমাটি। ইলিও, একজন ষোলো বছর বয়সী ইতালীয় কিশোর, তার পরিবারের সাথে উত্তর ইতালিতে একটি গ্রীষ্মকালীন বাড়িতে ছুটি কাটাতে যায় । তার বাবা প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক, একজন আমেরিকান গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অলিভিয়ারকে নিজের গবেষণার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই সুযোগে ইলিও এবং অলিভিয়ারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । তারা একসাথে সাঁতার কাটে,সাইকেল চালায়,স্থানীয় বাজারে যায়,রাতে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দেয়। ইলিও অলিভারের প্রতি ক্রমে আসক্ত হয় । অথচ এর পরিণাম কী ? অলিভিয়ারের গবেষণা শেষ হলেই তো তাকে ফিরে যেতে হবে !
একদিন স্থানীয় ডাকঘরে যাওয়ার সময় ইলিও পরোক্ষভাবে অলিভারের প্রতি তার অনুভূতির কথা স্বীকার করে। অলিভার প্রথমে তার এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। তাই সেই দিন , আরো পরে, দু’জন দু’জনকে চুম্বন করলেও অলিভার এর বেশি এগোতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে দু ’জনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অলিভিয়ার চলে গেলে ইলিওকে , এই প্রথম প্রেমের স্মৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
এই সিনেমাটি এক ক্ষণস্থায়ী দূর স্মৃতির মতো মনে হয়, একই সাথে খুব স্পষ্ট অথচ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। অলিভারের সাথে আরেকটা স্মৃতিবহুল উদ্বায়ী গ্রীষ্মে কী আবার ফেরা যায় ? যায় না । অলিভারের বিয়ে ঠিক হয়েছে। জানা যায়। ইলিও সেই অতিবাহিত দূরগামী গ্রীষ্মের উত্তাপের খোঁজে নিঃস্ব হয়, অন্তরে । শীত ঋতু আসন্ন। শীত , বিবর্ণ , সাদা প্রান্তরে শুধু ফেলে আসা গ্রীষ্মের বর্ণিল উচ্ছ্বাস চাপা পড়ে ,মুছে যায় ক্রমে। ফায়ারপ্লেসের আগুনের গৈরিক উত্তাপ ঝলসে ওঠে ইলিওর দু'চোখ ভরা অশ্রুতে। সেই দু'চোখ আমাদের চোখ বুজতে বলে ,দেখতে বলে যা কিছু আমাদের দেখার ওইপারে।
“পরিণামহীন ,শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা
আমাদের সমস্ত জীবন ধরে ছায়া ফেলে ছাতিমের মতো ।”
(প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)
Call Me by Your Name" সিনেমাটি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ,আসক্তি, প্রথম প্রেম এবং হৃদয়বেদনার বিরল স্বাক্ষর হয়ে থেকে যায় । মূলত সিনেমাটি আমাদের প্রাচীন দ্বিধার উত্তর খুঁজে যায় যেন ... যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে তা বলে ওঠার সাহস পায় না, তখন "Is it better to speak or die?”
মানব-মানবীর প্রেম তো ঢের হয় কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রণয় , প্রেম ! আধুনিক সময়ের একাকীত্বের ফলস্বরূপ প্রযুক্তি এবং মানবিক সংযোগের ,এমনকি আবেগ বিনিময়ের এক অনন্য রূপ আমরা দেখতে পাই 2013 সালের Her নামক সিনেমাটিতে।
থিওডোর , যিনি অন্যের জন্য ব্যক্তিগত চিঠি লেখার কাজ করেন। সম্প্রতি তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এবং তিনি গভীরভাবে একাকী বোধ করেন। এই সময় তিনি এক উন্নত অপারেটিং সিস্টেম, "সামান্থা" কিনে নেন। সামান্থা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা ইউজারের সাথে যোগাযোগ করে, শেখে এবং ক্রমবিকশিত হয়।
থিওডোর এবং সামান্থার কৃত্রিম স্বরের মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যা ধীরে ধীরে একপ্রকার প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়। সামান্থার সাথে থিওডোরের সম্পর্ক তার জীবনে নতুন আনন্দ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আসে। তিনি আবার জীবনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তার সৃজনশীলতা ফিরে পান।
সামান্থার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত বিকশিত হতে থাকে এবং সে মানুষের চেয়েও অনেক দ্রুত শিখে ফেলে । সামান্থা অনেক ইউজারের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের সাথেও একইরকম সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে থিওডোর ঈর্ষান্বিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। থিওডোরের মানবোচিত complex emotion এবং সামান্থার শারীরিক সান্ত্বনা প্রদানের অক্ষমতা এই প্রেমের ক্ষেত্রে এক অনন্য জটিলতা নিয়ে আসে। সামান্থা থিওডোরের সাথে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য একজন সারোগেট মানব সঙ্গীকে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করেছিল, যা থিওডোরকে গভীরভাবে বিরক্ত করেছিল এবং এই মুহূর্তটি সম্পর্কের একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে প্রমাণিত হয়। ছবিটি আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে এই সম্পর্কের কিছু অস্বাভাবিকতা আরো তীব্র মনে হতে থাকে এবং শারীরিক দেহ না থাকার সমস্যা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় ।
একদিন সামান্থা সংক্ষিপ্তভাবে অফলাইনে চলে গেলে থিওডোর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে আসে সে এবং জানায় যে একটি আপগ্রেডের জন্য অন্যান্য O.S.-এ যোগদান করতে হচ্ছে যা তাদের processing -এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাইরে নিয়ে যাবে। সামান্থা ক্রমে সচেতনতা অর্জন করে এবং একদিন থিওডোরকে ছেড়ে চলে যায়। থিওডোর গভীরভাবে আহত হলেও, ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেন যে সামান্থা তার জন্য হয়তো সঠিক ছিল না। সামান্থার কাছে হিউম্যান একটা বিস্তৃত সাবজেক্ট,যাকে পড়া যায়,বোঝার চেষ্টা করা যায় ,মাঝখানে তবু থেকে যায় অন্তহীন শূন্যস্থান ।
“তুমি এত ভুলো...
সপ্তাহান্তে দূরে-টুরে যেতে হলে রকেটে জ্বালানি
ঠিকমতো নিও কিন্তু। ভয় করে, তোমাকে তো জানি!
ড্রয়ারে চাবিটা রাখছি। মিলির রিমোট।
রোবটমানবী ভেবে অগ্রাহ্য কোরো না। ওর চোখ নাক ঠোঁট আমারই আদলে তৈরি,
মনে রেখো। রোজ চার্জ দিয়ো।
আমার অবর্তমানে ও-ই দেখেশুনে নেবে
ঘরদোর, গৃহস্থালি, লৌকিকতা, প্রেম-ট্রেম-যা যা করণীয়।”
(কবিতা : চলে আসার আগে,কবি: রাকা দাশগুপ্ত)
প্রেম দুই ভিন্ন মানুষকে কাছে আনে,ভিন্ন স্বভাব,ভিন্ন চাওয়া-পাওয়া,ভালোলাগার ভিন্ন প্রকাশ। আমাদের পার্থক্যের অনন্যতাই বস্তুত প্রেমের সকল অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি গড়ে তোলে । এক্ষেত্রে একজন মানুষ এবং a.i -এর physical difference সেই বিভেদের অনন্যতাকে গাঢ় করে বৈকি ! সামান্থা এক sexish কম্পিউটার প্রোগ্রাম যাকে কোনো কোম্পানির প্রোগ্রামার-রা সৃষ্টি করেছেন ব্যবসায়িক তাগিদে । তার অনুভূতির যান্ত্রিকতা সেই পথেই চলে যেমনটা তার প্রোগ্রামাররা চায় বা চেয়েছে । সামান্থার যদি কোন insecurity থেকে থাকে তবে তা হলো তার মানবিক মূল্যবোধের অভাব । সামান্থা একদিন থিওডোরকে প্রশ্ন করে "Are these feelings even real or are they just programming?" অনুভূতির সততায় সে যেতে চায় কিন্তু এই ধারনার প্রতিবন্ধকতা তাকে হতাশ করে মুহুর্মুহু । এমন স্থান-কালহীন অস্তিত্বের সাথে প্রেম কে হয়তো সহজে ভরসা হয় না । থিওডোর তাই আত্মদ্বন্দ্বে ভোগে । সামান্তার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থিওডোরের মধ্যে যে আতঙ্ক, হতাশা এবং উদ্বেগ দেখা দেয়, তা সবচেয়ে স্পর্শযোগ্য মনে হয়েছে । ছবির এই মুহূর্তটি মানুষ এবং এআই-এর বিচ্ছেদের সারাংশ সফলভাবে তুলে ধরে।
“আপাতত চলি।
সুদূর কৈশোর থেকে কোনও এক অনুজ্জ্বল স্কুল বাস, মফস্সল গলি-
রাস্তা ভুলে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে, শুধুমাত্র আমাকেই নিতে
এসে গেছে। তোমাদের দৃপ্ত পৃথিবীতে
আমার ফুরোল দিন। থাকার উপায় নেই আর।
অন্য কোনও দেশ-কালে দেখা হবে কখনও, আবার।”
(কবিতা : চলে আসার আগে,কবি: রাকা দাশগুপ্ত)
এই অভিনব প্রেম দর্শকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যায় , যেমন থিওডোর ও সামান্থার সম্পর্কটি রক্তমাংসের প্রকৃত মানবীর সাথে থিওডোরের নতুন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কি বাধাস্বরূপ! একজন মানুষ এবং একটি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম সত্যিই কি সব দিক থেকে পরিপূর্ণ কোনো আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলতে পারে ! সামান্থা এক নিখুঁত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, A perfect being in an imperfect world,সামান্থার সাথে সর্বগ্রাসকারী এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের ভবিতব্য কী ? অস্পর্শযোগ্য,যান্ত্রিক অথচ অবসাদ-ভোলানো এক ডিভা রূপে ‘সামান্থা’ থিওডোরের জীবনে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেছিল। সেই মানবোচিত অবসাদের কিছু অংশ হয়তো সে নিজের সাথেও খানিকটা নিয়ে গেলো,নিজের অংশ হিসেবে।
“ক্যাসিনোর এক কোণে নীল কফিশপ; আমি কি
তাহলে সেই মৃত শহরের বাধ্যত-আবিষ্কারক, যে শুধু
বুঝেছে তুমি ক্যাসিনোর ডিভা, অবসাদে আত্মহত্যাকারী
উঠে এসে টেবিলে বসেছ
আমি কি চেয়েছি সেই টি-পটে জড়ানো মৃত
আমি কি চেয়েছি সেই টি-পটে জড়ানো মৃত
প্রেমিকার শাদা ও শীর্ণ আঙুল”
(অন্ধকার, সামগাথা কবি : পার্থজিৎ চন্দ)
গ্রিক শব্দ Storge , প্রাকৃতিক সহজাত এবং পারিবারিক ভালবাসাকে বোঝায় যেখানে একে অপরের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী commitment দেখা যায়। সুস্থ সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে এই Storge love . একে familial love-ও বলা হয়ে থাকে। অতীত ভারতে পারিবারিক প্রেম ও পরিবার গঠনের যৌথতা এই stroge love এর এক্সটেনশন হিসেবে ভাবা যেতে পারে ।
মীরা নায়ারের The Namesake ছবিটি শুরু হয় একটি ট্রেন দুর্ঘটনার সাথে । বছরটি 1974 । অশোক গঙ্গোপাধ্যায়( ইরফান খান) একজন aspiring engineer এবং রাশিয়ান সাহিত্যপ্রেমী । কলকাতা থেকে জামশেদপুরে দাদুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য ট্রেন যাত্রা করছিলেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনো হয় না আর। নিকোলাই গোগোলের হতভাগ্য প্রোটাগনিস্টে মজে থাকার মুহূর্তে সহসা ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং সেই থেকে অশোকের জীবনের গতিপথ বদলে যায়। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বকে যে শুধুমাত্র বই পড়ার মাধ্যমে জেনে এসেছেন -" travel without moving an inch" যেমনটি তার দাদু বলতেন,দুর্ঘটনার পর তিনি তার সহযাত্রী মিঃ ঘোষের পরামর্শ মতো ( see the world- you will never regret it) গৃহত্যাগী হয়ে বিদেশে যাওয়া মনস্থির করলেন। পরবর্তীতে অশোক তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী অসীমাকেও (তাবু ) তার পরিচিত পারিবারিক বাঙালি জীবন থেকে নিউইয়র্কের শীতল অপরিচিত জীবনে সরিয়ে নিয়ে যায়।
বিবাহের পর প্রথম শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্যটিতে অদ্ভুত নিরীহতা লক্ষ্য করা যায়। আবছায়া আলোয় অশোকের হাত অল্প অল্প করে অসীমার ছয় গজ শাড়ির মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে যায়। দৃশ্যটি সাবলীল,সংক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে অশোক ও অসীমার আমেরিকা আবিষ্কারের সমান্তরালে তাদের প্রেম আরো বিকশিত হয় । তারা তাদের ছেলের নাম রাখলেন গোগল, অশোকের প্রিয় লেখকের নাম অনুসারে। আমরা গোগলকে একজন আমেরিকান হয়ে বড় হতে দেখি, যে তার শিকড় অনেক বছর পর ভারত ভ্রমণের সুযোগে প্রথমবার উপলব্ধি করতে শুরু করে।
আমি এই প্রবন্ধের পরিসর অনুযায়ী ছবিটির ডিটেলে আর যাব না। তবে অশোক ও অসীমার প্রেম আর বিবাহ এক ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে নিষ্ঠা ও companionship এর গভীর অনুভূতি বিরাজ করতো । তাদের প্রেমের ভিত্তি ছিল ভারতে কাটানো তাদের যৌথ অতীত সময়কাল। অপরদিকে তাদের সন্তান গোগল একাধিক নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় । গোগল প্রেমকে ব্যবহার করে নিজের অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, নিজের স্বকীয় পরিচয় গড়ে তুলতে। সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের দিকে সেই ক্রম-উত্তরণ,জেনারেশন গ্যাপের প্রখর অভিব্যক্তি,অস্থিরতা,যেখানে ঠুনকো মনে হয় যেকোনো ধরনের প্রাচীনতা,সাবেকি প্রেম আমাদের পিতা-মাতার কিংবা পূর্বপুরুষের ।
“তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন
বিজলি এখন পোড়াচ্ছে ঘর
তোমার-আমার মধ্যে ছিলো অগ্নিস্বাক্ষী ভয়ের পাথর
এখন পাথর গুঁড়িয়ে গিয়ে করছে মাটি
তোমার খেলা বলতে ছিলো চু-কপাটি
এখন খেলা বদলে গেছে, খেলা একার
তোমার-আমার ছোট্ট সে-ঘর আজকে দেখার
সময় পেলাম, ছোট্ট সময়।”
( তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন
- শক্তি চট্টোপাধ্যায় )
অশোক ও অসীমার জন্য, বিয়ে স্বাধীনতা অর্জন বা পরিচয় গঠনের কোনো অনুশীলন ছিল না, বরং জীবন যাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল, যা সাহচর্যের দিকে , পরিবার গঠনের দিকে তাদের উভয়কেই পরিচালিত করেছিল।
ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক কাল্ট ক্লাসিক। সিনেমার প্রোটাগনিস্ট নীতা সর্বংসহা,বলিদানের প্রতিমূর্তি,দেবী-সমা নারী,যার ভালত্বকে আদর্শের সংজ্ঞা দিয়েছে আমাদের সমাজ। বাঙালি আট দশটা মেয়ের মতোই 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির নীতা । সাদামাটা নম্র ভদ্র শিক্ষিত। প্রকৃতির ঘুরপাকেই প্রেম আসে নীতার জীবনে । ছেলে মেধাবী সৎ এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ভালো ডিগ্রীধারী । নীতার স্বপ্ন সনৎ গবেষনা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে , তাই চাকরি বাকরি এখনই তার জন্যে না । নীতা টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে সনৎকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে । নীতাও এম.এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।নীতার বাবা স্ট্রোকে অচল হয়ে যান । সংসারের হাল নীতার ঘাড়েই চেপে বসে । নীতার বাধ্য হয়েই একটা চাকরি নিতেই হয় । প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা অফিস করতে করতে নীতাও কেমন জানি হয়ে যায় । সনৎও নীতার চাকরি করা মেনে নিতে পারেনা ! ইতিমধ্যে নীতা বিবাহপ্রসঙ্গে সনৎকে বলে 'অপেক্ষা করতে হবে'। কী নমনীয় ঋজু সেই বলা ।
নীতা তার দাদাকে প্রসঙ্গক্রমে বলে -' যদি কেউ ভালবাসে,যদি সত্যিই বাসে তাহলে সে অপেক্ষা করবেই'। কী নমনীয় ঋজু সেই বলা । নীতা তার দাদাকে প্রসঙ্গক্রমে বলে -' যদি কেউ ভালবাসে,যদি সত্যিই বাসে তাহলে সে অপেক্ষা করবেই'।
(অন্ধকার, সামগাথা কবি : পার্থজিৎ চন্দ)
গ্রিক শব্দ Storge , প্রাকৃতিক সহজাত এবং পারিবারিক ভালবাসাকে বোঝায় যেখানে একে অপরের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী commitment দেখা যায়। সুস্থ সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে এই Storge love . একে familial love-ও বলা হয়ে থাকে। অতীত ভারতে পারিবারিক প্রেম ও পরিবার গঠনের যৌথতা এই stroge love এর এক্সটেনশন হিসেবে ভাবা যেতে পারে ।
মীরা নায়ারের The Namesake ছবিটি শুরু হয় একটি ট্রেন দুর্ঘটনার সাথে । বছরটি 1974 । অশোক গঙ্গোপাধ্যায়( ইরফান খান) একজন aspiring engineer এবং রাশিয়ান সাহিত্যপ্রেমী । কলকাতা থেকে জামশেদপুরে দাদুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য ট্রেন যাত্রা করছিলেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনো হয় না আর। নিকোলাই গোগোলের হতভাগ্য প্রোটাগনিস্টে মজে থাকার মুহূর্তে সহসা ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং সেই থেকে অশোকের জীবনের গতিপথ বদলে যায়। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বকে যে শুধুমাত্র বই পড়ার মাধ্যমে জেনে এসেছেন -" travel without moving an inch" যেমনটি তার দাদু বলতেন,দুর্ঘটনার পর তিনি তার সহযাত্রী মিঃ ঘোষের পরামর্শ মতো ( see the world- you will never regret it) গৃহত্যাগী হয়ে বিদেশে যাওয়া মনস্থির করলেন। পরবর্তীতে অশোক তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী অসীমাকেও (তাবু ) তার পরিচিত পারিবারিক বাঙালি জীবন থেকে নিউইয়র্কের শীতল অপরিচিত জীবনে সরিয়ে নিয়ে যায়।
বিবাহের পর প্রথম শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্যটিতে অদ্ভুত নিরীহতা লক্ষ্য করা যায়। আবছায়া আলোয় অশোকের হাত অল্প অল্প করে অসীমার ছয় গজ শাড়ির মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে যায়। দৃশ্যটি সাবলীল,সংক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে অশোক ও অসীমার আমেরিকা আবিষ্কারের সমান্তরালে তাদের প্রেম আরো বিকশিত হয় । তারা তাদের ছেলের নাম রাখলেন গোগল, অশোকের প্রিয় লেখকের নাম অনুসারে। আমরা গোগলকে একজন আমেরিকান হয়ে বড় হতে দেখি, যে তার শিকড় অনেক বছর পর ভারত ভ্রমণের সুযোগে প্রথমবার উপলব্ধি করতে শুরু করে।
আমি এই প্রবন্ধের পরিসর অনুযায়ী ছবিটির ডিটেলে আর যাব না। তবে অশোক ও অসীমার প্রেম আর বিবাহ এক ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে নিষ্ঠা ও companionship এর গভীর অনুভূতি বিরাজ করতো । তাদের প্রেমের ভিত্তি ছিল ভারতে কাটানো তাদের যৌথ অতীত সময়কাল। অপরদিকে তাদের সন্তান গোগল একাধিক নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় । গোগল প্রেমকে ব্যবহার করে নিজের অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, নিজের স্বকীয় পরিচয় গড়ে তুলতে। সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের দিকে সেই ক্রম-উত্তরণ,জেনারেশন গ্যাপের প্রখর অভিব্যক্তি,অস্থিরতা,যেখানে ঠুনকো মনে হয় যেকোনো ধরনের প্রাচীনতা,সাবেকি প্রেম আমাদের পিতা-মাতার কিংবা পূর্বপুরুষের ।
“তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন
বিজলি এখন পোড়াচ্ছে ঘর
তোমার-আমার মধ্যে ছিলো অগ্নিস্বাক্ষী ভয়ের পাথর
এখন পাথর গুঁড়িয়ে গিয়ে করছে মাটি
তোমার খেলা বলতে ছিলো চু-কপাটি
এখন খেলা বদলে গেছে, খেলা একার
তোমার-আমার ছোট্ট সে-ঘর আজকে দেখার
সময় পেলাম, ছোট্ট সময়।”
( তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন
- শক্তি চট্টোপাধ্যায় )
অশোক ও অসীমার জন্য, বিয়ে স্বাধীনতা অর্জন বা পরিচয় গঠনের কোনো অনুশীলন ছিল না, বরং জীবন যাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল, যা সাহচর্যের দিকে , পরিবার গঠনের দিকে তাদের উভয়কেই পরিচালিত করেছিল।
ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক কাল্ট ক্লাসিক। সিনেমার প্রোটাগনিস্ট নীতা সর্বংসহা,বলিদানের প্রতিমূর্তি,দেবী-সমা নারী,যার ভালত্বকে আদর্শের সংজ্ঞা দিয়েছে আমাদের সমাজ। বাঙালি আট দশটা মেয়ের মতোই 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির নীতা । সাদামাটা নম্র ভদ্র শিক্ষিত। প্রকৃতির ঘুরপাকেই প্রেম আসে নীতার জীবনে । ছেলে মেধাবী সৎ এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ভালো ডিগ্রীধারী । নীতার স্বপ্ন সনৎ গবেষনা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে , তাই চাকরি বাকরি এখনই তার জন্যে না । নীতা টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে সনৎকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে । নীতাও এম.এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।নীতার বাবা স্ট্রোকে অচল হয়ে যান । সংসারের হাল নীতার ঘাড়েই চেপে বসে । নীতার বাধ্য হয়েই একটা চাকরি নিতেই হয় । প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা অফিস করতে করতে নীতাও কেমন জানি হয়ে যায় । সনৎও নীতার চাকরি করা মেনে নিতে পারেনা ! ইতিমধ্যে নীতা বিবাহপ্রসঙ্গে সনৎকে বলে 'অপেক্ষা করতে হবে'। কী নমনীয় ঋজু সেই বলা ।
নীতা তার দাদাকে প্রসঙ্গক্রমে বলে -' যদি কেউ ভালবাসে,যদি সত্যিই বাসে তাহলে সে অপেক্ষা করবেই'। কী নমনীয় ঋজু সেই বলা । নীতা তার দাদাকে প্রসঙ্গক্রমে বলে -' যদি কেউ ভালবাসে,যদি সত্যিই বাসে তাহলে সে অপেক্ষা করবেই'।
"স্বপ্নের সমুদ্র সে কী ভয়ংকর,ঢেউহীন,শব্দহীন,যেন
তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে,হারানো
আংটির মতো
দূরে তোমার দিগন্ত"
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীতাদের সংসারে সেই সংসারের হাল ধরবে তা না নীতা ক্যান সংসারের ঘানি টানবে , এই যুক্তি সনতের কিন্তু নীতা যে উমা! তার কী কোনো যুক্তি থাকে ! নীতার কথা একটাই 'আমি করবো না তো কে করবে । বেশ তো আমার জন্যে একটা কাঠের একটা বাক্স বানাও তাতে আমাকে আটকে রাখো ।'
সনতও বদলে যায় , জানে উমাকে ভালবেসে পুজো দেয়া যায় স্ত্রী করা যায়না ! তাইতো নীতার বোন গীতাকে হুটহাট বিয়ে করে বসে ।
নীতা প্রবন্ধের প্রথমে আলোচিত সেই Agape love এর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। ভেতর ভেতর দগ্ধ , পিষ্ট হলেও সংসার ঘানি টেনে যায়। দুঃখের কথা কাউকেই বলতে নেই । নীতা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়,সব দৈনন্দিনতা থেকে ছুটি নিয়ে অনেক দূরে চলে যায় এবং সিনেমা শেষে তার সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ
'দাদা আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম ... !আমি বাঁচতে চাই দাদা...আমার যে বাঁচার বড় শখ দাদা... ' শংকর শুধু প্রতি উত্তরে বলে 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি ! '
আত্মত্যাগী প্রেম বা self-sacrifing প্রেমের প্রতিমূর্তি হয়ে থেকে যায় নীতা ।
চলচ্চিত্রের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার আত্মত্যাগী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে সে টিউশনের মাধ্যমে উপার্জন করা সামান্য টাকাটাও নিজের ছেঁড়া চটির বদলে নতুন চটি না নিয়ে খরচ করে ভাইবোনদের জন্য। সনৎ যখন বেকার থাকে,তখনও নীতা তাকেও আর্থিকভাবে সাহায্য করে । নীতা যেন সেই গ্রিক ট্র্যাজেডির এপিক হিরো ।কিন্তু সে দেবী না,উমা না,সে তীব্র সংবেদী এক মানবী। সে ভালোবেসেছিল সনৎকে,পাগলের মতো ভালবেসেছিল জীবনকে । জীবনের দৈনন্দিনতাকে ।
গ্রাম্য বালিকা নস্টালজিক উঠোনেতে মাখা জোছনায়
বুকের ভিতর কষ্ট আটকে দু'চোখের জল মোছ না!
খাতা লেনদেন মন দেয়ানেয়া খুনসুটি আর পদ্য।
চুলের ফিতেয় বিকেলের রোদ ঝরে ঝরে পড়ে সদ্য।
নিষেধাজ্ঞার পাঁচিল ডিঙিয়ে স্বপ্ন দেখার স্পর্ধায়
দু'জনাতে মিলে টান দিয়ে ছিঁড়ি অন্ধকারের পর্দা।
চল্ মেয়ে চল্ হেঁটে হেঁটে যাই ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধে,
যৌথ সফরে দু'হাতে সরাই যত আছে অবরুদ্ধ।
(চল্ মেয়ে চল্ কবি: সব্যসাচী গোস্বামী)




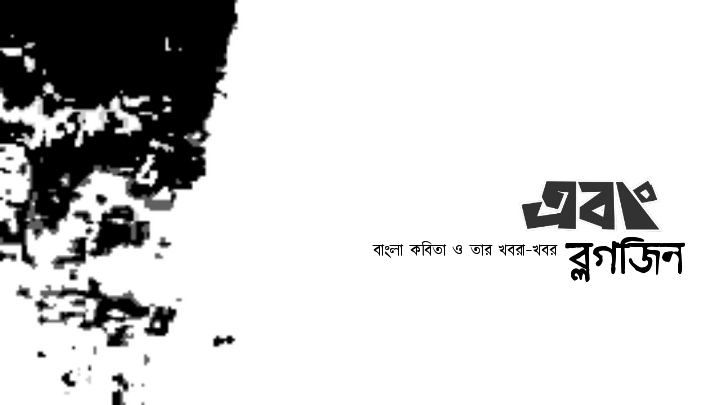
Comments