প্রচ্ছদ আখ্যান
“এখন তো জলই নেই, আগে কতবার বন্যা হয়েছে। আমাদের আটচালা অবধি জল থইথই করত। কত মাছ চারদিকে! মাছ ধরার ওটাই তো সময়।” জাল বুনতে বুনতে বলত দাদু। “এখন হাঁটু অবধিও জল ওঠে না। মাছটাছ আর নেই। ওই দহগুলোতেই এখন মাছ ধরে সবাই। কিন্তু কোথায় মাছ!”
বন্যার বিভীষিকা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকা শিশুমন বন্যার জন্য আকুল হয়ে উঠত। আহা, যদি আবার বন্যা হত, মাছ ধরতে ছুটতাম দাদুর সঙ্গে! যার জন্য কাঁসাইয়ে এখন জল নেই, সেই মুকুটমণিপুরের বাঁধটি হয়ে উঠত চক্ষুশূল।
দাদু জাল নিয়ে চলত ছানাতুপার দিকে। পিছনে আমি। উৎসাহে, আনন্দে আত্মহারা।
ছানাতুপা জায়গাটা ছিল গ্রামের বাইরে, হাঁটা পথ, মিনিট দশেকের বা আরেকটু বেশি। সেই যুগে কারোর হাতেই ঘড়ি নেই। ঘড়ি পরার চলও ছিল না। গ্রামের সময় চলত প্রকৃতির নির্দেশে। তাই দশ মিনিট না আধ ঘণ্টা, তা আজ আর মনে পড়ে না। তাছাড়া সময় কেটে যেত দাদুর নানা গল্পে। সে রূপকথাই হোক বা লোকগাথা, বা শুধুই মনগড়া গল্প। দাদুর গল্প আর আমার প্রশ্ন থামতই না।
তবু “ছানাতুপার নাম ছানাতুপা কেন?” এই প্রশ্ন ওই ছোট বয়সে মাথায় আসেনি। আসলে নিশ্চইয় জিজ্ঞেস করতাম। বা করতাম না হয়তো। না জানি কোন ছানাকে পুঁতে রেখেছিল ওখানে! ভয় ভয় করত ছানাতুপার দিকে একা যেতে, কিন্তু নিজেকে আটকানোও যেত না।
ছানাতুপা একটি বিশাল জায়গা, যাকে বলে আমাদের ‘বাঞ্ছারামের বাগান’। কত বিঘা চাষের জমি ছিল সেটাও আর মনে নেই। অনেক সেগুন গাছ দিয়ে ঘেরা ছিল। ছিল সবজির জমি। আর কয়েকটা ছোটোখাটো পুকুর। আদতে এমন কিছুই না, কিন্তু বেশ একটা জমিদার জমিদার ভাব হতো ওখানে গেলে।
ছানাতুপার ওই সব ছোট পুকুরগুলোতেই আমরা যেতাম মাছ ধরতে। কিছু পুকুর ছিল শালুকভর্তি। সেগুলোতে জাল ফেলা যেত না। দাদু তখন আমায় বঁড়শি ধরিয়ে দিত। সারা দুপুর আমরা মাছ ধরে কাটাতাম।
ফেরার পথে এক জায়গায় এসে দাদু দাঁড়িয়ে যেত। বলত, “গড় কর।”
আমি হাতজোড় করে প্রণাম করতাম। একটা গাছ আর কিছু ঝোপ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ত না। তবু, প্রণাম করতাম।
দাদুর কাছে নরসিংহ আর প্রহ্লাদের গল্প শুনেছি। ভগবান যে সব কিছুতেই বিদ্যমান সেটাও বিশ্বাস করতাম। তাই প্রণাম করতাম। তবে ‘গড় করা’ যাকে বলে ঠিক ততটা ঝুঁকে না, অল্প ঝুঁকে। তাই ধরাও পড়ে যেতাম। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে অনেক প্রশ্নও থাকত যে।
দাদু আমার ইতস্তত ভাবটা ধরতে পেরে বলত, “এখানে তোর বাবা ঠাকুর পেয়েছিল। ওই গাছটার নিচে। মাটি খুঁড়ে হাতি-ঘোড়ার মূর্তি পেয়েছিল। এখন আর এখানে নেই, ঠাকুরের থানে রাখা আছে, পরে নিয়ে যাব।”
মনে হাজারটা প্রশ্নের উদয় হত। বাঁকুড়ায় বাড়ি অথচ মাটির হাতিঘোড়া দেখেনি এমন হয়তো কেউই নেই। আমিও দেখেছি। কিন্তু মাটির তলা থেকে? মাটি খুঁড়ে মাটির তলা থেকেও জিনিস পাওয়া যায়? এমন আশ্চর্যজনক কথা এর আগে শুনিনি।
মনে নেই কত পরে কিন্তু পরে সেই হাতিঘোড়ার মূর্তি দেখেছিলাম। খুব সাধারণ, মাটির তৈরি ছোট্ট ছোট্ট হাতিঘোড়ার মূর্তি। বিভিন্ন আকারের অসংখ্য হাতিঘোড়ার মাঝে ঠিক কোন দু'টো তা ঠাওর করতে না পারলেও, ছোট ছোট কোনো দু'টো হবে আন্দাজ করেছিলাম। ধর্মঠাকুরের থানে তখন পুজো চলছে। আমি সেই কোলাহল কাটিয়ে মদনডিহির দিকে হাঁটা লাগাতাম।
“যে ঠাকুর যা চায়, তাই দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। আমাদের কেমন পাঁঠা বলি হয় কালীপূজায়।” আমার মোটেও পছন্দ ছিল না পাঁঠা বলি দেওয়া। পুজোর অনেক আগে থেকেই একটা ছাগলকে এনে রাখা হতো। তাকে রোজ খেতে দেওয়া, চরতে নিয়ে যাওয়া। অনেক সময় এই সব কাজ আমিও করতাম। আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যেত পাঁঠাটির। কালীপুজোর রাতে যখন বেচারাকে বলির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, মনটা বড্ড খারাপ হতো। ওর আর্তচিৎকার কানে আটকে থাকত। আমি ওই রাতের অন্ধকারেই নদীর দিকে হাঁটা লাগাতাম।
কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে খুব বেশি দূর যেতে পারতাম না। কালীপুজোর কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই দূর থেকে ধামসা-মাদলের আওয়াজ ভেসে আসত। অন্ধকারে অসমান মোরাম ফেলা পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে শাল-পলাশের গাছগুলোকে মনে হতো আস্ত ভূতের দল। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন তালে বিভিন্ন লয়ে বেজে চলা নানান বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে শুনতে নিজেকে বেশ ভূতেদের রাজা বলে মনে হয়। চোখ বন্ধ করে সেই জলসা উপভোগ করার চেষ্টা করতাম, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করতাম। মন ও শরীর— দুটোই খানিকটা হালকা লাগত।
তবে এই অনুভূতি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না। ঘাড়ের উপর কার যেন নিঃশ্বাস পড়ত। ঘুরে তাকাতেই এক বিকট মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতাম। দেখতাম ভূতটাও একই রকম আঁতকে উঠে ‘উঞ্চা উঞ্চা পাবত, উঞ্চা উঞ্চা পাবত’ করতে করতে ছুটছে উল্টো দিকে। ওকে ছুটতে দেখে আমি থেমে যেতাম।
“কই দেখাও দেখি একটা?”
প্রতিবেশীর সেই অসামান্য সংগ্রহ দেখে আমারও খুব শখ হয়েছিল মূর্তি খোঁজার। কিন্তু পাইনি। অনেক খুঁজেও পাইনি। উঞ্চাও পায়নি। দুই হতভাগ্য প্রস্পেক্টর রাঢ়বঙ্গের ধূলিধূসরিত নদীতটে বিকেলটা কাটিয়ে দিত টলটলে স্বচ্ছ জলে গোড়ালি ভিজিয়ে। ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি সব কিছু শুষে নিয়ে কাঁসাই বয়ে যেত নিজের পথে। সেই সব সোনালি বিকেলগুলোতে উঞ্চাকে বড্ড নিজের লোক মনে হতো।
আজও সেই সব দিনের কথা যখন ভাবি উঞ্চার কথা খুব মনে পড়ে। ওকে দেখতেও যেন ওই মূর্তিগুলোর মতোই ছিল। যেন একই রকম কালো পাথরে বানানো। চোখের কোণে একই রকম প্রশান্তি চিকচিক করত ওর। সামনের কিছু দাঁত ভাঙা ছিল ঠিকই তবু ঠোঁটে লেগে থাকত একই রকমের স্মিতহাসি।
খুঁজে পেয়েছিলাম আমার ছোটবেলায় দেখা মাটির ঘোড়াগুলোরও। সিন্ধুসভ্যতার মহেঞ্জোদারো ও লোথাল অঞ্চলে একই রকম ঘোড়ার মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল।
খোঁজ পেয়েছিলাম মার্বেলেরও। সিন্ধুসভ্যতার বাচ্চারাও আমাদের মতো মার্বেল নিয়ে খেলত। মহেঞ্জোদারোয় পাওয়া গিয়েছিল পাথরের ছোট ছোট মার্বেল। সেই হরবোলাকে আর বলা হয়নি, কিন্তু মার্বেলের নাম মার্বেল কারণ একসময় এগুলো কাঁচের না হয়ে মার্বেল পাথরেরই হতো।
এই রকম ছোট ছোট পাথরের গোলক মিশরেও পাওয়া গিয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতি গোলকগুলোকে গোলক বানানো হয়েছিল ঘষে ঘষে। নিজের থেকেই পাথরগুলো গোল ছিল না। এর চেয়ে খানিকটা বড় আকারের, প্রায় ক্রিকেট বলের আকারের চুনাপাথরের গোলক পাওয়া গেছে ইজরায়েলের উবেইদিয়া অঞ্চলে। সেগুলোর বয়স শুনলে হতবাক হতে হয়। প্রায় ১৪ লক্ষ বছর আগেকার। এবং সেগুলোকেও কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে ধীরে গোলোকে পরিণত করেছে।
এই গোলকগুলোর ব্যবহার কী ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু চুনাপাথর নয়, চকমকি পাথর ও ব্যাসাল্টেরও গোলক পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে অসংখ্য হ্যান্ডঅ্যাক্স-এর সঙ্গে। হ্যান্ডঅ্যাক্স বলতে পাথরের তৈরি হাতলবিহীন কুঠার, দেখতে গাছের পাতা বা অশ্রুবিন্দুর মতো। এর দুই ধার সাধারণ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। এগুলো প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত হাতের মুঠোয় ধরে তাই নাম হ্যান্ডঅ্যাক্স।
হ্যান্ডঅ্যাক্স নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে ফেরা যাক রহস্যময় গোলকগুলো নিয়ে। অনেকের ধারণা এগুলোকে গোলার মতো ব্যবহার করা হতো, শিকারের সময় দূর থেকে ছুঁড়ে মারার জন্য। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একদম নিটোলভাবে গোল করার দরকার হয়তো ছিল না। কিন্তু সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকতা হয়তো মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই ছিল। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে মানুষ বলতে শুধু হোমো সেপিয়েন্সদের কথা ভাবলে চলবে না। কারণ যে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলের কথা হচ্ছে সেটি প্রায় ১৪ লক্ষ বছর আগের আর হোমো সেপিয়েন্সের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ বছর আগে। অবশ্য সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা বলছে এই সময়কাল পিছিয়ে প্রায় ৪ লক্ষ বছর হতে পারে। তাই ১৪ লক্ষ বছর আগে হোমো সেপিয়েন্সদের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেক্টাসরা ওই গোলকগুলো বানিয়েছিল।
উদাহরণস্বরূপ মাকাপান উপত্যকার একটি বিশেষ নুড়িপাথর। এটি একটি ছোট লাল রঙের পাথর। এটি যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেই প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের মধ্যে লাল রঙের এই পাথরটিকে পাওয়া এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার কারণ ওই জায়গায় আর কোনো লাল জেসপারাইট পাথর নেই। সবচেয়ে কাছে যেটা আছে সেটাও ৩ মাইল দূরে। অর্থাৎ কেউ একজন এই বিশেষ পাথরটিকে বয়ে নিয়ে এসেছিল সযত্নে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই পাথরটি শুধু লালই নয়, সঙ্গে ভালো করে লক্ষ করলে চোখ-মুখও দেখা যায়। কিন্তু এর কোনোটাই জোর করে বানানো নয়, প্রাকৃতিকভাবেই তৈরী হওয়া। অর্থাৎ আমাদের মতোই, আমাদের পূর্বপুরুষ কেউ একজন সুন্দর একটি নুড়িপাথর দেখে টুক করে তুলে নিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাসায়, সযত্নে রেখেছিল তাকে।
এই নান্দনিক বোধের প্রসঙ্গে আরেকটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিই। একটু আগেই আমরা হ্যান্ডঅ্যাক্সের কথা বলছিলাম। এই প্রকার অস্ত্র মনুষ্যপ্রজাতি প্রায় ১৬ লক্ষ বছর আগে থেকে ব্যবহার করছে। ১৪ লক্ষ বছর আগে এই অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মূলত হোমো ইরেক্টাসরাই এই অস্ত্র ব্যবহার করত, হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যে এর ব্যবহার কমই দেখা যায়। নানান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এই পাথরের অস্ত্রগুলো খুব নিখুঁত করে বানানো হয়েছে। যদি এই অস্ত্রগুলোকে বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য শিকার করাই হয় তাহলে অতটা নিখুঁত সুষম করে বানানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু মানুষ সেটাই করত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানান হ্যান্ডঅ্যাক্সের মধ্যে এমনও মিল দেখা গেছে যে সন্দেহ হয় সেগুলো একজন শিল্পীরই বানানো কিনা। এখানে খুব সচেতনভাবেই কারিগরের জায়গায় শিল্পী বললাম, কারণ সেই হ্যান্ডঅ্যাক্সগুলো এতটাই সুন্দর যে কোনো শৈল্পিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এগুলো বানানো সম্ভব।
আরোও এক চমৎকার হ্যান্ডঅ্যাক্স পাওয়া গেছে ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট টফ্ট এলাকা থেকে যার বয়স ৩ থেকে ৫ লক্ষ বছর। এই হ্যান্ডঅ্যাক্সটি অস্ত্র হিসেবে কতটা কার্যকরী ছিল সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কিন্তু এটিকে একবার দেখলেই বোঝা যায় এইটিকে বানানোর উদ্দেশ্য আর যাই হোক শিকার করা ছিল না। অন্তত আমি হলে তো এটাকে ঘরে সাজিয়ে রাখতাম।
শুধু এই অস্ত্রটি একটামাত্র উদাহরণ হলে হয়তো একে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নেওয়াই যেত। কিন্তু শুধু এটি নয়, আরও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অস্ত্রগুলো এতটাই যত্ন নিয়ে বানানো যে সেইগুলোকে আর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারও করা হয়নি। আবার কিছু ক্ষেত্রে এই সুন্দর অস্ত্রগুলো এতটাই বড় আকারে বানানো হয়েছে যে ওগুলো ব্যবহার করা সম্ভবই না। তাহলে কেন এমন করত? মার্কিন দার্শনিক ডেনিস ডাটনের মতে, এই অস্ত্রগুলো শুধু অস্ত্র নয়, এগুলো কারুকার্য, মানুষের সৌন্দর্যবোধের প্রমাণ। এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এই সুষম নিপুণভাবে কাটা পাথরের অস্ত্রগুলো দেখিয়েই, এই কারিগরি ও শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েই সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা হতো। এটা শুনে একটু হাসি পেতেই পারে কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে ভাবি তাহলে দেখব এই প্রথা এখনো চলছে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্তে। প্রিয়জনকে হীরের আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার রীতি নতুন কিছু নয়, হীরাও এক প্রকার খনিজ পদার্থ যাকে নির্দিষ্ট নিয়মে নিপুণভাবে কেটে অপরপক্ষকে প্রভাবিত করা হয় আজও। হীরা বা সোনার গয়না বানিয়ে দেওয়া বা উৎসবে অনুষ্ঠানে সেগুলো পরে অন্যদের দেখানো, এ মোটেও আজকের ব্যাপার না, এর পিছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ রয়েছে তার ইতিহাস সুদীর্ঘ।
একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে, তারা সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চলের হওয়া সত্ত্বেও, একই প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে সাইটগুলোতে। সাধারণত এই মূর্তিগুলো ‘ভেনাস ফিগারিন’ নামেই পরিচিত।
যেমন, মরক্কোর টান-টান অঞ্চলের ভেনাস মূর্তি। এর সময়কাল ধরা হয় ৩ থেকে ৫ লক্ষ বছর কিন্তু এই সময়কাল নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কোনো কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। তাছাড়া, এই পাথরটি বহু গবেষকের মতে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট, এই মূর্তিকে রূপায়িত করে তুলতে মানুষের কোনো হাত নেই।
এই রকম নারীমূর্তি পৃথিবীর নানান জায়গায় পাওয়া গেছে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে সাইবেরিয়া পর্যন্ত। ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই নারীমূর্তিগুলোকে বানানো হতো তা নিয়ে নানান মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন এগুলো প্রাগৈতিহাসিক ধর্মীয় মূর্তি, বা প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক, বা গর্ভবতী মহিলাদের প্রতীক। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ভাবা হয় যে, এই মূর্তিগুলো বানিয়ে প্রণয়িনীকে প্রেম নিবেদন করা হতো। বা, মহিলা শিল্পীরাই নিজেদের দেখে এগুলো বানাতেন তাই বক্ষযুগল স্ফীত হতো, হাত ও পা প্রায় দেখাই যেত না ঠিক করে। অনেকে এটাও মনে করেন যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন খাবার খুবই সীমিত ছিল, ফলত মানুষরা স্বভাবতই শীর্ণকায় হতো তখন এইপ্রকার স্ফীত শরীরই কাঙ্ক্ষিত ছিল কারণ সন্তান ধারণের জন্য ও স্তন্যপানের জন্য স্ফীত, সুপুষ্ট দেহের দরকার ছিল। উদ্দেশ্য যেটাই হোক, এই মাতৃমূর্তি স্থান ও কালের বেড়াজাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে এই মূর্তিগুলো পাওয়া গেছে। এবং শুধু প্রাগৈতিহাসিককালেই নয়, এই মুর্তিগুলোকে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ঐতিহাসিককালেও নানান জায়গায় খনন করে পাওয়া গেছে, এমনকি আমাদের সিন্ধুসভ্যতাতেও পাওয়া গেছে।
ফেরা যাক হোলহেফেলসের ভেনাস মূর্তিকে নিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওটাই সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে পুরোনো মাতৃমূর্তি। কিন্তু এটিই সবচেয়ে পুরোনো ভাস্কর্য নয়। হোলহেফেলসের মতোই জার্মানির আরেক গুহা, হোলেনস্টেইন-স্টাডল থেকে একটি নরসিংহ মূর্তি পাওয়া গেছে। এটিও ম্যামথের দাঁতে বানানো এবং কার্বনডেটিংএ দেখা গেছে এর বয়স ৩৫ থেকে ৪১ হাজার বছর। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এই মূর্তিটির মাথা সিংহের ও শরীর মানুষের। পৌরাণিক নরসিংহের মতোই। এতে মানুষের মস্তিষ্ক কতটা বিকশিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ শুধু প্রাণী বা শুধু মানুষের মূর্তি নয়। মানুষ পশু ও মানুষকে নিজের কল্পনায় এক করতে শিখে গেছে এই সময়ে।
জানতে খুব ইচ্ছে করে কে বা কারা এই মূর্তি বানিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা কে একটি নিরেট হাতির দাঁতের স্তম্ভের মধ্যে যে একটা নরসিংহ লুকানো আছে তা ভেবে ফেলতে পেরেছিলেন। কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রহ্লাদই হবে নিশ্চয়।
যেই করে থাকুন এই কাজ, আমার বিশ্বাস তিনিও তাঁর সময়ে ‘ইল দিভিনো’-র সমতুল্য কোনো আখ্যা পেয়েছিলেন। একটি নিরেট বস্তুর মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর একটি মূর্তিকে দেখতে পাওয়া এ তো ঈশ্বরের বরপুত্রের পক্ষেই সম্ভব।
তবু “ছানাতুপার নাম ছানাতুপা কেন?” এই প্রশ্ন ওই ছোট বয়সে মাথায় আসেনি। আসলে নিশ্চইয় জিজ্ঞেস করতাম। বা করতাম না হয়তো। না জানি কোন ছানাকে পুঁতে রেখেছিল ওখানে! ভয় ভয় করত ছানাতুপার দিকে একা যেতে, কিন্তু নিজেকে আটকানোও যেত না।
ছানাতুপা একটি বিশাল জায়গা, যাকে বলে আমাদের ‘বাঞ্ছারামের বাগান’। কত বিঘা চাষের জমি ছিল সেটাও আর মনে নেই। অনেক সেগুন গাছ দিয়ে ঘেরা ছিল। ছিল সবজির জমি। আর কয়েকটা ছোটোখাটো পুকুর। আদতে এমন কিছুই না, কিন্তু বেশ একটা জমিদার জমিদার ভাব হতো ওখানে গেলে।
ছানাতুপার ওই সব ছোট পুকুরগুলোতেই আমরা যেতাম মাছ ধরতে। কিছু পুকুর ছিল শালুকভর্তি। সেগুলোতে জাল ফেলা যেত না। দাদু তখন আমায় বঁড়শি ধরিয়ে দিত। সারা দুপুর আমরা মাছ ধরে কাটাতাম।
ফেরার পথে এক জায়গায় এসে দাদু দাঁড়িয়ে যেত। বলত, “গড় কর।”
আমি হাতজোড় করে প্রণাম করতাম। একটা গাছ আর কিছু ঝোপ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ত না। তবু, প্রণাম করতাম।
দাদুর কাছে নরসিংহ আর প্রহ্লাদের গল্প শুনেছি। ভগবান যে সব কিছুতেই বিদ্যমান সেটাও বিশ্বাস করতাম। তাই প্রণাম করতাম। তবে ‘গড় করা’ যাকে বলে ঠিক ততটা ঝুঁকে না, অল্প ঝুঁকে। তাই ধরাও পড়ে যেতাম। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে অনেক প্রশ্নও থাকত যে।
দাদু আমার ইতস্তত ভাবটা ধরতে পেরে বলত, “এখানে তোর বাবা ঠাকুর পেয়েছিল। ওই গাছটার নিচে। মাটি খুঁড়ে হাতি-ঘোড়ার মূর্তি পেয়েছিল। এখন আর এখানে নেই, ঠাকুরের থানে রাখা আছে, পরে নিয়ে যাব।”
মনে হাজারটা প্রশ্নের উদয় হত। বাঁকুড়ায় বাড়ি অথচ মাটির হাতিঘোড়া দেখেনি এমন হয়তো কেউই নেই। আমিও দেখেছি। কিন্তু মাটির তলা থেকে? মাটি খুঁড়ে মাটির তলা থেকেও জিনিস পাওয়া যায়? এমন আশ্চর্যজনক কথা এর আগে শুনিনি।
মনে নেই কত পরে কিন্তু পরে সেই হাতিঘোড়ার মূর্তি দেখেছিলাম। খুব সাধারণ, মাটির তৈরি ছোট্ট ছোট্ট হাতিঘোড়ার মূর্তি। বিভিন্ন আকারের অসংখ্য হাতিঘোড়ার মাঝে ঠিক কোন দু'টো তা ঠাওর করতে না পারলেও, ছোট ছোট কোনো দু'টো হবে আন্দাজ করেছিলাম। ধর্মঠাকুরের থানে তখন পুজো চলছে। আমি সেই কোলাহল কাটিয়ে মদনডিহির দিকে হাঁটা লাগাতাম।
মদনডিহি বা মদনডি ছানাতুপার পাশেরই এক গ্রাম। সেখানেই একবার এক কুমোর বাড়িতে মাটি টিপে টিপে ওই রকম ছোট ছোট ঘোড়া বানাতে দেখেছি। বানাত ছোট ছোট মাটির পুতুলও, সবই আঙুল দিয়ে টিপে টিপে। বাড়ির বড়, বুড়ো, বাচ্চা সবাই পুতুল বানাচ্ছে। আমার মতো অচেনা কাউকে ওদের উঠানে দেখেও ওরা ইতস্তত করে না। উল্টে খড়ের দড়ির খাটিয়াতে বসতে বলে, সেখানে আরেক বাচ্চা দুলে দুলে কিশলয় পড়ছে। মনে আছে এক দাদু ছোট্ট মাটির তৈরি একটা পাখিতে ফুঁ দিয়ে পাখির আওয়াজ বের করছিল। কী মধুর সে ডাক! আমার মনটা কোথায় যেন ভেসে যেত সেই পাখির ডানায় ভর করে। আমার থেকে থেকেই খালি নিজের দাদুর কথা মনে পড়ত। আমি আবার ছানাতুপার দিকে হাঁটা লাগাতাম।
ততদিনে বেশ কিছুটা বড় হয়ে গেছি। ছানাতুপায় একা একা ঘুরে বেড়াতে ভয় করে না। এমনকি নদীর দিকেও একাই ঘুরে বেড়াই। শীতের ছুটিতে সকালের নরম রোদ গায়ে মাখতে মাখতে হেঁটে যেতাম নদীর দিকে।
নদীর ধরে এক গ্রাম। ওদিকে অনেক খেজুর গাছ। খেজুর গাছে বাঁধা হাঁড়িগুলো নামিয়ে রাখা থাকত সারি সারি। দূরে এক দাদু ওই বয়সেও জাল দিত সেই রসে। অনেক কসরতের পর তৈরি হত খেজুরের গুড়। আমায় না চিনলেও ডেকে একটু চাখতে বলত সেই গুড়। কী মিষ্টি! আর তখনও গরম। ভালোবাসার মতোই মিষ্টি আর গরম। আমার আবার দাদুর কথা মনে পড়ত।
মনে পড়ত দাদুর কাঁধে চড়ে গাজন দেখতে যাবার কথা। সাঁওতাল পরব দেখতে যাবার কথা। সেখানে কাড়া বলি হতো। আমায় দেখতে দিত না। বলির আগে আমায় নিয়ে চলে আসত। আমি প্রশ্ন করতাম, “কাড়া বলি দেয় কেন?”
“যে ঠাকুর যা চায়, তাই দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। আমাদের কেমন পাঁঠা বলি হয় কালীপূজায়।” আমার মোটেও পছন্দ ছিল না পাঁঠা বলি দেওয়া। পুজোর অনেক আগে থেকেই একটা ছাগলকে এনে রাখা হতো। তাকে রোজ খেতে দেওয়া, চরতে নিয়ে যাওয়া। অনেক সময় এই সব কাজ আমিও করতাম। আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যেত পাঁঠাটির। কালীপুজোর রাতে যখন বেচারাকে বলির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, মনটা বড্ড খারাপ হতো। ওর আর্তচিৎকার কানে আটকে থাকত। আমি ওই রাতের অন্ধকারেই নদীর দিকে হাঁটা লাগাতাম।
কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে খুব বেশি দূর যেতে পারতাম না। কালীপুজোর কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই দূর থেকে ধামসা-মাদলের আওয়াজ ভেসে আসত। অন্ধকারে অসমান মোরাম ফেলা পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে শাল-পলাশের গাছগুলোকে মনে হতো আস্ত ভূতের দল। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন তালে বিভিন্ন লয়ে বেজে চলা নানান বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে শুনতে নিজেকে বেশ ভূতেদের রাজা বলে মনে হয়। চোখ বন্ধ করে সেই জলসা উপভোগ করার চেষ্টা করতাম, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করতাম। মন ও শরীর— দুটোই খানিকটা হালকা লাগত।
তবে এই অনুভূতি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না। ঘাড়ের উপর কার যেন নিঃশ্বাস পড়ত। ঘুরে তাকাতেই এক বিকট মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতাম। দেখতাম ভূতটাও একই রকম আঁতকে উঠে ‘উঞ্চা উঞ্চা পাবত, উঞ্চা উঞ্চা পাবত’ করতে করতে ছুটছে উল্টো দিকে। ওকে ছুটতে দেখে আমি থেমে যেতাম।
উঞ্চা ক্ষ্যাপা ওই রকমই ছিল। দিন নেই, রাত নেই, মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াত। বন্ধনহীন জীবন। মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইত। কেউ ওকে বিরক্ত করত না, আর পারতপক্ষে ও-ও কাউকে বিরক্ত করত না। প্রতি গ্রামেই নাকি এই রকম একটা-আধটা পাগল থাকে। জানি না কবেকার এই নিয়ম বা জানা নেই কে বা কারা কত দিন ধরে বংশপরম্পরায় পাগল সরবরাহ করে চলেছে প্রতি গ্রামে। কেউ উত্তর দিত না এই সব প্রশ্ন করলে। একবার এক ভিনগাঁয়ের হরবোলা বলেছিল একটা পাগল থাকলে নাকি গ্রামের বাকি লোক ঠিক থাকে। পাগল না থাকলেই নাকি যত বিপদ। ওই পাগলকে দেখেই নাকি বাকিরা বুঝে চলে, যাতে পাগল না হয়ে যায় সেই আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর গাঁয়ে পাগল না থাকলে এর পর কে পাগল হতে চলছে সেই ভাবতে ভাবতে নাকি গোটা গাঁ পাগল হয়ে যায়।
“যত্তসব ভুলভাল কথা!” খুব হেসেছিলাম সেদিন।
গ্রীষ্মের অলস দুপুরে আটচালার ছায়ায় বসে হরবোলা তখন নানান পাখির ডাক ডাকতে ব্যস্ত। আমার হাতে গুলতি, পকেটে কাচের মার্বেল আর এক ঠোঙা সবুজ মটর। ওর শ্রোতা বলতে তখন আমিই, কারণ আর যে দুয়েকজন আটচালায় ছিল তারা মাদুর পেতে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। আমাকে ঠোঙা থেকে সবুজ মটর খেতে দেখে সে-ও হাত বাড়াল। প্রিয় জিনিস, দিতে মন চায় না তবু গুনে গুনে কয়েকটা দিয়েই আমি ঠোঙাটা পকেটে পুরলাম। পকেটের ভিতরের মার্বেলগুলো নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে টরটর টরটর আওয়াজ করে উঠল।
“যত্তসব ভুলভাল কথা!” খুব হেসেছিলাম সেদিন।
গ্রীষ্মের অলস দুপুরে আটচালার ছায়ায় বসে হরবোলা তখন নানান পাখির ডাক ডাকতে ব্যস্ত। আমার হাতে গুলতি, পকেটে কাচের মার্বেল আর এক ঠোঙা সবুজ মটর। ওর শ্রোতা বলতে তখন আমিই, কারণ আর যে দুয়েকজন আটচালায় ছিল তারা মাদুর পেতে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। আমাকে ঠোঙা থেকে সবুজ মটর খেতে দেখে সে-ও হাত বাড়াল। প্রিয় জিনিস, দিতে মন চায় না তবু গুনে গুনে কয়েকটা দিয়েই আমি ঠোঙাটা পকেটে পুরলাম। পকেটের ভিতরের মার্বেলগুলো নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে টরটর টরটর আওয়াজ করে উঠল।
“কই দেখাও দেখি একটা?”
আমি একটা মার্বেল বের করে দেখালাম। লোকটা হেসে বলল, “নাম মার্বেল, এদিকে জিনিসটা কাচের। কেমন লোকঠকানো ব্যাপার বলো দেখি!”
আমার ওসবে মন নেই। আমি বললাম, “কই, পাশের গাঁয়ে তো কোনো পাগল দেখিনি।”
“আছে আছে। শুধু জানতে পারো না। পাগল ছাড়া কি পৃথিবী চলে? ঠি-ই-ক আছে। খুঁজে দেখো।”
নাহ, পাগলের খোঁজে ঘুরে বেড়াবার মতো বিলাসিতা হয়নি ওই বয়সে। আর পরবর্তীকালে বনফুলের ‘জাগ্রত দেবতা’ পড়ার পর তো আরোই ওইদিকে পা বাড়াইনি।
এরপর যতবারই গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গেছি, ঘুঘুডাকা নিঃঝুম দুপুরে আটচালায় বসে ঝাল-ঝাল সবুজ মটর খেয়েছি, মনে মনে আশা করেছি সেই হরবোলার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কিন্তু হয়নি। আফসোস হয়েছে আরও কয়েকটা মটর দিইনি বলে। অনেক অপেক্ষার পরেও যখন আসেনি, তখন মনে সন্দেহ হয়েছে যে ওই হরবোলাই ছিল পাগলধরাচক্রের পাণ্ডা। আর যতদিন উঞ্চা ক্ষ্যাপা আমাদের গ্রামে আছে ও আর আসবে না।
রোদ একটু পড়ে এলেই হরবোলাকে ছেড়ে উঞ্চার খোঁজে বেরিয়ে পড়তাম। ওর আস্তানাগুলো এতদিনে আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। নতুন পাগল খুঁজতে না বেরোলেও পুরোনো পাগলের হালহকিকত আমার জানা ছিল। উঞ্চাকে সবসময়ই খুব ব্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যেত কাঁসাই নদীর অপর পারে।
“আছে আছে। শুধু জানতে পারো না। পাগল ছাড়া কি পৃথিবী চলে? ঠি-ই-ক আছে। খুঁজে দেখো।”
নাহ, পাগলের খোঁজে ঘুরে বেড়াবার মতো বিলাসিতা হয়নি ওই বয়সে। আর পরবর্তীকালে বনফুলের ‘জাগ্রত দেবতা’ পড়ার পর তো আরোই ওইদিকে পা বাড়াইনি।
এরপর যতবারই গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গেছি, ঘুঘুডাকা নিঃঝুম দুপুরে আটচালায় বসে ঝাল-ঝাল সবুজ মটর খেয়েছি, মনে মনে আশা করেছি সেই হরবোলার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কিন্তু হয়নি। আফসোস হয়েছে আরও কয়েকটা মটর দিইনি বলে। অনেক অপেক্ষার পরেও যখন আসেনি, তখন মনে সন্দেহ হয়েছে যে ওই হরবোলাই ছিল পাগলধরাচক্রের পাণ্ডা। আর যতদিন উঞ্চা ক্ষ্যাপা আমাদের গ্রামে আছে ও আর আসবে না।
রোদ একটু পড়ে এলেই হরবোলাকে ছেড়ে উঞ্চার খোঁজে বেরিয়ে পড়তাম। ওর আস্তানাগুলো এতদিনে আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। নতুন পাগল খুঁজতে না বেরোলেও পুরোনো পাগলের হালহকিকত আমার জানা ছিল। উঞ্চাকে সবসময়ই খুব ব্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যেত কাঁসাই নদীর অপর পারে।
গ্রীষ্মে গোড়ালিজলও থাকত না কাঁসাইয়ে। অজস্র সুন্দর গোল গোল চিকন নুড়িপাথরের আহ্বান এড়াতে না পেরে দুয়েকটাকে পকেটে পুরতে পুরতে, জলের উপর ছপাৎ ছপাৎ করতে করতে পৌঁছে যেতাম অন্য প্রান্তে, এক শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের পাদদেশে। সেই মন্দিরের অবশ্য কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধুই ভিতটুকু রয়ে গেছে। তবু ক্ষ্যাপা খুঁজে চলে।
উঞ্চা কী খোঁজে একদম ঠিক করে না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমিও খুঁজতে আসতাম। খুব শখ ছিল বাবার মতো আমিও কোনো ঠাকুর খুঁজে পাব। মাটি খুঁড়ে না হোক, নদী খুঁড়ে।
শুনতে পাগলের পাগলামি মনে হলেও ব্যাপারটা তা নয়। সত্যিই কাঁসাই থেকে অনেক প্রাচীন মূর্তি অনেকে খুঁজে পেয়েছে। কালো পাথরের মূর্তি। জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। নদীর ওই পাশেই পরকুল মেলার শিবমন্দিরেও ছিল এক মূর্তি। পরে মনে হয় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে এসে নিয়ে যায় সেই মূর্তি। আমাদের গ্রামের একজনের বাড়িতেও এক মূর্তি ছিল যার সন্ধান আমরাই জানতাম খালি। সেই মূর্তিতে ফুল, বেলপাতা চাপিয়ে হিন্দু মতেই পূজা হতো। তাতে মূর্তির স্মিতহাসি ম্লান হয়ে যেতে দেখিনি কোনোদিন। সব ঠাকুরই হয়তো ভক্তি দেখে খুশি থাকেন, আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না।
উঞ্চা কী খোঁজে একদম ঠিক করে না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমিও খুঁজতে আসতাম। খুব শখ ছিল বাবার মতো আমিও কোনো ঠাকুর খুঁজে পাব। মাটি খুঁড়ে না হোক, নদী খুঁড়ে।
শুনতে পাগলের পাগলামি মনে হলেও ব্যাপারটা তা নয়। সত্যিই কাঁসাই থেকে অনেক প্রাচীন মূর্তি অনেকে খুঁজে পেয়েছে। কালো পাথরের মূর্তি। জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। নদীর ওই পাশেই পরকুল মেলার শিবমন্দিরেও ছিল এক মূর্তি। পরে মনে হয় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে এসে নিয়ে যায় সেই মূর্তি। আমাদের গ্রামের একজনের বাড়িতেও এক মূর্তি ছিল যার সন্ধান আমরাই জানতাম খালি। সেই মূর্তিতে ফুল, বেলপাতা চাপিয়ে হিন্দু মতেই পূজা হতো। তাতে মূর্তির স্মিতহাসি ম্লান হয়ে যেতে দেখিনি কোনোদিন। সব ঠাকুরই হয়তো ভক্তি দেখে খুশি থাকেন, আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না।
প্রতিবেশীর সেই অসামান্য সংগ্রহ দেখে আমারও খুব শখ হয়েছিল মূর্তি খোঁজার। কিন্তু পাইনি। অনেক খুঁজেও পাইনি। উঞ্চাও পায়নি। দুই হতভাগ্য প্রস্পেক্টর রাঢ়বঙ্গের ধূলিধূসরিত নদীতটে বিকেলটা কাটিয়ে দিত টলটলে স্বচ্ছ জলে গোড়ালি ভিজিয়ে। ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি সব কিছু শুষে নিয়ে কাঁসাই বয়ে যেত নিজের পথে। সেই সব সোনালি বিকেলগুলোতে উঞ্চাকে বড্ড নিজের লোক মনে হতো।
আজও সেই সব দিনের কথা যখন ভাবি উঞ্চার কথা খুব মনে পড়ে। ওকে দেখতেও যেন ওই মূর্তিগুলোর মতোই ছিল। যেন একই রকম কালো পাথরে বানানো। চোখের কোণে একই রকম প্রশান্তি চিকচিক করত ওর। সামনের কিছু দাঁত ভাঙা ছিল ঠিকই তবু ঠোঁটে লেগে থাকত একই রকমের স্মিতহাসি।
আজ ভাবতে বসলে প্রশ্ন জাগে মনে, সত্যিই কি সেদিন ভগবানকে খুঁজে পাইনি? না কি পেয়েছি? প্রহ্লাদের মতো পাথরের থামের মধ্যে নয়, বা মাটির হাতিঘোড়ার মধ্যে নয়, কালো মূর্তির মধ্যে নয়, কিন্তু এক পাগলের বেশে?
নাহ, পৃথিবীতে সত্যিই পাগলের দরকার! আজ হয়তো উঞ্চা আর নেই। সেই হরবোলা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে গেছে আমাদের গ্রামে। বা সে হয়তো বসে আছে আজও। ঝাল-ঝাল সবুজ মটর আর এক পাগলের ফেরার অপেক্ষায়।
নাহ, পৃথিবীতে সত্যিই পাগলের দরকার! আজ হয়তো উঞ্চা আর নেই। সেই হরবোলা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে গেছে আমাদের গ্রামে। বা সে হয়তো বসে আছে আজও। ঝাল-ঝাল সবুজ মটর আর এক পাগলের ফেরার অপেক্ষায়।
আজ লিখতে বসেছিলাম ভাস্কর্য নিয়ে, কিন্তু জানি না কোন অজ্ঞাত কারণবশত নিজের ছোটবেলার কথাগুলো লিখে ফেললাম। হয়তো এই জন্যই যে আমরা মানুষরা সততই উৎসসন্ধানী। পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী নেই যে নিজের উৎস নিয়ে আবেগপ্রবণ। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করে চলেছে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমরা কোথা থেকে এলাম বা কীভাবে এলাম।
ঠিক এই কারণেই আজকাল জিনিওলজিস্টদের এত চাহিদা। সবাই জানতে চায় তাদের পরিবারের উৎস কোথায়। অবশ্য জিনিওলজিস্টদের ওই একটাই আজ তা নয়। আর জিন থেকে শুধুই একজনের পরিবার নিয়ে জানা যায় তা-ও নয়, বরং জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গোটা মানবজাতির ইতিহাস। বর্তমানে জেনেটিক্স এতটাই উন্নত হয়েছে যে, মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কীভাবে কোন পথ ধরে পৃথিবীর নানান স্থানে যাত্রা করেছে তারও আন্দাজ পাওয়া যায়। মানবজাতির সূচনাস্থল হিসাবে আফ্রিকাকেও চিহ্নিত করা গেছে। মানবজাতি বলতে আমরা যদি আপাতত শুধু হোমো সেপিয়েন্সকে ধরে নিই, তাহলে অন্যান্য বিলুপ্ত মানবপ্ৰজাতিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন ছিল সেই বিষয়েও আমরা জানতে পারি ওই জিনের মাধ্যমে।
আমাদের নিজেদের পরিবারের উৎস সন্ধান বা সামগ্রিক মানবজাতির উৎস সন্ধানের পাশাপাশি আমরা মানুষরা আরও একটি জিনিস খোঁজার চেষ্টা করে চলি অনবরত— আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার উৎস কোথায়। আমরা কেন এই রকম হলাম বা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দগুলো কীভাবে জন্মাল, আমাদের কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মাল কীভাবে, এগুলোও আমাদের অনেককে ভাবিয়ে তোলে।
লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম আমরা সবাই শুনেছি। আমরা সবাই তাঁর আঁকা ছবি দেখেছি, অনেকেই তাঁর নোটবইয়ের ছবি দেখেছি। তাঁর নানান গবেষণার কথাও শুনেছি। অসম্ভব প্রতিভাধর এই মানুষটি জীবনের একটা বড় সময় কাটিয়েছেন মানুষ কী করলে আকাশে উড়তে পারবে সেই নিয়ে গবেষণা করে। সেই সঙ্গে বানানোর চেষ্টা করেছেন প্যারাস্যুটও। কিন্তু এই উড্ডয়ন বিষয়ক গবেষণাগুলো নিজের নোটবইয়ে লিখে রাখার সময় তিনিও ভাবতে বসেছেন কেন তিনি উড্ডয়ন পদ্ধতি নিয়ে এত আসক্ত হয়ে পড়েছেন।
একটি চিল কীভাবে ওড়ে এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন – চিলকে নিয়ে আমার লিখতে বসাটা মনে হয় আমার ভবিতব্য। কারণ আমার একদম ছোটবেলার প্রথম স্মৃতিটাই হলো আমি আমার কাঠের দোলনায় শুয়ে আছি আর কোত্থেকে একটা চিল উড়ে আসে আর তারপরে ওর লেজ দিয়ে আমার মুখে বারংবার টোকা দিতে থাকে।
লিওনার্দোকে নিয়ে দীর্ঘকাল পড়াশুনা করার সুবাদে জানি, ওঁর এই স্মৃতিচারণা কতটা বিরল। লিওনার্দো পাতার পর পাতা নিজের হাজারো গবেষণার কথা লিখে গেছেন। বর্তমানে এপিঠ-ওপিঠ মিলিয়ে প্রায় তেরো হাজার পাতার সন্ধান আমরা পেয়েছি যা কিনা সমগ্র নোটবইয়ের মাত্র এক চতুর্থাংশ। অথচ এত এত লেখার মাঝে তাঁর নিজেকে নিয়ে, নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা প্রায় নেই-ই বললে চলে। সেই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ওঁর ছোটবেলার কথা লিখতে বসার একটাই অর্থ হতে পারে, উনি নিজেকে আটকাতে পারেননি। খুব সহজাত ভাবেই লিখে ফেলেছিলেন ছোট্ট ঘটনাটা।
ঠিক যে রকম আমিও নিজেকে আটকাতে পারিনি – কে কীভাবে লিখিয়ে নিল জানি না কিন্তু খুব সহজাতভাবেই লিখে ফেলেছি ছোটবেলার কথাগুলো।
হয়তো ভাস্কর্য নিয়ে আমার এই ভালোবাসার সূত্র লুকিয়ে আছে আমার ছোটবেলার ঘটনাগুলোতেই। কারণ ছোটবেলায় আঁকা শিখলেও, ভাস্কর্য নিয়ে আমি কিছুই শিখিনি। আটা দিয়ে সাপ, টিকটিকি বানানো ছাড়া আর কিছুই বানাইনি। পুলিপিঠে বা মোমো বানানোকেও হয়তো ভাস্কর্যের মধ্যে ধরা হবে না। জীবনে সামান্য কিছু মাটির প্রদীপ ছাড়া আর কিছু বানিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তবু ছোটবেলা থেকেই ভাস্কর্যের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসা আমি সর্বদাই অনুভব করেছি। এর একটা কারণ হতে পারে— এক, শিল্পমাধ্যম হিসাবে ভাস্কর্য এমনিই প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ও সুন্দর। আর সুন্দর, সুষম যেকোনো কিছুর প্রতি টান আমাদের মজ্জাগত। এক সহজাত সৌন্দর্যবোধ নিয়েই আমরা মানুষরা জন্মেছি। দুই, কোনো না কোনোভাবে অবচেতনে রয়ে গিয়েছিল ছোটবেলার ঘটনাগুলো। এখন যদি সত্যিই ভাবতে বসি তাহলে অবাক লাগে এটা ভেবে যে, ‘প্রত্নতত্ত্ব’-এর মতো ভারিক্কি একটা শব্দ না জেনেও, মাটি খুঁড়ে যে অতীত উদ্ধার করা যায় তার পাঠ পেয়েছিলাম কোন ছোটবেলায়। আর অতীত জানার এই নেশা পেয়ে বসলে স্কুলজীবনে ইতিহাস হয়ে ওঠে অন্যতম প্রিয় বিষয়।
মনে পড়ে, মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচিতে সিন্ধুসভ্যতার ইতিহাস ছিল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে যেটুকু তথ্য ছিল তা যথেষ্ট না হওয়ায় উচ্চমাধ্যমিকের, এমনকি অনার্সের বইও পড়া শুরু করি। একমাত্র ইতিহাসের শিক্ষকমহাশয় প্রবালবাবু ছাড়া আর কেউই বিশেষ উৎসাহ যোগাননি।
ওইসব ভারী ভারী ইতিহাসের বই পড়তে পড়তেই একদিন আবিষ্কার করি আমার ছোটবেলার, আমাদের বাঁকুড়ার টেপা পুতুলকে। পথ ভুলে সিন্ধুসভ্যতার ভাস্কর্যের মধ্যে দিব্যি ঢুকে পড়েছে তারা। সেই সময় মাধ্যমিকের পড়ার চাপে খুব বেশি এগোনো যায়নি এই নিয়ে। কিন্তু ভুলিনি। পরে পড়াশুনা করে জেনেছি বাংলার টেপা পুতুলদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কথা। বাংলার এক হতদরিদ্র অবহেলিত ভাস্কর্যশিল্পেরও যে এত প্রাচীন এক সংযোগ থাকতে পারে তা হয়তো আমাদের বেশিরভাগেরই অজানা রয়ে গেছে।
খোঁজ পেয়েছিলাম মার্বেলেরও। সিন্ধুসভ্যতার বাচ্চারাও আমাদের মতো মার্বেল নিয়ে খেলত। মহেঞ্জোদারোয় পাওয়া গিয়েছিল পাথরের ছোট ছোট মার্বেল। সেই হরবোলাকে আর বলা হয়নি, কিন্তু মার্বেলের নাম মার্বেল কারণ একসময় এগুলো কাঁচের না হয়ে মার্বেল পাথরেরই হতো।
এই রকম ছোট ছোট পাথরের গোলক মিশরেও পাওয়া গিয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতি গোলকগুলোকে গোলক বানানো হয়েছিল ঘষে ঘষে। নিজের থেকেই পাথরগুলো গোল ছিল না। এর চেয়ে খানিকটা বড় আকারের, প্রায় ক্রিকেট বলের আকারের চুনাপাথরের গোলক পাওয়া গেছে ইজরায়েলের উবেইদিয়া অঞ্চলে। সেগুলোর বয়স শুনলে হতবাক হতে হয়। প্রায় ১৪ লক্ষ বছর আগেকার। এবং সেগুলোকেও কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে ধীরে গোলোকে পরিণত করেছে।
এই গোলকগুলোর ব্যবহার কী ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু চুনাপাথর নয়, চকমকি পাথর ও ব্যাসাল্টেরও গোলক পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে অসংখ্য হ্যান্ডঅ্যাক্স-এর সঙ্গে। হ্যান্ডঅ্যাক্স বলতে পাথরের তৈরি হাতলবিহীন কুঠার, দেখতে গাছের পাতা বা অশ্রুবিন্দুর মতো। এর দুই ধার সাধারণ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। এগুলো প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত হাতের মুঠোয় ধরে তাই নাম হ্যান্ডঅ্যাক্স।
হ্যান্ডঅ্যাক্স নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে ফেরা যাক রহস্যময় গোলকগুলো নিয়ে। অনেকের ধারণা এগুলোকে গোলার মতো ব্যবহার করা হতো, শিকারের সময় দূর থেকে ছুঁড়ে মারার জন্য। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একদম নিটোলভাবে গোল করার দরকার হয়তো ছিল না। কিন্তু সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকতা হয়তো মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই ছিল। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে মানুষ বলতে শুধু হোমো সেপিয়েন্সদের কথা ভাবলে চলবে না। কারণ যে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলের কথা হচ্ছে সেটি প্রায় ১৪ লক্ষ বছর আগের আর হোমো সেপিয়েন্সের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ বছর আগে। অবশ্য সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা বলছে এই সময়কাল পিছিয়ে প্রায় ৪ লক্ষ বছর হতে পারে। তাই ১৪ লক্ষ বছর আগে হোমো সেপিয়েন্সদের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেক্টাসরা ওই গোলকগুলো বানিয়েছিল।
উদাহরণস্বরূপ মাকাপান উপত্যকার একটি বিশেষ নুড়িপাথর। এটি একটি ছোট লাল রঙের পাথর। এটি যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেই প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের মধ্যে লাল রঙের এই পাথরটিকে পাওয়া এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার কারণ ওই জায়গায় আর কোনো লাল জেসপারাইট পাথর নেই। সবচেয়ে কাছে যেটা আছে সেটাও ৩ মাইল দূরে। অর্থাৎ কেউ একজন এই বিশেষ পাথরটিকে বয়ে নিয়ে এসেছিল সযত্নে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই পাথরটি শুধু লালই নয়, সঙ্গে ভালো করে লক্ষ করলে চোখ-মুখও দেখা যায়। কিন্তু এর কোনোটাই জোর করে বানানো নয়, প্রাকৃতিকভাবেই তৈরী হওয়া। অর্থাৎ আমাদের মতোই, আমাদের পূর্বপুরুষ কেউ একজন সুন্দর একটি নুড়িপাথর দেখে টুক করে তুলে নিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাসায়, সযত্নে রেখেছিল তাকে।
এই নান্দনিক বোধের প্রসঙ্গে আরেকটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিই। একটু আগেই আমরা হ্যান্ডঅ্যাক্সের কথা বলছিলাম। এই প্রকার অস্ত্র মনুষ্যপ্রজাতি প্রায় ১৬ লক্ষ বছর আগে থেকে ব্যবহার করছে। ১৪ লক্ষ বছর আগে এই অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মূলত হোমো ইরেক্টাসরাই এই অস্ত্র ব্যবহার করত, হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যে এর ব্যবহার কমই দেখা যায়। নানান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এই পাথরের অস্ত্রগুলো খুব নিখুঁত করে বানানো হয়েছে। যদি এই অস্ত্রগুলোকে বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য শিকার করাই হয় তাহলে অতটা নিখুঁত সুষম করে বানানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু মানুষ সেটাই করত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানান হ্যান্ডঅ্যাক্সের মধ্যে এমনও মিল দেখা গেছে যে সন্দেহ হয় সেগুলো একজন শিল্পীরই বানানো কিনা। এখানে খুব সচেতনভাবেই কারিগরের জায়গায় শিল্পী বললাম, কারণ সেই হ্যান্ডঅ্যাক্সগুলো এতটাই সুন্দর যে কোনো শৈল্পিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এগুলো বানানো সম্ভব।
শুধু এই অস্ত্রটি একটামাত্র উদাহরণ হলে হয়তো একে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নেওয়াই যেত। কিন্তু শুধু এটি নয়, আরও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অস্ত্রগুলো এতটাই যত্ন নিয়ে বানানো যে সেইগুলোকে আর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারও করা হয়নি। আবার কিছু ক্ষেত্রে এই সুন্দর অস্ত্রগুলো এতটাই বড় আকারে বানানো হয়েছে যে ওগুলো ব্যবহার করা সম্ভবই না। তাহলে কেন এমন করত? মার্কিন দার্শনিক ডেনিস ডাটনের মতে, এই অস্ত্রগুলো শুধু অস্ত্র নয়, এগুলো কারুকার্য, মানুষের সৌন্দর্যবোধের প্রমাণ। এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এই সুষম নিপুণভাবে কাটা পাথরের অস্ত্রগুলো দেখিয়েই, এই কারিগরি ও শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েই সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা হতো। এটা শুনে একটু হাসি পেতেই পারে কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে ভাবি তাহলে দেখব এই প্রথা এখনো চলছে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্তে। প্রিয়জনকে হীরের আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার রীতি নতুন কিছু নয়, হীরাও এক প্রকার খনিজ পদার্থ যাকে নির্দিষ্ট নিয়মে নিপুণভাবে কেটে অপরপক্ষকে প্রভাবিত করা হয় আজও। হীরা বা সোনার গয়না বানিয়ে দেওয়া বা উৎসবে অনুষ্ঠানে সেগুলো পরে অন্যদের দেখানো, এ মোটেও আজকের ব্যাপার না, এর পিছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ রয়েছে তার ইতিহাস সুদীর্ঘ।
বিখ্যাত ভাস্কর মিকেলাঞ্জেলো তাঁর অসামান্য দক্ষতার জন্য জীবদ্দশাতেই ‘ইল দিভিনো’ অর্থাৎ ‘ঐশ্বরিক’ বা ‘ঈশ্বরের স্নেহধন্য’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর এক কবিতায় লিখেছিলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পীও এমন কিছু কল্পনা করতে পারবে না যা একটি মার্বেলের ব্লকের মধ্যে লুকানো নেই। অর্থাৎ দক্ষতা থাকলে যেকোনো কিছুই বানানো সম্ভব একটি পাথরের টুকরো থেকে এবং এই দক্ষতা ১৪ লক্ষ বছর আগেও মানবজাতির মধ্যে ছিল এ এক অভাবনীয় ব্যাপার।
হ্যান্ডঅ্যাক্সের স্বপক্ষে নানান যুক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হ্যান্ডঅ্যাক্সকে প্রথম ভাস্কর্য রূপে ধরা হয় না। তার বদলে বেশ কিছু প্রাগৈতিহাসিক মাতৃমূর্তিকে প্রথম ভাস্কর্য হিসেবে ধরা হয়, যদিও সেগুলোর ক্ষেত্রেও নানান মতবিরোধ আছে।
হ্যান্ডঅ্যাক্সের স্বপক্ষে নানান যুক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হ্যান্ডঅ্যাক্সকে প্রথম ভাস্কর্য রূপে ধরা হয় না। তার বদলে বেশ কিছু প্রাগৈতিহাসিক মাতৃমূর্তিকে প্রথম ভাস্কর্য হিসেবে ধরা হয়, যদিও সেগুলোর ক্ষেত্রেও নানান মতবিরোধ আছে।
একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে, তারা সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চলের হওয়া সত্ত্বেও, একই প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে সাইটগুলোতে। সাধারণত এই মূর্তিগুলো ‘ভেনাস ফিগারিন’ নামেই পরিচিত।
যেমন, মরক্কোর টান-টান অঞ্চলের ভেনাস মূর্তি। এর সময়কাল ধরা হয় ৩ থেকে ৫ লক্ষ বছর কিন্তু এই সময়কাল নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কোনো কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। তাছাড়া, এই পাথরটি বহু গবেষকের মতে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট, এই মূর্তিকে রূপায়িত করে তুলতে মানুষের কোনো হাত নেই।
এই রকম নারীমূর্তি পৃথিবীর নানান জায়গায় পাওয়া গেছে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে সাইবেরিয়া পর্যন্ত। ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই নারীমূর্তিগুলোকে বানানো হতো তা নিয়ে নানান মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন এগুলো প্রাগৈতিহাসিক ধর্মীয় মূর্তি, বা প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক, বা গর্ভবতী মহিলাদের প্রতীক। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ভাবা হয় যে, এই মূর্তিগুলো বানিয়ে প্রণয়িনীকে প্রেম নিবেদন করা হতো। বা, মহিলা শিল্পীরাই নিজেদের দেখে এগুলো বানাতেন তাই বক্ষযুগল স্ফীত হতো, হাত ও পা প্রায় দেখাই যেত না ঠিক করে। অনেকে এটাও মনে করেন যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন খাবার খুবই সীমিত ছিল, ফলত মানুষরা স্বভাবতই শীর্ণকায় হতো তখন এইপ্রকার স্ফীত শরীরই কাঙ্ক্ষিত ছিল কারণ সন্তান ধারণের জন্য ও স্তন্যপানের জন্য স্ফীত, সুপুষ্ট দেহের দরকার ছিল। উদ্দেশ্য যেটাই হোক, এই মাতৃমূর্তি স্থান ও কালের বেড়াজাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে এই মূর্তিগুলো পাওয়া গেছে। এবং শুধু প্রাগৈতিহাসিককালেই নয়, এই মুর্তিগুলোকে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ঐতিহাসিককালেও নানান জায়গায় খনন করে পাওয়া গেছে, এমনকি আমাদের সিন্ধুসভ্যতাতেও পাওয়া গেছে।
ফেরা যাক হোলহেফেলসের ভেনাস মূর্তিকে নিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওটাই সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে পুরোনো মাতৃমূর্তি। কিন্তু এটিই সবচেয়ে পুরোনো ভাস্কর্য নয়। হোলহেফেলসের মতোই জার্মানির আরেক গুহা, হোলেনস্টেইন-স্টাডল থেকে একটি নরসিংহ মূর্তি পাওয়া গেছে। এটিও ম্যামথের দাঁতে বানানো এবং কার্বনডেটিংএ দেখা গেছে এর বয়স ৩৫ থেকে ৪১ হাজার বছর। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এই মূর্তিটির মাথা সিংহের ও শরীর মানুষের। পৌরাণিক নরসিংহের মতোই। এতে মানুষের মস্তিষ্ক কতটা বিকশিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ শুধু প্রাণী বা শুধু মানুষের মূর্তি নয়। মানুষ পশু ও মানুষকে নিজের কল্পনায় এক করতে শিখে গেছে এই সময়ে।
জানতে খুব ইচ্ছে করে কে বা কারা এই মূর্তি বানিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা কে একটি নিরেট হাতির দাঁতের স্তম্ভের মধ্যে যে একটা নরসিংহ লুকানো আছে তা ভেবে ফেলতে পেরেছিলেন। কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রহ্লাদই হবে নিশ্চয়।
যেই করে থাকুন এই কাজ, আমার বিশ্বাস তিনিও তাঁর সময়ে ‘ইল দিভিনো’-র সমতুল্য কোনো আখ্যা পেয়েছিলেন। একটি নিরেট বস্তুর মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর একটি মূর্তিকে দেখতে পাওয়া এ তো ঈশ্বরের বরপুত্রের পক্ষেই সম্ভব।
























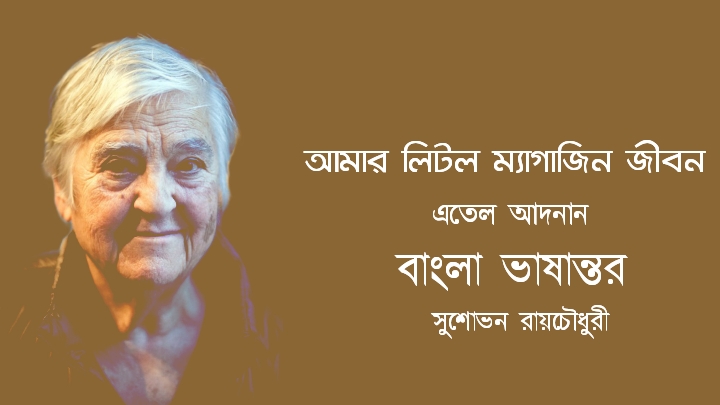
Comments
---
Salil Hore