লিটল ম্যাগাজিন ও ফিনিক্স মিথ
সাম্প্রতিক সময়কে যাঁরা পড়ছেন, লিখছেন, লেখা প্রকাশ করতে চাইছেন এবং লিটল ম্যাগাজিনের জগতে পা রেখেছেন তাঁদের অনেকেরই মনে হচ্ছে 'লিটল-এর ধারণ ধরনের বদল ঘটেছে'। অত্যন্ত সংগত এই মনে হওয়া। এবং অভিনন্দনযোগ্য।
সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বদল স্বাভাবিক। জীবন ও বস্তুর চলমানতার যে ধর্ম তা-ই আমাদের এই নির্বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু যে নিয়মে চলমানতা বজায় থাকে, এক কথায় যাকে আমরা শক্তি বলি, সেই শক্তির নিরিখে সাধারণের মধ্যেও 'বিশেষ' থাকে যা বস্তু বা জীবনকে ভিন্ন- ভিন্নভাবে 'বিশিষ্ট' করে। বস্তু বা জীবনের উন্মেষলগ্নেই এই 'বিশেষ'-এর আবির্ভাব বা বলা যেতে পারে 'বিশেষ'সহ সাধারণে জন্ম। তাই বদল বুঝতে হলে, 'শক্তি'কে মনে রাখতে হবে। বদল মানে রূপান্তর। রূপান্তর মানেই শক্তির রূপান্তর।
তা হলে লিটল ম্যাগাজিনের বদল মানে তার শক্তির রূপান্তর-- একে শক্তির নিত্যতাসূত্র অনুসারেও ভাবা যেতে পারে।
আবিশ্ব আধুনিক কবিতা ও ছোটগল্পের জন্ম আর লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম প্রায় সমসাময়িক, একজন ছোটগল্পকার হিসাবে ভাবতে ভালো লাগে যে, ছোটগল্প ধারণের তাগিদেই লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়েছিল-- এই ভাবনার মধ্যে আবেগ বেশি, যুক্তি কম মনে হতে পারে, তবে এটি আমার একান্ত বিশ্বাস-- কাঁচা যুক্তিতে একে সত্য মনে হতে পারে-- নতুন কবি বা গল্পকার তাঁর লেখাটি কোথায় প্রকাশ করবেন, ছোটকাগজ ছাড়া !
আমাদের দেশে, ছোট করে বললে বাংলা ভাষায় প্রথম যে ছোট কাগজ প্রকাশ করা হয়, প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র, বুদ্ধদেব বসু তাকে 'লিটল ম্যাগাজিন' আখ্যা দিয়েছিলেন-- এই আখ্যাটি অবশ্যই তৎকালীন শাসকের ভাষা-সাহিত্য থেকে বুদ্ধদেব বসু চয়ন করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লেখক-কবির পক্ষে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 'শিল্প-আন্দোলন'-এর খবর তাঁদের কাছে এসে পৌঁছাত।
লিটল ম্যাগাজিন এই আন্দোলনের ফসল। এই আন্দোলনের স্বরূপ কী ? নতুন কোনও বয়ান তৈরি না করে, বরং সবুজ পত্রের আবির্ভাব সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :
এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়োই কঠিন বিশেষত, এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন করে তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দু-দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নয়ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলে।
সবুজ পত্রের প্রকাশ ১৯১৪-- পরাধীন দেশের জলবায়ু ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায়, সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে, উদ্ধৃতির মধ্যেই ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে : পুরনো পৃথিবীর বিরুদ্ধে জেহাদ, নতুনকে আবাহন।
কোনও আলোচনা না রেখে, কেবল প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ মনে রেখে এ কথা বলা যায় যে, স্বজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর 'লিটল ম্যগাজিন' প্রকাশ করার অন্যতম কারণ ছিল। এর তাৎপর্য হল স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল বলে, আন্দোলনের পক্ষে নতুন চিন্তা ধারণ করতে চেয়েছিল সবুজ পত্র।...
১৯৩৫শে দেখা দিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার ভিন্ন ভিন্ন দল। দলবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছে নানা সাহিত্য সম্মিলন কিন্তু সবুজপত্রের 'স্পিরিট'টি তখনও থেকে গেছে 'লিটল ম্যাগাজিন' হিসাবে, সম্ভবত তখনও দলগুলির মধ্যে 'স্বাধীনতা' রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ছিল-- স্বাধীনতার মানে তখন ব্রিটিশ হটানো, ব্রিটিশমুক্ত স্বদেশ।
স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার স্বাদ না পাওয়া 'পিপল অফ ইন্ডিয়া' নানা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক 'স্বাধীনতা' পাওয়ার মতো কোনও আন্দোলন গড়ে না উঠলেও, শ্রমিক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের অভিঘাতে রুশবিপ্লবের পথে মুক্তির স্বপ্ন নতুন করে জেগেছে...
১৯৪৭-এর পর 'স্বাধীনতা'-আর সমাজের সার্বিক রাজনৈতিক আদর্শ থাকেনি। তখন 'সাহিত্য' খুব দ্রুত 'বিনোদন পণ্য' হয়ে উঠছে। মোটা দাগে রাজনীতি দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ধনতান্ত্রিক রাজনীতি ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি অর্থাৎ 'পলিটিকাল এনিমাল' মানুষও একই পরিবারে 'কংগ্রেস-কমিউনিস্ট' হয়েছে-- লিটল ম্যাগাজিনও 'আন্দোলন' হয়ে থেকেছে বটে, ভাগ হয়েছে...
ষাট সত্তর দশক পর্যন্ত লিটল ম্যাগাজিন মূলত বামপন্থী আদর্শের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করেছে-- চীন বিপ্লবের পথে 'সাতের দশক মুক্তির দশক' হয়নি-- এই সত্যের পাশাপাশি ১৯৭৭ সালে সংসদীয় বামপন্থার জয়জয়াকার, সংসদীয় পথে বুঝি 'স্বাধীনতা'র স্বপ্ন জাগল কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের কবি লেখক সম্পাদক-- সকলেই সমস্যায় পড়লেন, সমস্যাটা কেবল আদর্শগত নয়, সমস্যাটা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা-- এক কথায় 'অভাব'-- এই অভাব ব্রিটিশ-ভারতে ছিল ও অভাব-মুক্তির আন্দোলনে লিটলম্যাগ-সাহিত্যের ঘোষিত একটা ভূমিকা প্রমথ চৌধুরীর উক্ত সম্পাদকীয়ের মধ্যে বিবৃত হয়েছিল বলে মনে হয় কিন্তু সবুজ পত্রের স্থায়িত্ব কাল গড়ে সাড়ে ছয় বছর (প্রায়), ১৯২৭শে বন্ধ হয়ে যায়-- এই অভাবের বিরুদ্ধে আটের দশক থেকে 'লিটল ম্যাগাজিন' কোনও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না-- স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্রের যে স্বপ্ন ইতিহাস দেখেছিল, সাময়িক পত্রে ঘোষিত হল 'ইতিহাসের স্বপ্ন ভঙ্গ'র কথা...
কিন্তু এই প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক সাময়িক পত্রগুলির কাছে লিটল ম্যাগাজিন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্য দিকে তাদের লেখক-কবি জোগান দেওয়ার 'বীজক্ষেত্র' হয়ে উঠল। এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় কোনও কোনও লিটল ম্যাগাজিন নিজেদের 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী' ঘোষণা করে...
'স্বাধীনতা' 'সমাজতন্ত্র' ও 'গণতন্ত্র'-- তিনটি ধারণার রাজনৈতিক প্রয়োগ যথাক্রমে ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬, ১৯৭৭ থেকে ২০০৯-১১ ও ২০১২ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অসফল হয়েছে
অথচ তিনটি ধারণাই আমাদের সংবিধান ধারণ করে আছে...
ধারণ করেছে কিন্তু মানুষের নিত্যদিনের বেঁচে থাকা পরাধীন দেশের থেকেও দুর্বিষহ-- এই দুর্বিষহ বেঁচে থাকা মানুষ গল্পের চরিত্র হয়েছে, দুঃসহ জীবনের কবিতা কথা বাণিজ্যিক পত্রিকায় বিক্রি হয়েছে-- লেখা জীবিকা হতে পারে, এই ধারণা প্রচার হয়েছে তবু, বাণিজ্যিক পত্রিকার বিক্রি কমেছে, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার 'লিটল ম্যাগাজিন' সাহিত্যের বিক্রি বেড়েছে-- এই প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিক পত্রিকার তরফ থেকে, তাদের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে এই মর্মে যে, লিটলম্যাগ আর প্রতিবাদের নয়, প্রতিবাদের ছকবাজিতে বিশ্বাসী (আবা. প. ১১. ০১. ২০০৫)। এবং ঐ একই পত্রিকা, ২৩. ০২. ২০০৫-এ প্রশ্ন তুলল, "লিটল ম্যাগাজিন তার অপ্রিয় সত্যকথা বলার সৎসাহস হারিয়েছে ?"
এখন কমবেশি হাজার দেড়েক পত্রিকা প্রকাশ হয়, তারা লিটল ম্যাগাজিন নামেই পরিচিত। ২০০৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার মূল্যায়ন কতটা ঠিক, অংশত ঠিক তো বটেই, তার পরিবর্তন হয়েছে কি না, বলা মুশকিল তবে ঐ ২০০৫ সালেই অনেকেই ভেবেছিলেন, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় জরুরি, আনন্দবাজারের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যায় এই ভাবনা। কিন্তু আজকের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এ কথা বলা যায় যে, দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতে পারেনি।
একজন ঘোষিত লিটল ম্যাগাজিনের গল্পকারকে জানি, তিনি খুব কম লিটলম্যাগের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন, একইভাবে কম লিটলম্যাগও পৌঁছেছে তাঁর কাছে-- অর্থাৎ খুব কম সম্পাদক তাঁর কাছে গল্প চেয়েছেন-- তাঁর মতে যে সব কাগজ তাঁর গল্প চেপেছে সবই লিটল ম্যাগাজিন, তাদের অনেকেই এখন মৃত, এটা অবশ্য লিটল ম্যাগাজিনের 'নিয়তি'-- তাঁর কাছে যাজন, উবুদশ, শিস, নবান্ন, পরিধি, কুঠার, সাংস্কৃতিক সমসময়-- এ সব লিটলম্যাগের উদাহরণ-- এদের মধ্যে কেউ মৃত, কয়েকটি অনিয়মিত...
সহমত পোষণ করে পৃথকভাবে বলতে হবে, এদের মধ্যে 'সাংস্কৃতিক সমসময়' বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে-- এই পত্রিকাটি এই সময়ের অন্যতম একটি লিটল ম্যাগাজিনের উদাহরণ হতে পারে। যাঁরা ছোট কাগজে্র লেখক-পাঠক, তাঁরা কাগজটি সংগ্রহ করতে পারেন, এমনকি, যাঁরা নতুন কাগজ করতে চান, আশা করা যায়, তাঁরাও অনুপ্রাণিত হবেন-- এ ক্ষেত্রেও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সম্প্রীতি মনন
বিশ শতকের প্রথমে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের 'ছোট কাগজ' প্রকাশ করার প্রেরণা ছিল পরাধীন বেঁচে থাকা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর গ্রাম্য মানুষেরা 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি'-- এই বিশ্বাসে গ্রামে গ্রামে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়' গড়ে তোলার আন্দোলন করেছেন-- সেই গ্রাম্য জীবনেও কোথাও কোথাও লিটল ম্যগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে-- হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন প্রাইমারি স্কুলগুলোর মৃত্যু ঘটছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, এই স্কুলমৃত্যু রুখে দেওয়ার মতো কোনও আন্দোলন নেই-- এই মুহূর্তে লিটল ম্যাগাজিন জনমত তৈরির কাজটি করতে পারে, লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হওয়া জরুরি...
প্রশ্ন হল, 'বাণিজ্যবায়ু'র এই উথালপাথাল সময়ে অবাণিজ্যিকভাবে কি 'লিটল ম্যাগাজিন' প্রকাশ করা সম্ভব? এক কথায়, না। যদি সম্ভব না-ই হয়, তা হলে বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশ করা ভালো নয় কি? অবশ্যই ভালো কিন্তু তা আর 'লিটল' থাকবে না, যেমন একদা লিটল ম্যাগাজিন 'অনুস্টুপ' তার 'লিটল'ত্ব হারিয়েছে!
আমাদের বোধহয় আর-একবার লিটলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমরা বুদ্ধদেব বসুকে উদ্ধৃত করব :
লিটল কেন? আকারে ছোটো বলে? প্রচারে ক্ষুদ্র বলে ? না কি বেশি দিন বাঁচে না বলে? সব ক-টাই সত্য, কিন্তু এগুলোই সব কথা নয়; ওই 'ছোটো' বিশেষণটাতে আরও অনেকখানি অর্থ পোরা আছে। প্রথমত, কথাটা একটা প্রতিবাদ; এক জোড়া মলাটের মধ্যে সবকিছুর আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বহুলতম প্রচারের ব্যাপকতম মাধ্যমিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন : বলেই বোঝা গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনও ছোঁবে না, নগদ মূল্যে বড়োবাজারে বিকোবে না...
অর্থাৎ এর বাণিজ্যিক চলন, চাহিদা অনুসারে জোগান, লাভ-লোকসান ইত্যাদির হিসাব নেই! ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত এই চরিত্রলক্ষণ সাম্প্রতিক সময়েরও প্রতিস্পর্ধী-- 'কর্পোরেট সাহিত্যে'র বিপরীত, তার পণ্যচরিত্র হওয়া চলবে না। এর অর্থ ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা।
এবং এই লড়াইয়ে পাঠকও সামিল হবেন।
অর্থাৎ লেখক-সম্পাদক-পাঠক এই সমাজের সেই সব মানুষ যাঁরা বেঁচে থাকার পরিসরে কোনও না কোনোভাবে অসন্তুষ্ট, অধিকার-বঞ্চিত কিন্তু সচেতন, প্রতিবাদ করতে চান-- প্রতিবাদের ভাষা, কন্ঠস্বরই তাঁদের ঐক্যসূত্র-- লেখক-সম্পাদক প্রতিবাদের ভাষা ধারণ করতে না পারলে তাঁদের কাগজের প্রতি পাঠক বিশ্বাস হারাবেন, এটা স্বাভাবিক...
প্রতিবাদের ভাষা হারানোর নানা কারণ থাকতে পারে কিন্তু সব কারণের কেন্দ্রীয় বিষয়, অস্তিত্ব-- অস্তিত্বের সমস্যা যার মধ্যে লুকিয়ে বা প্রত্যক্ষ থাকতে পারে ভয়-- সকলেই জানেন, ভয় একটি জৈব আবেগ, একমাত্র মানুষই ভয়কে যেমন জয় করতে শিখেছে, তেমনই শিখেছে ভয়ের ব্যবহার, ফলত মানুষের সমাজ অঘোষিতভাবে যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে আছে-- এই যুদ্ধক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের লেখক-সম্পাদকের ভয় থাকবে না, এমনটা ভাবা বোধহয় সমাজবিজ্ঞান সম্মত হবে না যতক্ষণ না সক্রিটিসের মতো তাঁরা সত্যে অবিচল থাকবেন...



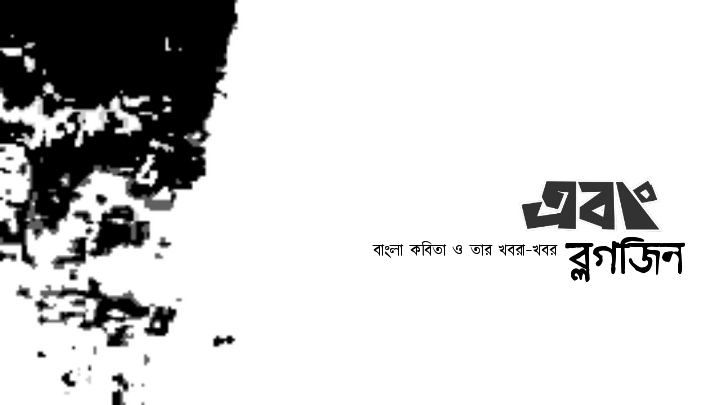
Comments