
সব্যসাচী সেনের দীর্ঘ সম্পাদক-জীবন, কারুবাসয়া পত্রিকা, হাংরি-সাহিত্যের প্রতি এভাবে নিবেদিত থেকে বছরের পর বছর কাজ করে যাওয়া। এই পুরো সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপ, কাজের সূত্রে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা... টুকরো টুকরো যতই শুনেছি, মনে হয়েছে কোনো দাস্তানগোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, দেখা হয়ে ব্যস্ততার মাঝে, উনিও দ্রুত কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন... আমিও ভিড়ে মিশে যাই।
একটা নির্দিষ্ট বায়োডেটার মতোই সব্যসাচীদার উল্লেখযোগ্য কাজগুলির একটি তালিকা রাখা যায়... পাঠকের জানা প্রয়োজন। এখানে রেখে দিলাম। তবে পত্রিকার উদ্যোগে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি সব্যসাচী সেনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে, পর্যায়ক্রমে ওঁর এই যাপন এবং যাত্রাকে চেনার চেষ্টা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো এ-ও দেখি, কত জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া যেত, অথচ নেওয়া হয়নি। আর কোথাও এক ব্যক্তি চৌষট্টিবার সাক্ষাৎকার, তাতেও নতুন কিছু আসে না। পরিস্থিতি। তাই, সব্যসাচীদা 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ'-তে যে সামান্য ভূমিকা দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন, সেখান থেকেই আবার ধরার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে উনি সদয় হলে, আরো কিছু সংযোজন করতে পারব, আশা রাখি... কিছুটা হলেও ডকুমেন্টেড থাকুক। আমি জানব, আমি ভুলেও যাব। অথবা জানাব না। অন্ততঃ যা ডকুমেন্টেড রইল... তা রইল। থাকবে।
সব্যসাচী সেন সম্পাদিত পত্রিকা—
কারুবাসনা' - আত্মপ্রকাশ ২০০৭
'আভাঁগার্দ' - আত্মপ্রকাশ -- ২০১২
সব্যসাচী সেনের প্রকাশিত বইগুলি—
অন্ত্যজ অন্ধকার (কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক: শব্দভেদী)
চেঙ্গিসের ঘোড়া (কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক: কবিতা প্রতিমাসে)
মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ (গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক: প্রতিভাস। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক: শহরতলি প্রকাশনী )
মুক্তির প্ররোচনা ও পথ (কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক: কারুবাসনা)
হেমন্তের কারুবাসনা ও পরাজিতের আখ্যান (উপন্যাস। প্রকাশক: কারুবাসনা)
ক্ষমতা শরীর ও যৌনতা(প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশক: ক্রৌঞ্চদ্বীপ প্রকাশন )
আনন্দভৈরবী (কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক: ক্রৌঞ্চদ্বীপ প্রকাশন)
অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প (গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক: কারুবাসনা)
চার ফ্যাতাড়ুর গল্প (প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশক: কারুবাসনা)
হাংরি জেনারেশন আন্দোলন (প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশক: কারুবাসনা)
ক্ষতিকর কবি শৈলেশ্বর ঘোষ (প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকা
শক: কারুবাসনা)
বাণিজ্য বায়ুর গল্প (কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক: কারুবাসনা)
আলাপচারিতা:
(১) একটু ছাত্রজীবনের কথা বলুন। কলেজ জীবন, সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি... আপনার ওপর প্রভাব।
উত্তর: ছাত্রজীবনের কথা বলতে গেলে একেবারে শুরু থেকে বলতে হয়-আমরা মেদিনীপুরের আদিবাসিন্দা। মা তমলুক মহাকুমার গোপালনগর, পূর্ব বাজারপাড়ার বাসিন্দা। বলা যেতে পারে প্রাচীন শহর তাম্রলিপ্ত-এর মেয়ে। এটি এখন পূর্ব-মেদিনীপুর জেলায়। বাবা, দাসপুর থানার অন্তর্গত জোতঘনশ্যামের বালিচড়া পাড়ার বাসিন্দা- যেটি এখন পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত। ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আমরা মেদিনীপুর থেকে দমদমের লাহা বাগানে চলে আসি। তখন আমাদের সাহিত্যে হাংরি আন্দোলন-এর প্রথম পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে গেছে, নকশাল আন্দোলন প্রায় শেষের দিকে... একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছে, ব্ল্যাক আউট চলছে... চারিদিকে একটা উথাল-পাথাল অবস্থা...
চারিদিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা... প্রতিটি মানুষ তখন লড়ে যাচ্ছে দুমুঠো ভাতের জন্য... ছোটোবেলায় বাবার মুখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নকশাল আন্দোলনের কথা শুনেছি... তখনও এই বিষয়ে কোনো ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হয়নি... হ্যাঁ, বাড়িতে দারিদ্র্য দেখেছি... দারিদ্রের বিরুদ্ধে মায়ের লড়াই দেখেছি...
প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল আমাদের এই অঞ্চলে ২ নম্বর তানোয়ার কলোনিতে অবস্থিত দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয় মা, তখন আমার বয়স আটের কাছাকাছি... তখন চতুর্থ শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা চালু ছিল। বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম। এই বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষিকা ও শিক্ষকের কথা মনে পড়ে... প্রধানশিক্ষিকা কল্পনা দিদিমনি ও অঙ্কের শিক্ষক বাসু মাস্টারমশাই... এইসব শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের হাতে দুষ্টুমি করার জন্য মারও খেয়েছি... ভালোবাসাও পেয়েছি অনেক... সেই শৈশবের দিনগুলো ছিল আনন্দময়। তারপর বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করার পর মা শেঠবাগান আদর্শ বিদ্যামন্দিরে ভর্তি করে দিয়েছিল। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ হলাম। এই অনুত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে একটা কারণ হল- যে বছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছিলাম বাবার চাকরি গেল। দমদম রোডের ওপর সাত নম্বর বস্তির সামনে বাবা সবজি-তরকারির দোকান দিল। সকালবেলা আমি বসতাম। বিকেল বেলায় মা বসত।
আমার জীবনে যাদের প্রভাব বেশি রকম করে পড়েছে, তাঁরা হলেন আমার মা, আমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক অশোক চৌধুরী, ইংরাজি শিক্ষক শেখর দেব ও সহকারী প্রধান শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ পাল। আমার সৃজনশীল কাজের পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা আমার মায়ের। এ ব্যাপারে মা আমাদের ভাইবোনদের সকলকে উৎসাহিত করত। লেখাপড়ার ব্যাপারে মা ছিল ভীষণ কঠোর। লেখাপড়া করতেই হবে। লেখাপড়ার ব্যাপারে মা বলত, 'আমাদের মতো গরীব মানুষের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র লেখাপড়া। লেখাপড়া করেই তোদের বড়ো হতে হবে।' আমরা চার ভাই ও এক বোন। অভাব আমাদের পিছু ছাড়েনি। বাবা লেখাপড়া তেমন পছন্দ করত না, বাবা চাইত আমরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজবাজ করি। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে মায়ের প্রায় গোলমাল হত। মা বাবার কথা কোনোদিনও মানেনি। মা নিজে মেশিন সেলাই করত- ব্লাউজ ও প্যান্ট সেলাই করত। এছাড়া রাতের বেলায় ঠোঙা বানাত। আমি ছিলাম মায়ের হেল্পার। আমি মায়ের কাছ থেকে ঠোঙা বানানো, মেশিন সেলাই ও হেম সেলাই শিখেছিলাম। এইসব কাজ করে মা আমাদের লেখাপড়ার খরচ তুলত। আমি যখন নবম শ্রেণিতে উঠি ছোটো বাচ্চাদের পড়াতে শুরু করি। আমাদের কঠোর শাসনে মা আমাদের সকলকে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। আমাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে বলেছিল-'লেখাপড়া শিখে মানুষ হও।' আমার মা কখনও হিন্দু-মুসলমান এই বিভেদে বিশ্বাস করত না। মা বলত, 'আমরা সকলে মানুষ। সকলের শরীর কাটলে রক্ত ঝরে। তার রঙ লাল।' মা খুব পীর-ফকিরদের পছন্দ করত। বাড়িতে কোনো পীর বা ফকির আসলেই মা আমাদের সকলকে তার কাছে নিয়ে আসত... আর সেই পীর এক অদ্ভুত সুর গান গাইত... তার হাতে চামর থাকত... সেই চামর আমাদের মাথায় বুলিয়ে দিতে বলত। বিনিময়ে মা কিছু চাল আর পাঁচ পয়সা কিংবা দশ পয়সা দিত। মা বিশ্বাস করত- এই গাজী পীরের চামর মাথায় বুলিয়ে দিলে আমরা সকলেই সুস্থ থাকব।
'লালন' শব্দটি প্রথম শুনি আমার মায়ের কাছে। আমার মায়ের গানের গলা ছিল অসাধারণ। মায়ের লালন ফকিরের বেশ কয়েকটি গান মুখস্ত ছিল। মা প্রায়ই গুনগুন করে গাইত। মা একদিন মেশিন সেলাই করতে করতে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...' এই গানটি গাইছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করি, 'মা এই গানটি কার?' মা বলেন, 'লালন ফকির।' মা আরো একটা গান গাইত মাঝেমধ্যে, সেটা হল, 'জাত গেল জাত গেল বলে...' মাকে আরও জিজ্ঞেস করি, 'মা এগুলো কী ধরনের গান?' মা বলেন- 'দেহতত্ত্বের গান।' তারপর থেকে বাউল-ফকিরদের প্রতিআগ্রহী হয়ে উঠি। বাউল-ফকিরদের নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছি। রচনাটি লিখেছিলাম ১৯৯৮ সালে। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'শব্দভেদী' পত্রিকায় ২০০০ সালে। পরবর্তীতে 'কারুবাসনা' ২০২৪ সালে জুন সংখ্যায় পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণ করেছি রচনাটি। তাই আমার মানুষে বিশ্বাস, আমার লালনে বিশ্বাস। আমরা যখন জন্মাই, আর পাঁচটা জীবজন্তুর মতোই থাকি। আমাদের মানুষ হয়ে উঠতে হয়... জন্ম থেকে মৃত্যু- এই দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যেতে হয়। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মানুষ হওয়ার...
(২) একজন আইডল যাকে যুব সমাজের কাছে, ঠিক-ভুল আপেক্ষিক ও বিচার্য। কিন্তু থাকে। কাউকে মনে হত সেই সময়... যিনি/যাঁরা প্রভাবিত করেছিলেন?
উত্তর: প্রথমে আসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা... এরপর চারু মজুমদার... বাবার মুখে প্রথম চারু মজুমদারের নামটা শুনি। তখন আমার বয়স সম্ভবত ছয়-সাতের মতো হবে। তখন আমাদের দমদমে দেখতাম নকশালরা বন্ধ ডাকলে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত... মনে মনে ভাবতাম- কেন মানুষ এত ভয় পায় ওদের?! হ্যাঁ, নকশাল আন্দোলন ও চারু মজুমদার আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমার শৈশবে দেখেছি তখনও দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা ছিল- নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ, চারু মজুমদার জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, ওদের অনেক ত্রুটি ছিল, তবুও ওরা আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মতো অসৎ ছিলেন না- সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু স্যানাল, সরোজ দত্ত... দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ...।
একটু পেছন ফেরা যাক- কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম সেই অষ্টম শ্রেণী থেকে। সেসময় কেমন এলেবেলে আলবাল লিখে যেতাম বঙ্গলিপি খাতায়। ১৯৮৫ সালে, যেদিন মীরাপিসির সাথে দেখা, সেদিন রাতে একটি কবিতা লিখলাম, 'স্বপ্ন বিষয়ক লাল ইস্তেহার'। আমার তখন দুজন খুব প্রিয় বন্ধু- তথাগত ও স্বরূপ। তথাগত খুব সাহসী লড়াকু ছেলে, প্রতিবাদী ও সৎ। ওর বাবা সিপিএমের পার্টিমেম্বার ছিল। আশির দশকে শালখিয়া প্লেনামের পর পার্টিমেম্বারশিপ ছেড়ে দেন। আমার মতো স্বরূপও কবিতা লিখত। ও আর্থিক দিক থেকে বেশ স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। ওর প্রচুর কবিতা বই কিনত। আমি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান। আমার তখন খুব একটা বইপত্র কেনার ক্ষমতা ছিল না। ওর বাড়িতে আমার খুব যাতয়াত ছিল। আমি ওর থেকে বিভিন্ন সময় বইপত্র চেয়ে এনে পড়তাম। এর আগে ওর থেকে চেয়ে এনে পড়ে ফেলেছি কবি নবারুণ ভট্টাচার্যের 'মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কাব্যগ্রন্থটি। স্বরূপ আমাকে একদিন পড়তে দিল কবি মৃদুল দাশগুপ্তের 'জলপাই কাঠের এসরাজ' কাবগ্রন্থটি। সেখানে 'আগামী' নামে একটি কবিতা ছিল। ওই কাব্যগ্রন্থের আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা। ওই কবিতার দুটি পংক্তি আমার উক্ত কবিতাটির ভেতর কেমন করে যেন ঢুকে গেল- 'টাঙ্গি হাতে ছুটে গেল কার্তিক কাহার', 'সোনার টুকরো ছেলে দ্রোণাচার্য ঘোষ'।
১৯৮৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে কলেজে ভর্তি হলাম। এসএফআই-এর সংস্পর্শে এলাম। ওরা আমাকে কলেজ নির্বাচনে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। আমি দাঁড়াইনি। বাবার কথা মনে রেখে ওদের বুঝে নিতে চাইছিলাম। তবে ওদের সমর্থন করেছিলাম। বন্ধু তথাগত নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিল। ও জিতেছিল। এই নির্বাচনে এসএফআই জয়ী হল। এসএফআই পেলো ৩৯ টি আসন। আর সিপি পেলো ২১ টি আসন। আমরা পূর্বের দুর্নীতিগ্রস্ত জিএস শুভেন্দু ঘোষকে সরাতে চাইছিলাম। সেও জিতেছিল কলেজ নির্বাচনে। গোলমাল বাঁধল জিএস নির্বাচন নিয়ে। সিপিএম-এর নেতারা চাইছিলেন শুভেন্দু ঘোষই জিএস থাকুক। শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা মতো ভোটাভুটি হল। ৩৬- ৩ ভোটে আমাদের প্রার্থী বিষ্ণুনারায়ণ দেব জিএস হল। এ ব্যাপারে তথাগত আর আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলাম। ফলে আমরা লোকাল সিপিএম নেতৃত্বের রোষের মুখে পড়লাম। আমরা কলেজে ছাত্র ভর্তিতে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। ওরা ছাত্রদের কাছ থেকে লেখা চাইল। কলেজ ম্যাগাজিনে 'স্বপ্ন বিষয়ক লাল ইস্তেহার' কবিতাটি দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা চারু মজুমদারের নাম দেখে ক্ষেপে উঠল। ওদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠাল। জোনাল অফিসে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে ওদের এক নেতা আমাকে বলল, 'ষাট-সত্তর দশকে এ ধরনের কবিতা লেখা হত। এখন এসব অতিবিপ্লবী ও হঠকারী কবিতার কোনো মূল্য নেই।' বাতিল হয়ে গেল আমার কবিতাটি-প্রকাশ পেল না আমার প্রথম কবিতা... পরবর্তীতে 'শব্দভেদী' পত্রিকায় সেই কবিতাটি ছাপা হয়। এইসব ঘটনাগুলো 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ও তাহার পর' নামক আমার লেখা একটি লেখায় এসেছে; যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কালি কলম ইজেল' নামক একটি পত্রিকায়। নির্লজ্জভাবে বলি এই লেখাটি নিয়ে 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্সেস' নাট্য সংস্থা প্যান্ডেমিকের আগে একটি নাটক প্রযোজনা করে 'হেমন্ত ও তাহার পর' নামে।
একসময় পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বোস ও চারু মজুমদার ছিল আমার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে যুক্ত হল গান্ধীজি। আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা বাইনারি আছে সুভাষ চন্দ্র বোস ও গান্ধিজীকে নিয়ে... বাঙালি যতটা সুভাষচন্দ্র বোসকে ভালোবাসে; গান্ধিজীকে ততটা নয়। পরবর্তীতে গান্ধিজীকে যত জেনেছি মানুষটার ওপর শ্রদ্ধা তত বেড়ে গেছে।
(৩) হাংরি প্রজন্মের লেখার সঙ্গে পরিচয়, এবং ক্রমে সেই লেখকদের সঙ্গে পরিচয়... এটা ঠিক কোন সময় থেকে? কোনো বিশেষ ঘটনা আছে? কাউকে মনে পড়ে?
উত্তর: দেখো, এককথায় এই উত্তরটা দেওয়া যাবে না। একটু পেছন ফিরি... সালটা ১৯৯১ কি ১৯৯২ হবে... বন্ধু রঞ্জয়গোপাল সরকার-এর কাছ থেকে আমি হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারি... তখন ও আর আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে সেলস রিপ্রেজেন্টটেটিভের কাজ করি... ওঁর দাদা সঞ্জয়গোপাল সরকার 'কোরক' পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যায় জীবনানন্দের প্রচ্ছদ করেছিলেন... এক ছুটির দিন, সম্ভবত রোববার হবে, রঞ্জয় আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তখন আমি লেখালেখি করছিলাম। আমার লেখা পড়ে বলেছিল- তোমার লেখালেখি অনেকটা হাংরিদের মতো। তখনই প্রথম জানতে পারি হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কথা। তারপর শুরু হাংরি সাহিত্যের খোঁজ... সকালে সেলেসের কাজ করতাম। কাজ থেকে ফিরে এসে সন্ধে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বেশ কয়েকটা টিউশনি করতাম। তারপর সেলসের কাজ ভালো না লাগায় সেটা ছেড়ে দিয়ে টিউশন করতে শুরু করলাম। সংসারে অনেকটাই টাকা দিয়ে দেওয়ার পর নিজের জন্য কিছুটা টাকা সরিয়ে রাখতাম। ওই টাকা দিয়ে বই কিনতাম। প্রায় প্রতি বুধবার অথবা সপ্তাহের কোনো একদিন আমি আর আমার বন্ধু অরূপ দাস কলেজ স্ট্রিট যেতাম। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে অল্প পয়সায় নিজের পছন্দের পুরোনো বই কিনতাম। এছাড়া 'পাতিরাম' থেকে মূলত লিটল ম্যাগাজিন আর 'দে বুক স্টোর' থেকেও বই কিনতাম। ওরা বইয়ের ওপর কুড়ি শতাংশ ছাড় দিত। এখনও দেয়। আর ওদের ওখানে সব বই-ই মোটামুটি পাওয়া যায়। একদিন বন্ধু রঞ্জয়গোপাল খবর দিল মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি কিংবদন্তী' নামক বইটার। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস, সেই বছর 'দে বুক স্টোর' থেকে প্রকাশিত হয় মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি কিংবদন্তী', মূল্য ছিল ২৪ টাকা। হাংরি নিয়ে পড়া ওটাই আমার প্রথম বই। ওখানে কবি শৈলেশ্বর ঘোষ-এর একটি কবিতা ছিল- 'ক্রুর অভিনয়'। ভালো লেগে যায় কবিতাটি। তারপর খুঁজতে থাকি শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা আর জানতে চেষ্টা করি এই আন্দোলন সম্পর্কে। তারপর এক শনিবার কলেজ স্ট্রিটে গেছি-পাতিরামে পত্রপত্রিকা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ-এর 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' গ্রন্থটির ওপর। বইটির দাম তখন ছিল ৩০ টাকা। সালটা ১৯৯৫, সম্ভবত এপ্রিল-মে মাস। বইটা প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে। পাতিরাম থেকে বইটা তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করি। ওখান থেকে কবি শৈলেশ্বর ঘোষ-এর ঠিকানা সংগ্রহ করি- এ/৮ লেক ভিউ পার্ক, কলকাতা-৩০। তাঁকে এই ঠিকানায় চিঠি লিখি তাঁর বইপত্র পাওয়ার জন্য। উনি চিঠির উত্তর দেন। চিঠিতে একদিন যেতে বলেন ওঁনার বাড়িতে। চিঠির নির্দেশনা দেখে ওঁনার লেক ভিউ-র বাড়িতে পৌঁছুই। উনি আমাকে ওঁনার বইগুলো দেন। কিন্তু পয়সা নেননি। তারপর ওঁনার বাড়িতে যাওয়া-আসা... দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে হাংরিদের নিয়ে পড়াশুনা করছি...
আমাকে হাংরি আন্দোলন যেমন প্রভাবিত করেছে। তেমনি নকশাল আন্দোলনও। আমি নকশাল আন্দোলনের কথা আগে জেনেছি, পরে জেনেছি হাংরি আন্দোলনের কথা। যদিও হাংরি আন্দোলন আগে ঘটেছিল, পরে ঘটেছিল নকশালন আন্দোলন।
(৪) শৈলেশ্বর ঘোষ এবং আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ আপনার কাজে এবং লেখায় এসেছে। এ নিয়ে সামান্য কথা হয়েছে। শুরুর দিকের আলাপ কেমন? নতুন প্রজন্মের সঙ্গে এমন ব্যক্তিত্বদের যদি পরিচয় করিয়ে দিতে হয়... যারা দৃশতই একটি কারখানা এবং ব্রয়লারের কাজ দেখছে... কিছু ভাবেন এই নিয়ে? কীভাবে রিসিভ করছে এখনকার তরুণ পাঠক?
উত্তর: ২০০৭ সালে পুজোর আগে প্রকাশিত হল কারুবাসানার প্রথম সংখ্যা। ঠিক করেছিলাম প্রথম সংখ্যাই হবে 'শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা'। কিন্তু যখন এই সংখ্যাটি করার প্রস্তাব নিয়ে শৈলেশ্বর ঘোষের কাছে যাই... তখন কবি শৈলেশ্বর ঘোষ আমাকে একপ্রকার ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'দেখুন সব্যসাচী, আমি যদি কিছু লিখে থাকি তবে আমি থাকব। না হলে থাকব না। এইসব সংখ্যা-টংখ্যা করেও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।' মানুষটাকে রাজি করাতে আমার প্রায় মাস পাঁচ-ছয়েকের সময় লেগেছিল। ইতিপূর্বে সম্পর্কটা কখনও 'আপনি' কখনও 'তুমি'- এইভাবে চলছিল... তারপর সম্পর্কটা ধীরে ধীরে 'আপনি' থেকে একদিন 'তুমি'তে এল। 'কারুবাসনা'র প্রথম সংখ্যায় আমাকে লেখা কিছু লেখক-কবির চিঠি ছেপেছিলাম। পত্রিকা হাতে পেয়ে উনি আমাকে বললেন। 'তোমাকে লেখা এইসব কবি-লেখকের চিঠি ছেপে তুমি কী প্রমাণ করতে চাও, বাংলা সাহিত্যের অনেক লোক তোমাকে চেনে!' প্রাথমিক ভাবে একটা ধাক্কা খেলেও আমি সেদিন তাঁর সেই কথায় রাগ করিনি। বারেবারে ভেবেছি... এই লোকটাকে নিয়ে সংখ্যা করব, জেনেও এই লোকটা এরকম কথা বলছে! সেদিন থেকে মানুষটার ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। সেদিন যদি এই কথা শুনে ওঁনার রাগ করে চলে আসতাম, তাহলে আর 'শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা' করতে পারতাম না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম- তাকে লেখা দেশি-বিদেশি লেখক-কবিদের অসংখ্য চিঠি, যা কোনোদিন তিনি একটাও তাঁর সম্পাদিত 'ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ' বা তাঁদের 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় ছাপেননি। তখন আরও লজ্জিত হয়েছি। মানুষটার কাছে, শিখেছি কী করে নিজেকে একা করে নিতে হয়। কী করে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। ওঁনার শেখানো প্রত্যাখ্যানের আনন্দ নিয়েই তো বেঁচে আছি।
শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা পাঁচশ কপি করেছিলাম। শুনে বলেছিলেন, 'করেছো কী! আমার তো কুড়িজন পাঠক। দেখো কতদিনে যায়!' সংখ্যাটা করতে হাজার পঁচিশেক টাকা লেগেছিল। দশহাজার টাকা ধার হয়েছিল। বারবার জিজ্ঞেস করতেন, 'কত টাকা খরচ হল?' আমি বলেছিলাম, 'ছাড়ুন ওসব।' নিজে একসময় কাগজ করতেন। সবই বুঝতেন। একদিন বললেন, 'আমার দশটা শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা' লাগবে।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, পরে আবার যেদিন আপনার বাড়িতে আসব, সেদিন আপনাকে দিয়ে যাব।' দশটা 'শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা' দেবার পর আমাকে হাজার টাকা দিতে চাইলেন। আমি তো কিছুতেই নেব না। আমাকে বললেন, 'তুমি যদি এই টাকা না নাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।' বাধ্য হয়ে টাকাটা নিয়েছিলাম। বন্ধু শিল্পী দেবাশিস সাহা প্রচ্ছদ করে দিয়েছিল। ও পয়সা নেয়নি। যে দশহাজার টাকা ধার হয়েছিল। সেটা শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা বিক্রি করেই শোধ করেছি। আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এই সংখ্যাটি কত টাকা খরচ হতে পারে। কারণ নিজেও তো একসময় পত্রিকা করেছেন। ওনার বাড়িতে অনেক 'কালু ফকিরের আজান' ও 'এত আলো আসে' ছিল। আমাকে দশটা করে দিয়েছিলেন। বইমেলায় বইগুলো বিক্রির পর টাকা দিতে গেলেও নেননি। আমার আর্থিক পরিস্থিতি জানতেন। নিজেই ফোন করতেন। সকলকে আপনি করে বলতেন, আমাকে প্রথম দু-একবার 'আপনি' করে বললেও সারা জীবন 'তুমি' করে বলতেন। পরে আমাকে নিজে থেকে দুটো বই করার কথা বলেছিলেন। 'আমাদের এই বীজক্ষেত' ও 'হাংরি আন্দোলনের সত্যমিথ্যা'। কেন বলেছিলেন, তাও জানি। বইদুটো করি, টুকটাক বিক্রি হচ্ছিল। রয়ালটি দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু নেননি। বলেছিলেন, 'ছিঃ তোমার থেকে আমি রয়্যালটি নেব। তাহলে তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।' সত্যিই আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি। অবাক হয়ে থেকেছি। আরও বেশি করে মানুষটাকে ভালোবেসেছি। এতে যদি স্বঘোষিত হাংরি মহাগুরু ও তাঁর ভক্তশিষ্যরা আমাকে 'শৈলেশ্বর ঘোষের চাকর-বাকর', 'শৈলেশ্বরের চামচা' পুরস্কার দেয়, তাতে আমি গর্বিত বোধ করি।
হাংরিদের আরও দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সুভাষ ঘোষ ও প্রদীপ চৌধুরী। এছাড়া সুবো আচার্য-এর সঙ্গে দু-একবার সাক্ষাৎ হয়েছে।
আর একজন সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল... যদিও তিনি হাংরি নন, তবু তার লেখা আমাকে আকর্ষণ করে এবং মুগ্ধ করে।
বাংলা সাহিত্যে সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। ফলত এই ধরনের কবি লেখকদের পাঠক সংখ্যা খুবই কম।
(৫) 'স্মৃতির আর এক নাম অসুখ'- এই কথাগুলো আপনার কাছ থেকে মাঝে মাঝে আসে... এর মধ্যে এক দর্শন ভেসে আসতে দেখি বার বার। এই সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ নিয়ে কিছু বলবেন?
উত্তর: 'স্মৃতি' আমার কাছে হল 'পেছন ফিরে দেখা...' বলতে পারো অতীতকে ফিরে দেখা... যতটা পারা যায় খুঁড়ে খুঁড়ে দেখা... আমার মা বলত, আমার বড়ো ছেলের স্মৃতি খুব প্রখর। হ্যাঁ, মায়ের এই কথাটার অনেকটাই ঠিক। আমি আমার বা আমাদের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ভুলি কম। আমাদের পারিবারিক জীবনে সুখের স্মৃতি থেকে বেদনার স্মৃতিই বেশি। আর সময় ছাড়া স্মৃতির অস্তিত্ব হয় না। শুধু সময়ের পটভূমিতে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। স্মৃতি কখনও মানুষের মনে প্রগাঢ় অতৃপ্তি এনে দেয়। স্মৃতি কখনও অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। তখন এই অতৃপ্তি আমৃত্যু অসুখ হয়ে দাঁড়ায়। মুরাকামি বলেছিলেন স্মৃতি কখনও মানুষকে কাঁদায়, আবার কখনও উত্তেজিত করে। প্রথমে ভেবেছিলাম নাম রাখব 'হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি' অথবা 'স্মৃতির সরণি'... কিন্তু ভালো লাগছিল নামটা। তারপর একদিন সুভাষ ঘোষ-এর বইটির কথা মনে পড়ে যায় 'স্মৃতির এক নাম অসুখ'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে। 'গ্রাফিত্তি' থেকে শুভদা বার করেছিল। কনকদি সুভাষদার লেখা থেকে এই শব্দগুলো নিয়ে নামকরণ করেছিল। হাংরি গদ্যকার সুভাষ ঘোষ বলেছিলেন, 'স্মৃতির এক নাম অসুখ'। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আমার নতুন উপন্যাসের নাম রেখেছি, 'স্মৃতির আর এক নাম অসুখ'। সুভাষ ঘোষের কাছে রয়ে গেল আমার অপরিশোধ্য ঋণ।
(৬) দশকগুলোর মধ্যে যে ট্রানজিশন, প্রায় পাঁচ দশক অতিক্রম করে- এখন কেমন লাগে? মানুষ হিসেবে, বাঙালি হিসেবে, একজন দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় সম্পাদক হিসেবে?
উত্তর: পত্রিকা করা একটা যুদ্ধ। বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিন করা... লিটল ম্যাগাজিনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল আর্থিক সমস্যা... আর একটি সমস্যা হল লেখা পাওয়ার সমস্যা। আমি যে ধরনের পত্রিকা করি, সেই ধরনের লেখকের সংখ্যা একেবারেই নগন্য... এ ব্যাপার তোমরা হয়তো আমাকে প্রশ্ন করতে পারো আপনি কী ধরনের পত্রিকা করেন?
আমি 'আঁভাগার্দ ভাবনা'র পত্রিকা করি। প্রশ্ন হতে পারে 'আভাঁগার্দ ভাবনা'টি কেমন? 'আভাঁগার্দ' একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ 'এগিয়ে থাকা সেনাদল বা অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী'। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে থাকা সেনাদল। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম আক্রমণটা তাদেরকেই করতে হয় শত্রুপক্ষের ওপরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আভাঁগার্দ' কবি-লেখকরা তাই করেন। রোলাঁ বার্ত দু-ধরনের আভাঁগার্দ-এর কথা বলেছেন- (১) ক্যাথেটিক: এক ধরনের টীকা বা ভ্যাকসিন, যা মূল্যবোধের শক্ত আস্তরণ ভেদ করে একটি মুক্ত চিন্তা নিয়ে আসে, কিন্তু যার উৎস অসুস্থতার মধ্যেই আবদ্ধ। এটিকে সহজ আভাঁগার্দ মনে করেছেন তিনি। (২) র্যাডিক্যাল: ক্যাথের্টিকের বিপরীত দিকে যে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, তা অনেক বেশি র্যাডিক্যাল। সমাজ বাস্তবের কাঠামোকে অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আক্রমণ। রাজনৈতিক বিবেককে প্রকাশ করাই প্রকৃত আভাঁগার্দ সাহিত্য। রোলা বার্ত বয়ান বা টেক্সটকেও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন একটি হল (১) রিডারলি, আর একটি (২) রাইটারলি। রিডারলি বয়ান হল পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্য করার জন্য যে বয়ান নির্মিত হয়। এখানে পাঠককে কিছু ভাবতে হয় না। এটি হল একরৈখিক। আর রাইটারলি বয়ান যেগুলি লেখক স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে চলেন, যার নির্দিষ্ট কোনো ছক বা আকার নেই। রাইটারলি টেক্সটে অনেক ফাঁক বা শূন্যতা থাকে, বহুস্বর ও বহুস্তর থাকে। ফলত, এ ধরনের বয়ান পাঠককে ভাবায়।
পাঠক নিজের মতো করে সেই শূন্যতাগুলি ভরিয়ে নিতে পারেন।
এবার আসি 'আভাঁগার্দ' কবি-লেখকদের কথায়। যেমন ধরো কবি ফালগুনী রায়-এর কথা। হাংরিদের সঙ্গে ছিলেন... কবি ফালগুনী রায় লিখেছিলেন- 'কবিতা লেখার জন্য আমি কোনো কাগজ পাচ্ছি না।' কী লিখতেন ফালগুনী- যে লেখার জন্য তিনি কাগজ পেতেন না? ফালগুনী রায়ের একটা লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। '... মেরুদণ্ডের/ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের আত্মপ্রত্যয়- তবু মানুষ কুঁজো হয়ে যায়/ শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ে কেউ পুণ্য সঞ্চয় করে- কেউ ভাইবোনের/যৌন সংগমের সংবাদ পায় অই গ্রন্থ পড়ে-পোয়াতীর পেট থেকে/বেরিয়ে মেয়েরা ফের পোয়াতী লিঙ্গদ্বারে প্রকাশোন্মুখ/মানুষের ভ্রূণ তুমি কি কথা বলতে পারো- চিন্তা ক্ষমতা/আছে কি তোমার...।' (ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি)
'বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ/আমি ভাইফোঁটার দিন হেঁটে বেড়াই বেশ্যাপাড়ায়।' (মানুষের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই)।
একদিন পুরুষের মূত্ররন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মহাপুরুষের ভ্রুণ বীজ একদিন লেনিন বলেছিলেন, আমার গা থেকে ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিলেও দু-লাইন কবিতা বেরুবে না- আর আজ লেনিন অনুগামীরা কবিদের দিকে ব্রেনগান তুলে বলছে- 'উঁহু ওরকম নয় এরকম লিখুন আমি দেখতে পাচ্ছি রাইফেল ও কবিতা দুজনেরই ম্যাগাজিন দরকার। (ব্রেনগান)
আসলে হাংরিরা সকলেই কুবাক্য লিখতেন। আর কুবাক্য লিখলে তুমি লেখার জন্য কোনো পত্রিকা পাবে না। বাংলা সাহিত্যের অন্যরকম গদ্যকার কমলকুমার মজুমদার একদা বলেছিলেন: 'ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই বাঁচায়।' হাংরিরা সেই ভাষাকেই আক্রমণ করে ফেলেন, যা দিয়ে পুঁজিবাদী-ধনতান্ত্রিক-রাষ্ট্র- ক্ষমতা-পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি একককেই নিয়ন্ত্রণ করে- হাংরিরা পুঁজিবাদের এই নিয়ন্ত্রণের মূলস্থানে মোক্ষম আঘাতটি করে ফেলেন। ফলত, তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়- তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রক্ষমতা অশ্লীলতার অভিযোগ আনে- গ্রেপ্তার, পুলিশী অত্যাচার, মামলা-মোকদ্দমা, আইন- আদালত... চলতে থাকে সামাজিক আক্রমণ।
ব্যাকরণবিদ সুনীতিবাবুর ভাষায় হাংরিরা অবশ্যই অসাধুভাষী। কেন্দ্রীয় ভাষা বিরোধী। আসুন এবার আমরা দেখি- স্ট্যান্ডার্ড ভাষার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাকরণবিদ (ব্রাহ্মণ) বাংলা ব্যাকরণের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন, "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটি সবদিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধরূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেই রূপে) ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে আলাপ করিতে পারা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়।” (ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মে ১৯৮৯, রূপা অ্যান্ড কোঃ পৃ. ৯) অভদ্র রাখাল বলল, আমি তোমাদের এসব বালের ব্যাকরণ-ফ্যাকরণ মানি না। একমাত্র রাখালই বুঝতে পারে, 'I was born intellegent but education ruined me.' (নোয়াম চমস্কির শিক্ষাভাবনা, অনুরাধা দে, জানুয়ারি ২০০৮, আলোচনা চক্র) তাই চমস্কির মতো রাখালই বলতে পারে, 'Those of you who have been through college know that the educational system is very highly geared to rewarding conformity and obedience: if you don't do that, you are a trouble maker.' (নোয়াম চমস্কির শিক্ষাভাবনা, অনুরাধা দে, জানুয়ারি ২০০৮, আলোচনা চক্র) এই trouble maker-টি হল রাখাল। অতএব হাংরিরাও ওই trouble maker এক-একজন রাখাল, মধ্যবিত্ত বাবুসমাজের কেউ নন, তাদের রচনা ভদ্র-মধ্যবিত্ত-বাবু সমাজের অস্বস্তির কারণ। তাদের রচনায় ভদ্র-সুশীল-সমাজের অপ্রিয়, অশ্লীল শব্দ ও বাক্য, নিষিদ্ধ বিষয় অনায়াসে ঢুকে পড়ে। হাংরিরা বাংলা ব্যাকরণগত শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে অস্বীকার করেন তাঁদের রচনায়। হাংরি জেনারশন সাহিত্য আন্দোলনকারীরা প্রথমদিকে প্রায় সকলেই মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাস করতেন। আমার মনে হয় মার্কসের চিন্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা অনুভব করেছিলেন জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাতেও ডি-ক্লাস বা শ্রেণিচ্যুতি ঘটাতে হবে। সেইজন্যই তারা সর্বহারা বা প্রান্তিক মানুষের ভাষাকে, যা সুনীতিবাবুর ভাষায় অসাধু-অভদ্র ভাষা, সেটাকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এদেশের মাকর্সবাদী দলের নেতারা প্রায় সকলেই এসেছিলেন উচ্চ-অভিজাত সমাজ থেকে। তারা সর্বহারা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের হয়ে বিপ্লব করতে চাইলেন ঠিকই; কিন্তু এইসব প্রান্তিক ও সর্বহারা মানুষের ভাষাকে গ্রহণ করলেন না। উলটে তাদের ভাষাকে 'অশ্লীল বা অসাধু' আখ্যা দিলেন। এই হিপোক্রেসির জন্যই তাদেরও চোখে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারী হয়ে যান অশ্লীল ভাষার লেখক এবং এদের নিকট নৈরাজ্যবাদী ও অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে যান। কিন্তু হাংরিরা এসব বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে নিচুমানুষের ভাষায় অনায়াসে লিখে গেছেন তাদের রচনাগুলি।
হাংরি গদ্যকার সুভাষ তাদের বা তার ভাষাকে বলতেন, 'গা-গতরের ভাষা'।
আসলে হাংরি কবি-লেখকরা কালচার ইন্ডাস্ট্রি-নির্দেশিত বাণিজ্যিক ছকে বা ভাষায় লেখেননি। তাঁদের রচনার ভাষা 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'কে সেবা প্রদান করেন নাই। 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' ধারণাটি আমরা 'ফ্রাঙ্কফুট স্কুল'-এর তাত্ত্বিক অ্যাডার্নোর কাছ থেকে পেয়েছি। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলা যাক- আমাদের মূল ধারার সাহিত্য' বলে যা আজ পাঠকের কাছে পরিচিত তার অধিকাংশই বাজারের স্বার্থে উৎপাদিত হয়। 'গণসংস্কৃতি' হিসেবে যা আমাদের কাছে পরিচিত, তার উৎপাদন জনগণের ভেতর থেকে উৎপাদিত হয় না, তা উৎপাদিত হয় বাণিজ্য স্বার্থ সম্বলিত নির্দেশিত পথে। এভাবে যে সাহিত্য রচিত হয় বা উৎপাদিত হয়, তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বা অস্ত্র হিসেবেই কাজ করে। 'Culture has become openly, and defiantly, an industry obeying the same rules of production is an integrated component of the capitalist economy as a whole.' (Introduction, The culture industry, Theodor W. Adorno, Routledge, 2010, page-9) সংস্কৃতির আজ পণ্যায়ন ঘটেছে। সংস্কৃতি আজ কারখানায় উৎপাদিত শিল্পের মতো। পুঁজিবাদী অর্থনীতি সংস্কৃতিকে স্থিতাবস্থার পক্ষেই চালিত করে। আর হাংরি রচনাগুলি এই সংস্কৃতির কারখানার কোনো ছাঁচে বা ছকে উৎপাদিত হয়নি। তাদের রচনাগুলি 'আভাঁগার্দ সত্তা' থেকে রচিত। 'আভাঁগার্দ' একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ 'এগিয়ে থাকা সেনাদল বা অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী'। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে থাকা সেনাদল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম আক্রমণটা তাদেরকেই করতে হয় শত্রুপক্ষের ওপরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আভাঁগার্দ' কবি-লেখকরা তাই করেন। তেমনই বাংলা সাহিত্যে হাংরি কবি-লেখকরা তাদের রচনার দ্বারা পুঁজির ভাষাকে আক্রমণ করে ফেলেন। তাঁদের রচনাগুলি মূলধারার বাংলা সাহিত্যের স্থিতাবস্থা ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছিল। ফলত, শুধু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়, কালচার ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্য-প্রিয় কবি-লেখকদের দ্বারা আক্রান্ত 'হাংরি' বা 'ক্ষুধার্ত'রা।
হাংরি রচনা পাঠ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা আভাঁগার্দ সত্তা থেকেই সংগ্রহ করেন অন্তর্ঘাতের আয়ুধ। গেরিলা হাংরি রচনাকাররা ভাষাকে অলআউট আক্রমণ করেন ওই অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যই। গদ্যকার সুভাষ ঘোষ আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন- 'বুর্জোয়ারা ভাষার ভেতর নির্মাণ করে আশ্রয়ের শেষ দুর্গ।' ওই বুর্জোয়াদের খপ্পর অর্থাৎ হাত থেকে ভাষাকে বের করে আনা'ই ছিল হাংরিদের প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টা থেকেই তাঁরা রচনা করেন- চিরাচরিত
বহুল প্রচলিত পুরোনো পদ্ধতিতে নির্মিত বয়ান থেকে সরে এসে; পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাজারের ভাষাকে অস্বীকার করে; প্রত্যাখ্যানের ভাষায় তৈরি করেন প্রত্যাখ্যানের বয়ান, যার দ্বারা এই পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সমাজের গায়ে মারাত্মক ফাটল ধরিয়ে দেন। এখান থেকে তাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নিন্দিত হন। স্বাভাবিক ভাবেই হাংরিরা নৈরাজ্যবাদী হয়ে যান এদের সকলের কাছে।
আমাদের তথাকথিত বাঙালি কবি-লেখকরা অধিকাংশই প্রতিষ্ঠান বলতে এখনও দেশ ও আনন্দবাজারকেই মনে করেন। এই গণমাধ্যমের বিরোধিতাকেই তারা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মনে করেন। আমাদের অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনও এই ধারণাই পোষণ করেন। তবুও তারা 'দেশ-আনন্দ'র মতোই পত্রিকা উৎপাদন করে। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রই হল সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে মজবুত ভিতটি হল পরিবার। এই পরিবারেই একটি শিশু জন্মায়, বড়ো হয়, বিদ্যালয়ে যায়, পড়াশুনা করে এবং আকাদেমিক ডিগ্রি লাভ করে, বিভিন্ন কাজকর্ম করে, তারপর একদিন বিবাহ করে, সন্তান জন্ম দেয়। এই মানুষ আবার একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। এইভাবে সে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে এবং প্রতিষ্ঠানের সেবাদাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ বিষয়টাকে যদি এভাবে বলি, পরিবার- বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়- বিশ্ববিদ্যালয়- সরকারি-বেসরকারি অফিস-চিকিৎসালয়-জেলখানা- উন্মাদাগার- আদালত- পুলিশ- মিলিটারি- গণমাধ্যম- আরো ছোটো বড়ো প্রতিষ্ঠান নিয়ে তৈরি রাষ্ট্র নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির। আমরা এসব ফুকোর থেকে জেনেছি। ফুকোর কাছ থেকে আরো জেনেছি, কীভাবে প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতা নীতি-নৈতিকতার সাহায্যে গড়েপিটে নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরটাকে দখল করে নেয়। এই নীতি-নৈতিকতা দিয়েই তৈরি করে নেয় অনুশাসন। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক- প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতা ঠিক করে দেয় আমরা কী করব, আর কী করব না। এই অনুশাসন দিয়েই শৃংখলা বা শৃংখল পরিয়ে দেয় মানুষকে। পূর্বে প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতা মূলত শাস্তির মাধ্যমে এই কাজ সেরেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সে সার্বভৌম শাস্তি বা যথেচ্ছ শাস্তি (শরীরের ওপর অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ড) থেকে অনেকটা সরে এসে অনুশাসনের মাধ্যমেই এই কাজটি সেরেছে।
আমাদের কথা বলা, চলা-ফেরা, পড়াশুনা, এই জীবনযাপন অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ আমরা বুঝতে পারি না। ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠান তার মতো করে তৈরি করে নেয় একপাল সুবোধ বালক সাধুভাষী গোপাল। যে কখনও কুবাক্য বলে না। গোপালদের তার দরকার। কারণ গোপাল ভালো ছেলে। উৎপাদক জীব। সে বাজারের সঙ্গে ফিট করে যায়।
রাখালদের তার দরকার নেই। কারণ রাখাল খারাপ ছেলে, ফাঁকিবাজ, খারাপ কথা বলে; অর্থাৎ কুবাক্য বলে এবং লেখাপড়া করে না। অনুৎপাদক জীব। কুবাক্য বলা রাখাল তাই অপরাধী। তাই সে গুরুমশাইদের হাতে মার খায়। রাষ্ট্র তার শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। তার কৃৎকৌশলের দ্বারা আমরা সকলেই নিয়ন্ত্রিত হই। সাহিত্য- ভাষাকেও সে নিয়ন্ত্রিত করে। কেউ যাতে এর বাইরে না থাকে সেজন্য ক্ষমতা তার ওই শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নজরদারি চালায়। প্রাতিষ্ঠানিকতা বা ক্ষমতা আমাদের শরীরের অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করে গেছে। আমরা সকলেই এই প্রাতিষ্ঠানিক ফাঁদের ভেতর আছি। আমরা অধিকাংশ এই ফাঁদের ভেতরেই থাকতে চাই। যদি চেষ্টা করি একমাত্র আমরা চেতনাকেই এর বাইরে রাখতে পারি। তবে সকলে নয়, একমাত্র চেতনাসম্পন্ন মানুষই বা প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা কবি-লেখকই এটা করতে পারেন। কিন্তু তারজন্য তাকে চরম আত্মত্যাগ করতে হবে। একাজের জন্য ক্ষমতা তাকে ক্ষমা করবে না। তার ওপর নানাভাবে অত্যাচার নেমে আসবে। প্রতিষ্ঠান সেবিত পত্র-পত্রিকা তার রচনা নেবে না। তাঁর রচনাকে চরমভাবে ঘৃণা করবে। তবু তাকে বিচলিত হলে চলবে না। পুরস্কার তো সে পাবেই না বরং ঘর-বাহির তাকে তিরস্কারে তিরস্কারে জর্জরিত করবে। কবি-লেখক ভেকধারী প্রতিষ্ঠানের দালাল অক্ষম পুরস্কারলোভী ভণ্ড তাঁর রচনা নিয়ে উপহাস করবে। তবু তার বিচলিত হলে চলবে না। প্রকৃত কবি সেই যে নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করে নিয়ে চলে আমৃত্যু।
এ প্রসঙ্গে আমার একজন অতিপ্রিয় লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কয়েকটি কথা মনে পড়ছে- "ছোটোগল্পের জন্যে ভরসা করতে হয় লিটল ম্যাগাজিনের ওপর। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবাঙলায় ছোটোগল্পে নতুন তরঙ্গ অনুভব করা যায় প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনেই। তাঁদের লেখায় ছোটোগল্পের ছিমছাম তনুখানি অনুপস্থিত, সাম্প্রতিক মানুষকে তুলে ধরার তাগিদে নিটোল গপ্পো ছেড়ে তাঁরা তৈরি করেছেন নানা সংকটের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত ছোটোগল্পের খরখরে নতুন শরীর। এইসব লেখকদের অনেকেই অল্পদিনে ঝরে পড়বেন, সমালোচকদের প্রশংসা পাবার লোভ অনেকেই সামলাতে না পেরে চলতে শুরু করবেন ছোটোগল্পের সনাতন পথে।” তিনি যথার্থই বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে তাঁর 'খোয়াবনামা' ও 'চিলেকোঠার সেপাই' পড়লে আমরা বুঝতে পারব- তিনি কীভাবে ভাষাকে আক্রমণ করেছেন। এছাড়া তাঁর ছোটোগল্প থেকে দু-একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারব:
"জুয়ার আড্ডা থেকে ১টা স্কুটার ড্রাইভার তাস ফেলতে ফেলতেকুকুরজোড়া দেখে এবং ১মিনিট পরপর সিগ্রিটওয়ালাকে ধমকায়, "আব্বে দে না হালায় চুতমারানি।" (উৎসব)
"আনোয়ার আলি তার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে সর্দার সাহেব গজগজ করে, 'শুওরের বাচ্চাগো কারবারটা দ্যাহেন। হালায় বেশরম বেলাহাজ মানুষ, কি কই এগো কন? মহল্লার মইদ্যে কতো শরিফ আদমি আছে, ঘরে বিবি বাল বাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়? দ্যাখছেন?" (উৎসব)
"বড়ো রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগীপট্টি, মতিনে হালায় দাওয়াই দিতো খানকি মাগীগো আর খানকিগো ভাউরা থাকে না? হেইগুলিরে। মাগীপট্টির কেউগার ব্যারাম হইছে তো ডাকো হালায় লম্বুরে, জিন্দাবাহারের মইদ্যে হ্যার নামই আছিলো খানকির ডাক্তার।” (ফেরারী)
ভাষাটা লক্ষ্য করো। এই ভাষায় তোমরা লেখালেখি করলে তোমাদের লেখা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, লিটল ম্যাগাজিন নামধারী সতী ম্যাগাজিনও তোমার লেখা ছাপবে না। ইলিয়াসের 'ফেরারী' গল্পটি ওদেশের কোনো লিটল ম্যাগাজিন ছাপেনি। শুধু তাই নয়, তার উপন্যাস দুটিও কিছু অংশ ছাপার পর আর কোনো ম্যাগাজিন ছাপতে চায়নি। আসলে কী জানো, আমাদের তথাকথিত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ধ্বজাধারীরা মনে করেন, শুধুমাত্র বড়ো বড়ো পত্রপত্রিকাগুলোই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এইসব বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক কাগজে না লিখলেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী হওয়া যায়। আগেও বলেছি, আবারও এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিবাহ করে একটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। এই পরিবার হল রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত ভিত। প্রতিষ্ঠানগুলি হল পরিবার, সমাজ [স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব, অফিস, আদালত, হাসপাতাল, ধর্মপ্রতিষ্ঠান (মসজিদ-মন্দির-গির্জা এবং কোরান-বাইবেল-গীতা) প্রভৃতি ও রাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে আমরা কতগুলিকে অস্বীকার করতে পারি? তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, ধর্মও একটা বড়ো প্রতিষ্ঠান। বলা যায় ক্ষমতার একটি বড়ো কেন্দ্র। ক্ষমতার সেই বড়ো স্থানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একটা চরম আঘাত দিয়ে ফেলায় কোনো
পত্র-পত্রিকা তাঁর 'ফেরারী' গল্পটি ছাপতে রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে শাহাদুজ্জামানকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন: "...ফেরারী'। বেশ কয়েকটি পত্রিকা থেকে গল্পটা ফেরত আসে। পড়েছো? গল্পের এক জায়গায় আছে যে, পিতৃশোক এড়াতে গিয়ে গল্পের চরিত্র হানিফ যখন এ-গলি ও-গলি ধরে পালাতে চেষ্টা করছে তখন তার হাত থেকে কোরান শরিফ পড়ে যায়। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, তাকে কেউই হেলপ করতে পারছে না, নট ইভন দা হোলি বুক। তবু কেউ আর ছাপতে চাইলো না। সুতরাং সরাসরি ওটা আমার বইয়ে ঢুকিয়ে দিলাম।" সেদিন আমরা বুঝে গিয়েছিলাম লিটল ম্যাগাজিনের সতীপনা, সেদিন বোঝা গিয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন কত বড়ো প্রতিষ্ঠান হতে পারে। এখানে যদি হানিফ না হয়ে রাম হত, তার পায়ের কাছে 'গীতা' পড়ে যেত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সতী লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা এই লেখা ছাপত না।
তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশই এপথে আর যেতে চায় না। আজ আর কেউ নষ্ট হতে চায় না। কেউ কষ্ট করতে চায় না। কষ্ট পেতে চায় না। কেউ নরকে যেতে চায় না। সকলেই স্বর্গে যেতে চায়... সকলেই ভদ্রলোক হইতে চায়... সকলেই সুশীলবাবু হইতে চায়... তারা অধিকাংশই নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে একে-অপরকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে... ধাক্কা খেয়ে পথে কেউ বা গড়াগড়ি খাচ্ছে... তবু আনন্দবাড়িতে যেতেই হবে... কে কার আগে আনন্দবাড়িতে পৌঁছবে... তরুণের দল আনন্দবাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে...
প্রসঙ্গে ফিরি, আমার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে থাকে এক বিপন্ন বিস্ময়, যা আমাকে সুস্থির থাকতে দেয় না। এই অস্থিরতা নিয়েই বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করা... আগেই বলেছি 'পত্রিকা করা একটা যুদ্ধ।' এই যুদ্ধটা আমার জীবন যুদ্ধের সঙ্গেই জুড়ে গেছে... এখন ভালোই লাগে। 'আমি আগে বাঙালি, পরে ভারতীয়'-আমি এভাবেই ভাবি এবং বিশ্বাস করি। আমার মায়ের ভাষাই আমার পরিচয়। প্রসঙ্গক্রমে নবারুণ ভট্টাচার্যের পুরন্দর ভাটের কবিতা থেকে একটি কবিতা বলি-'বাঙালির তরে যদি/বাঙালি না কাঁদে/চুতিয়া বলে তাকে/ডাকো ভীমনাদে।'
(৭) প্রকৃত বন্ধু বলতে কাদের কথা মনে পড়ে? কোন সময়টা?
উত্তর: দ্যাখো, বন্ধুত্বের কথা উঠলে আমার মনে পড়ে যায় কহলিল জিব্রানের সেই বিখ্যাত কথাটি - "Friendship is always a sweet responsi-bility, never an opportunity." শুধু তাই নয়, বন্ধু নিয়ে বব মারলির একটা অসাধারণ কথা আছে বন্ধুত্ব নিয়ে "True friends are like stars;
you can only recognize them when it's dark around you." সত্যিকারের বন্ধু নক্ষত্রের মতো... তুমি তখনই তাঁকে চিনতে পারবে যখন তোমার চারিদিকে অন্ধকার ঘিরে ধরবে... অবশ্যই শৈলেশ্বর ঘোষ। এছাড়া অরূপ দাশ, গৌতম সরকার ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় এরা আমার জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পরবর্তীতে সাত্ত্বিক নন্দী, স্বপনরঞ্জন হালদার, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ বিশ্বাস, শুভময় সরকার, আশিস দে সরকার, স্নেহাশিস রায় ... এরা সব আমার বন্ধু... অবশেষে একটা কথা বলি, 'সকলে বন্ধু নয়, কেউ কেউ বন্ধু।'
(৮) বিরাগভাজন হয়েছেন কখনও?
উত্তর: হ্যাঁ, হয়েছি... বহুবার হয়েছি... তুমি যদি সঠিক রাস্তায় থাকো তবে তুমি বিরাগভাজন হবেই। আসলে ঘটনাগুলো এমন যে, অপরাধ না করে অপরাধী হয়ে গেছি। যাদেরকে বন্ধু ভেবেছি তারা আমাকে বন্ধু ভাবেনি, তারা অনেকে ব্যবহার করেছে। আমার মা বলত, 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি।' এ ধরনের লোকজনই বেশি আমাদের সমাজে... তোমাকে ব্যবহার করবে, কাজ ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দিতে পারলে তুমি ভালো, না দিতে পারলে তুমি খারাপ। আমি খারাপ লোকই, আমি কোনোদিন ভালো লোক হতে চাইনি। আমি তো পাখি নই, তাই আমি উড়তে চাই না। যারা উড়ছে উদ্বুক... আসলে আমি মাটিতে পা রেখে আকাশ দেখতে চাই...
(৯) কর্মক্ষেত্রে, এত বছর পত্রিকা এবং প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর... কোনো রিগ্রেটস আছে? কোনো কিছু নিয়ে অনুশোচনা হয়?
উত্তর: হ্যাঁ, পত্রিকা করতে গিয়ে লেখালেখির ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো আক্ষেপ নেই। আমার পত্রিকাটি আমার সন্তান। ফলত, ফোকাসটা সবসময় পত্রিকার দিকেই থেকেছে। আর তাছাড়া আমি যে ধরনের লেখালেখি করি সে লেখা অধিকাংশ পত্রিকাই ছাপতে চায় না। ফলত পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন কবি ফালগুনী রায় বলেছিলেন, 'আমি লেখার জন্য কোনো কাগজ পাচ্ছি না।' কী লিখতেন ফালগুনী?
(১০) আপনার প্রকাশিতব্য যে উপন্যাস... নিয়ে অনেক বছর হল আপনি পাণ্ডুলিপির কাজ করছেন। মাঝে স্থগিতও থেকেছে কাজ। নিজের কাজকে ডিপ্রায়োরিটাইজ করতে পারাও এক স্যাক্রিফাইস। এমন একটা সময়ে, যেখানে নিজেকে ওপরে তুলে ধরতে পারলে আর কিছু চায় না অনেকেই। আপনার সেই প্রকাশিতব্য উপন্যাস, তার গড়ে ওঠার একটা দৃশ্য যদি আমাদের দেন।
উত্তর: প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। দু'বার প্রুফ দেখা এই কয়েকদিন আগে সম্পূর্ণ হল। হ্যাঁ, স্থগিত থেকেছে। নিজের পত্রিকার কাজ, এছাড়া শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ-এর 'রচনা সমগ্র'-এর সম্পাদনার কাজ একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে হয়েছে। যেমন আমার প্রথম উপন্যাস, 'হেমন্তের কারুবাসনা ও পরাজিতের আখ্যান'-ও দীর্ঘদিন লেখা হয়ে পড়েছিল। প্রায় কুড়ি বছর পর গ্রন্থটি প্রকাশ করি ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। ২০১১ সালে 'কারুবাসনা'র 'নৈরাজ্য সংখ্যা'য় একটা পর্ব 'আমরা বেদনার সন্তান' প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পর্বটি পড়ে শৈলেশ্বরদা পুরো লেখাটা পড়তে চান। আমি ওনাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিই। ভীষণ নাকউঁচু মানুষ ছিলেন। উনি পড়ে একটিই মন্তব্য করেছিলেন- 'সব্যসাচী উপন্যাসটি ছাপো।' মূল উপন্যাসটি লেখা হয়ে গিয়েছিল ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে। ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ পরপর তিনটি (১) 'আমরা বেদনার সন্তান' (২) 'ঋত্বিকের কারুবাসনা' (৩) 'মিরর ও তারকোভস্কির কারুবাসনা' নামে পর্বগুলোর সংযোজন ঘটে।
উপন্যাসটি একপ্রকার জোর করে নিয়ে অরুণাভ বিশ্বাস তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'আলাপপর্ব'-এ প্রকাশ করে ২০১৩ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায়। তবু পুরোটা সেখানে দেওয়া যায়নি। সেখানে পাতার সংকুলানের ব্যাপারটা ছিল। সেখানে তিনটি পর্ব বাদ দিই: (১) মরিবার হ'লো তার সাধ (২) 'ঋত্বিকের কারুবাসনা' (৩) 'মিরর ও তারকোভস্কির কারুবাসনা'। উক্ত তিনটি রচনার ভেতর শেষ দুটি রচনা শিলিগুড়ির 'সিনেভাস' পত্রিকায় ছাপা হয়, যথাক্রমে ২০০৯ ও ২০১১ সনে। প্রসঙ্গক্রমে জানাই সেখানে নামগুলো একটু অন্যরকম ছিল। যা-হোক এবার পুরোটা থাকল, সঙ্গে কিছুটা সংশোধন... এত কাল পড়ে থাকার ফলে স্বাভাবিক কারণে কিছু গ্রহণ ও বর্জন ঘটে গেছে... যদি সম্পূর্ণ উপন্যাসটির সৃজন সময় ধরতে হয়, সে-ক্ষেত্রে উপন্যাসটির সৃষ্টিকাল বলা যেতে পারে ২০১১ সালকেই। ২০১১ তে প্রকাশ করা যেতে পারত... কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই তা প্রকাশ করা যায়নি। আসলে পত্রিকাটি আমি বরাবরই বেশি গুরুত্ব দিই। ফেসবুকে কিছু কিছু করে পোস্ট করেছিলাম। আমার বন্ধু আশিস দে সরকার, ফোন করলেই বলত- 'সব্যসাচীদা এবার উপন্যাসটি ছাপুন।' শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হল উপন্যাসটি।
'স্মৃতির আর এক নাম অসুখ' লেখাটি শুরু করেছিলাম ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দেখো যখন লেখাটি শুরু করেছিলাম, তখন জানতাম না যে এই আকার ধারণ করবে! লিখতে লিখতে লেখা ২০২০ জুনে এসে লেখাটি দুশো পাতা ছাড়িয়ে গেল। ঠিক করলাম আর লিখব না। তারপর প্যান্ডেমিক এসে গেল। মা চলে গেল ১২ সেপ্টেম্বর। প্রায় বছর দুয়েক আর কোনো লেখা লিখতে পারি না। মাতৃহারা হয়ে দু-বছর এক ভয়ঙ্কর উন্মাদনার মধ্যে বাস করেছি। তখন বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। এক অসীম বেদনা নিয়ে যততত্র ঘুরে বেড়িয়েছি... মাকে খুঁজে বেড়িয়েছি... মায়ের মৃত্যু আমাকে পেড়ে ফেলেছিল... এমনও ভেবেছি-এ জীবন রেখে কী করব! এই মানুষটার না থাকা আমাকে সবসময় বেদনা দিয়েছে... আজ বেদনা দেয়... তারপর আমার ভাইরা ও দু-একজন বন্ধু-বান্ধব পাশে থেকেছে... বিশেষ করে স্বপনদা (বাঘের বাচ্চা'র সম্পাদক স্বপনরঞ্জন হালদার), উজ্জ্বলদা (কবিতা-ক্রিয়া-ইন্ডিয়ার সম্পাদক) ও অরুণাভ বিশ্বাস (লিবার ফিয়েরা প্রকাশনার কর্ণধার)... এরা সবসময়, প্রায় প্রতিদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে... কাজে উৎসাহ দিয়েছে... তারপর আবার লিখতে শুরু করলাম... ২০২২ প্রকাশিত হল কারুবাসনা... এই সময়ে কাজ হারিয়েছি... অক্ষর বিন্যাসের কাজ শুরু করলাম। সঙ্গে সময় পেলে মাঝেমধ্যে লেখাটা নিয়ে বসেছি... এই সময়ে মাকে নিয়ে 'অন্নপূর্ণার ঘর-সংসার' নামে একটা বড়ো পর্ব লিখেছি... এইভাবে ৩০০ পাতা ছাড়িয়ে গেল।











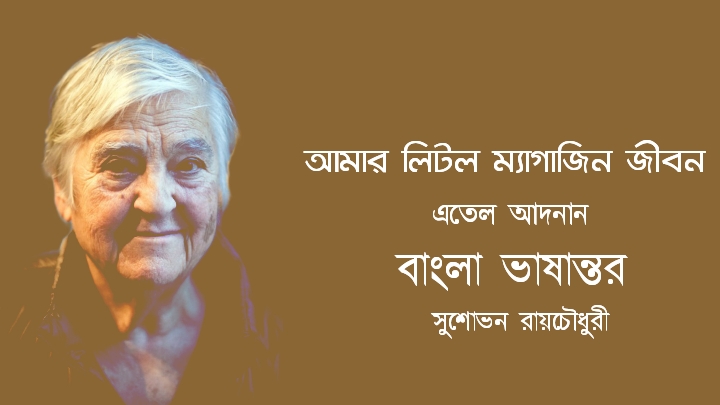
Comments